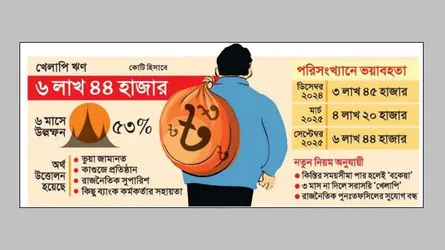ড. মো: শফিকুল ইসলাম
বাংলাদেশে অ্যানথ্রাক্স নতুন কোনো রোগ নয়। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে, এই রোগটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকেই বাংলাদেশে উপস্থিত আছে। ১৯৪০-৫০-এর দশকে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) অ্যানথ্রাক্সের প্রাদুর্ভাব রেকর্ড করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ও বিক্ষিপ্তভাবে দেখা গেছে। ১৯৯০-২০০০ সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অ্যানথ্রাক্সের প্রাদুর্ভাব নথিভুক্ত করা হয়েছে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ ও মধ্য অঞ্চলে।
বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ করে রংপুর বিভাগের পীরগঞ্জ, গাইবান্ধা ও রংপুর জেলার কিছু এলাকা ইদানীং অ্যানথ্রাক্স রোগের মুখোমুখি হয়েছে। এই রোগটি কেবল গবাদিপশুর জন্যই নয়, মানুষের জন্যও একটি মারাত্মক ঝুঁকি (জুনোটিক ডিজিজ)। প্রাণিসম্পদ অধিদফতর ও স্থানীয় প্রশাসনের জরুরি পদক্ষেপ সত্ত্বেও এই প্রাদুর্ভাব স্থানীয় জনগণ, কৃষক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
অ্যানথ্রাক্স একটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ, যার কারণ Bacillus anthracis নামক একটি অত্যন্ত সহনশীল ব্যাক্টেরিয়া। এটি স্পোর আকারে মাটিতে দশক এমনকি শতাব্দী ধরে টিকে থাকতে পারে। বাংলাদেশ, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের জমি, অনেকাংশে অ্যানথ্রাক্স স্পোর দ্বারা দূষিত বলে ইতিহাসে জানা আছে। স্পোরগুলো মাটি, পানি ও গাছপালায় লেগে থাকতে পারে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলে আবার ভেজিটেটিভ ফর্মে পরিণত হয়ে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।
মানুষের শরীরে অ্যানথ্রাক্স (জুনোটিক অ্যানথ্রাক্স) তিনটি প্রধান রূপে দেখা দিতে পারে; ত্বকীয় অ্যানথ্রাক্স, এটির সবচেয়ে সাধারণ রূপ (৯৫ শতাংশ)। আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসা, তার গোশত কাটা বা চামড়া ছাড়ানোর সময় ত্বকের মাধ্যমে ব্যাক্টেরিয়া প্রবেশ করে। প্রথমে একটি ফোস্কা পরে তা একটি
ব্লাক স্কার বা কালো পুঁজযুক্ত ঘায়ে পরিণত হয়। সময়মতো চিকিৎসা না হলে রক্তে সংক্রমণ (সেপ্টিসেমিয়া) হয়ে মৃত্যুও হতে পারে।
আন্ত্রিক অ্যানথ্রাক্স, আক্রান্ত পশুর অসিদ্ধ বা আধা-সিদ্ধ গোশত খাওয়ার মাধ্যমে হয়। এতে পেটে ব্যথা, জ্বর, বমি, রক্তাক্ত পায়খানা লক্ষণ দেখা দেয় এবং এটি অত্যন্ত মারাত্মক।
শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত অ্যানথ্রাক্স, অ্যানথ্রাক্স স্পোর শ্বাসের সাথে ফুসফুসে গেলে হয়। এটি সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ, যদিও বাংলাদেশে এটি খুব কম, এর মৃত্যুর হার খুব বেশি।
স্থানীয় হাসপাতাল সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ স্বকীয় অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের দ্রুত চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে। তবে, অপ্রতিবেদিত নথিভুক্ত সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে।
একজন ফার্মাকোলজিস্টের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনা কেবল একটি স্বাস্থ্য সঙ্কটই নয়, এটি আমাদের প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জৈব-নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্য নীতির একটি বড় ধরনের পরীক্ষা। অ্যানথ্রাক্স ম্যানেজমেন্টে ফার্মাকোলজির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওষুধের কার্যকারিতা, ডোজ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এই রোগ মোকাবেলায় অপরিহার্য। অ্যানথ্রাক্স একটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ হওয়ায় এর চিকিৎসার মূল ভিত্তি হলো অ্যান্টিবায়োটিক। সিপ্রোফ্লোক্সাসিন এবং ডক্সিসাইক্লিন হলো অ্যানথ্রাক্সের চিকিৎসার জন্য প্রথম পছন্দের অ্যান্টিবায়োটিক।
এই ওষুধগুলো অ্যানথ্রাক্স ব্যাক্টেরিয়াকে মেরে ফেলতে খুব কার্যকর। বিকল্প ওষুধ হিসেবে পেনিসিলিন, অ্যামক্সিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিকও কার্যকর, যদিও কিছু স্ট্রেইনে অকার্যকারিতার রিপোর্ট রয়েছে। অ্যানথ্রাক্সের চিকিৎসা সাধারণত সাত থেকে ১৪ দিন এমনকি ৬০ দিন (শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত অ্যানথ্রাক্সের ক্ষেত্রে) পর্যন্ত চলতে পারে। উপশম ভালো হলেও ওষুধের ডোজ সম্পূর্ণ করা অত্যন্ত জরুরি, নতুবা রোগ ফিরে আসতে পারে। গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে, যেমন দেহের পুরো সিস্টেমব্যাপী সংক্রমণের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের পাশাপাশি অ্যানথ্রাক্স অ্যান্টিটক্সিন ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যাক্টেরিয়া নিঃসৃত বিষ, যার প্রভাব প্রাণিদেহে অ্যানথ্রাক্সের টক্সিনকে নিষ্ক্রিয় করে।
পশুর জন্য অ্যানথ্রাক্সের লাইভ-অ্যাটেনিউটেড ভ্যাকসিন খুবই কার্যকর এবং এটি প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের মূল হাতিয়ার। মানুষের জন্যও টিকা আছে, যা মূলত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষাগার কর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, আমাদের এই জীবনরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর পর্যাপ্ত মজুদ, সঠিক ব্যবহার ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।
অ্যান্টিবায়োটিকের অসম্পূর্ণ কোর্স, ভুল মাত্রা বা নিম্নমানের ওষুধ ব্যবহার রোগীর জন্য বিপজ্জনক এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধের (AMR) সৃষ্টির ঝুঁকি বাড়ায়, যা বিশ্বব্যাপী একটি বড় স্বাস্থ্য হুমকি।
বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকটি জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আক্রান্ত ও সংলগ্ন এলাকার গবাদিপশুকে বিনামূল্যে অ্যানথ্রাক্সের টিকা দেয়া হচ্ছে। এটি ভবিষ্যৎ প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা। প্রাদুর্ভাবের স্পটগুলোতে পশুর চলাচল, ক্রয়-বিক্রয় এবং পরিবহন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণের মধ্যে অ্যানথ্রাক্সের লক্ষণ, প্রতিরোধ পদ্ধতি এবং ঝুঁকি সম্পর্কে উচ্চ সতর্কতা, লিফলেট ও সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে।
অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত মৃত পশুকে গভীর গর্ত খুঁড়ে চুন ছিটিয়ে পুঁতে ফেলা হচ্ছে, যাতে স্পোর পরিবেশে ছড়াতে না পারে। আক্রান্ত জনগণকে বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে। বর্তমান জরুরি পদক্ষেপ প্রশংসনীয়; কিন্তু একটি টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন করা জরুরি প্রয়োজন।
জাতীয় অ্যানথ্রাক্স নিয়ন্ত্রণ কৌশল তথা অ্যানথ্রাক্সকে নেগলেগটেড ট্রপিক্যাল রোগের মতো একটি ব্যাপক জাতীয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল তৈরি করতে হবে, যেখানে প্রতিরোধ, প্রাথমিক শনাক্তকরণ, দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং গবেষণার ওপর ফোকাস করতে হবে। নিয়মিত ও ব্যাপক টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে কেবল প্রাদুর্ভাবের সময় নয়, দেশের সব এনডেমিক এলাকায় গবাদিপশুর জন্য নিয়মিত (বার্ষিক) অ্যানথ্রাক্স টিকাদান কর্মসূচি বাধ্যতামূলক করতে হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল এবং মাঠপর্যায়ের পশুচিকিৎসকদের জন্য দ্রুত ডায়াগনস্টিক টেস্ট কিট সরবরাহ করতে হবে, যাতে তারা দ্রুত রোগ শনাক্ত করতে পারেন।
ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে প্রাণিস্বাস্থ্য এবং মানবস্বাস্থ্য সেক্টরের মধ্যে রিয়েল-টাইম ডেটা শেয়ারিং এবং সমন্বয় জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে অ্যানথ্রাক্স স্পোরের পরিবেশগত বণ্টন, প্রবাহিত স্ট্রেন, জেনেটিক বৈশিষ্ট্য এবং আরো কার্যকর ভ্যাকসিনের ওপর গবেষণাকে উৎসাহিত করতে হবে। আক্রান্ত পশু জবাই এবং পরিবহন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে পালন নিশ্চিত করতে হবে এবং আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখতে হবে।
উত্তরাঞ্চলে অ্যানথ্রাক্সের প্রত্যাবর্তন আমাদের জন্য একটি জোরালো অশনি সঙ্কেত। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্বল প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রাচীন রোগগুলোকে কিভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। এটি কেবল একটি ভেটেরিনারি ইস্যু নয়, এটি একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সঙ্কেত। সরকার, গবেষক, ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার, মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণের সমন্বিত প্রয়াসই কেবল এই হুমকিকে জয় করতে পারে। সচেতনতা, প্রতিরোধ, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রাণিসম্পদ ও জনগণের স্বাস্থ্যকে অ্যানথ্রাক্সের মতো ভয়াবহ রোগ থেকে রক্ষা করতে পারি।
লেখক : প্রফেসর, ফার্মাকোলজি বিভাগ, ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি সায়েন্স, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ