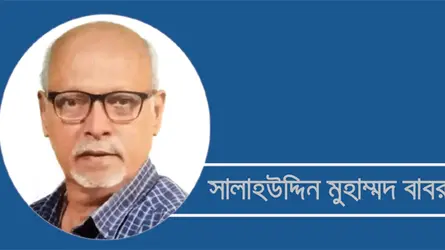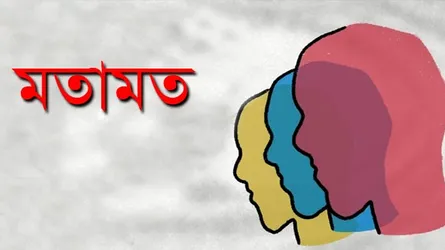এ এইচ এম ফারুক
বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম বরাবর একটি সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (কথিত শান্তিচুক্তি) এ অঞ্চলের দীর্ঘ দিনের সঙ্ঘাতের অবসানের একটি ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা হলেও এর বাস্তবায়ন নিয়ে এখনো বিতর্ক ও জটিলতা বিদ্যমান। অনেক গবেষক মনে করেন, চুক্তির আওতায় গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বাংলাদেশের একক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কার্যত আরেকটি স্বায়ত্তশাসিত কাঠামো তৈরি করেছে, যা অনেক ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রশাসনিক মডেলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ধারণাটি কেবল রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় নয়; বরং দেশের সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার দৃষ্টিকোণ থেকেও গভীর বিবেচনার দাবি রাখে। আঞ্চলিক পরিষদ ইস্যুতে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলে বিষয়টি আমলে নিয়ে উচ্চ আদালত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ অসাংবিধানিক ঘোষণা করে অবৈধ বলে রায় দেন। যদিও এ নিয়ে পরে আপিল করা হয়েছে।
পার্বত্য চুক্তির প্রেক্ষাপট ও আঞ্চলিক পরিষদ
দুই দশকের সশস্ত্র সঙ্ঘাতের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সংস্কৃতি রক্ষা করা এবং তাদের জন্য একটি বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এর ধারাবাহিকতায় গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। এ পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা এবং উন্নয়ন কাজের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করা। এটি কেবল একটি প্রশাসনিক সংস্থা নয়; বরং এর গঠন ও কার্যপরিধি বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক বলে এক নতুন বিতর্ক যোগ করে।
চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান হলেন একজন উপজাতীয় ব্যক্তি, যিনি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পদটি উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত। বলা বাহুল্য, চুক্তিতে পাহাড়ের নৃগোষ্ঠীভুক্ত জাতিগুলোকে উপজাতি এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীকে অ-উপজাতি হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়েছে।
২২ সদস্যের এ আঞ্চলিক পরিষদে উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয়দের প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার নিয়েও বিস্তর অভিযোগ ও ক্ষোভ রয়েছে। কারণ এখানে জনসংখ্যার বিচারে সব (১৩টি) উপজাতীয় জনগোষ্ঠী এবং অ-উপজাতি বা বাঙালি জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা প্রায় সমান সমান। ফলে এ সদস্য সংখ্যার অনুপাত নিয়ে বিতর্ক শুরু থেকে। এর মধ্যে উপজাতীয় সদস্যের সংখ্যা বেশি। ফলে এ অঞ্চলের জাতিগত ভারসাম্যের প্রতিফলন ঘটেনি। সমালোচকরা বলেন, কাঠামোটি কার্যত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, যা দেশের অন্য কোনো অঞ্চলে বিদ্যমান নেই।
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কাঠামোতে দেখা যায়, উপজাতীয় সদস্য (দু’জন মহিলা ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানসহ) ১৫ জন এবং অ-উপজাতীয় সদস্য একজন মহিলাসহ সাতজন। এখানে এটিও উল্লেখ্য, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানও পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য। এ তিন চেয়ার উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত।
আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যক্রম
অঙ্গরাজ্যের আদল : পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে যে কারণে একটি ‘অঙ্গরাজ্যের আদলে’ কাঠামো হিসেবে দেখা হয়, তার পেছনে রয়েছে এর ব্যাপক ক্ষমতা ও কার্যপরিধি। এ পরিষদ কেবল উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি করে না; বরং আইনশৃঙ্খলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় পুলিশ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমের ওপরও এর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ : পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী, আঞ্চলিক পরিষদ স্থানীয় পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলাবাহিনীকে নির্দেশনা দিতে পারে। যদিও প্রতিরক্ষা ও সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, স্থানীয় পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পরিষদের এ ক্ষমতা দেশের অন্য কোনো জেলা বা অঞ্চলে দেখা যায় না।
ভূমি ব্যবস্থাপনা : ভূমি সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয়গুলোর একটি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ এ ভূমি কমিশনের কার্যক্রমের ওপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যা ভূমি-সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ আরো শক্তিশালী করে। এ ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার সাধারণ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক বলে অনেকে মনে করেন।
প্রশাসনিক সমন্বয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিনটি জেলা পরিষদ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে কাজ করে। এ তিন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানও উপজাতি এবং আঞ্চলিক পরিষদের পদাধিকার বলে সদস্য। কাঠামোটি একটি একক রাষ্ট্রে বিকেন্দ্রীকরণের চেয়েও বেশি ক্ষমতাশালী বলে মনে হয়। এ দিক থেকে বলা যায়, আঞ্চলিক পরিষদ এমন একটি প্রশাসনিক মডেল, যা একটি একক, সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধীনে সীমিত স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে বেশি কিছু প্রদান করে।
চুক্তির অপূর্ণ শর্ত ও অবৈধ অস্ত্রের বিস্তার
দেশের অখণ্ডতার প্রশ্নে ভাগ্য ভালো যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। সেগুলো বাস্তবায়িত হলে এ বিষয়গুলো আঞ্চলিক পরিষদের কার্যকারিতা এবং এ অঞ্চলের শান্তিপ্রক্রিয়া বিঘ্নের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে।
অস্ত্র সমর্পণ : পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির একটি মৌলিক শর্ত ছিল জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান হয়েছিল; কিন্তু পাহাড়ে এখনো জেএসএসসহ অন্যান্য উপজাতীয় সংগঠনের সদস্যদের হাতে অবৈধ অস্ত্রের বিস্তার রয়েছে। এ অবৈধ অস্ত্রের কারণে প্রতিনিয়ত চাঁদাবাজি, অপহরণ ও সঙ্ঘাতের ঘটনা ঘটছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এসব অবৈধ অস্ত্র সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতি প্রমাণ করে, চুক্তির একটি মূল শর্ত অপূর্ণ রয়ে গেছে, যা আস্থার সঙ্কট তৈরি করেছে।
পারস্পরিক অবিশ্বাস : অবৈধ অস্ত্রের উপস্থিতি এবং জেএসএসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় বাঙালি ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহ বাড়ছে। বাঙালিরা মনে করে, জেএসএস একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াচ্ছে, আর উপজাতিরা মনে করে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক নয়। এ অবিশ্বাস দূর না হলে যেকোনো প্রশাসনিক কাঠামো অকার্যকর হতে বাধ্য।
হাইকোর্টের রায়ে আঞ্চলিক পরিষদকে অসাংবিধানিক ঘোষণা
২০১০ সালে হাইকোর্ট এক রায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮-কে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিলেন। এ রায়ের মূল বক্তব্য ছিল, আঞ্চলিক পরিষদের গঠন ও এর প্রদত্ত ক্ষমতা বাংলাদেশের সংবিধানের ‘একক রাষ্ট্র’ (ইউনিটারি স্টেট) নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।
হাইকোর্ট দু’টি প্রধান কারণে এ রায় দিয়েছিলেন-
একক রাষ্ট্রের নীতির লঙ্ঘন : আদালত বলেছিলেন, আঞ্চলিক পরিষদকে যেসব ক্ষমতা দেয়া হয়েছে (যেমন- আইনশৃঙ্খলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি), তা বাংলাদেশের সংবিধানের একক রাষ্ট্রীয় চরিত্র ক্ষুণ্ণ করে। পরিষদকে দেয়া বিশেষ ক্ষমতাগুলো একটি একক রাষ্ট্রের মধ্যে কার্যত একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করে, যা সংবিধানের মূল কাঠামোর সাথে মেলে না।
প্রশাসনিক ইউনিটের শর্ত পূরণ না হওয়া : আদালত আরো বলেছিলেন, যদি এ পরিষদকে স্থানীয় সরকার সংস্থা হিসেবে ধরা হয়, তবে এটি সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত হয়নি। এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, একটি স্থানীয় সরকার সংস্থা গঠনে সেই এলাকাকে একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ঘোষণা করা প্রয়োজন, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে করা হয়নি।
হাইকোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে আপিল করা হয়। আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দেন, যার ফলে পরিষদ এখনো তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে, বিষয়টি আপিল বিভাগে বিচারাধীন।
ভবিষ্যতের পথ ও সুপারিশমালা
পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নে রাজনৈতিক সমঝোতা ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা অপরিহার্য। একটি কার্যকর আঞ্চলিক পরিষদ তখন সফল হতে পারে, যখন এর ভিত্তি হয় পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। তবে তা এমনভাবে করা যাবে না যাতে তা সংবিধানের একক রাষ্ট্রকাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এ লক্ষ্য অর্জনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন-
অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার : অবিলম্বে এবং কঠোরভাবে পাহাড়ে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করা অপরিহার্য। যতক্ষণ পর্যন্ত অবৈধ অস্ত্রগুলো জনগণের হাতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক সমাধান স্থায়ী শান্তি আনতে পারবে না। এটি কেবল স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না; বরং সব পক্ষের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলবে।
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা : স্থানীয় প্রশাসনের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব কমিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সবধরনের অপরাধ, বিশেষ করে চাঁদাবাজি ও সহিংসতা কঠোর হাতে দমন করতে হবে, তা যেই করুক না কেন।
স্থানীয় সব জাতিগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে সংলাপের মাধ্যমে সমাধান স্থানীয় বাঙালি ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সব জাতিকে নিয়ে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের সাথে খোলামেলা ও গঠনমূলক সংলাপের আয়োজন করা উচিত। ভূমি, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি টেকসই ও সংবিধানসম্মত সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।
সবশেষে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ একটি ঐতিহাসিক প্রয়াস হলেও, এর গঠনপ্রণালী ও সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক আইন এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করেছে।
এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি নির্ভর করে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের আগে সংঘর্ষিক ধারাগুলো সংশোধন এবং সব পক্ষের মধ্যে আস্থা প্রতিষ্ঠার ওপর। যতক্ষণ পর্যন্ত অবৈধ অস্ত্রের বিস্তার বন্ধ না হচ্ছে এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ পরিষদ কার্যকরভাবে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। দেশের সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের স্বার্থ সুরক্ষায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাধান খুঁজে বের করা এখন সময়ের দাবি।
লেখক : সাংবাদিক ও লেখক