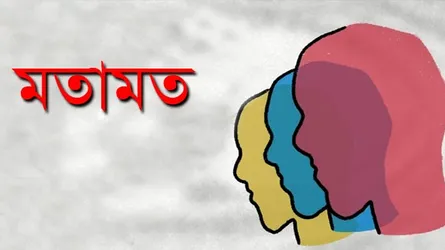ড. মাহবুবুর রাজ্জাক
সম্প্রতি সরকারের একজন প্রভাবশালী উপদেষ্টা দেশের প্রকৌশলীদের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, দেশের মেগা প্রজেক্টগুলোতে দেশীয় প্রকৌশলীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছেন না; এ ক্ষেত্রে আমরা পুরোটাই বিদেশনির্ভর। এর দায়টা তিনি চাপিয়ে দিলেন বুয়েটসহ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর।
আসলে কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই পেশাজীবনের প্রথম দিন থেকে স্নাতক প্রকৌশলীরা অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রস্তুত থাকেন না, তাদেরকে তৈরি করে নিতে হয়। নতুন প্রকৌশলীদের বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা দেয়ার জন্যই প্রকৌশল পেশায় প্রবেশন পিরিয়ডের ব্যবস্থা থাকে। এই সময়ে তারা পেশা-সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো হাতে-কলমে শিখে নেন। নতুন প্রকৌশলীদের যথাযথ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তথা রাষ্ট্রের। এই জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান তারা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অর্জন করে থাকেন। আমাদের যে সকল শিক্ষার্থী বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন এবং বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুনাম ও দক্ষতার সাথে প্রকৌশল পেশায় নিয়োজিত আছেন, তাদের সাফল্যই প্রমাণ করে- আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পাস করে বের হওয়া স্নাতকদের থেকেই আন্তর্জাতিক মানের প্রকৌশলী বের করে আনা সম্ভব।
তবে কেন আমাদের প্রকৌশলীরা দেশের মেগা প্রজেক্টগুলো নিজেরা সামলাতে পারেন না? এর উত্তরটা দিতে হবে তাদের, যারা বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট। তারা কি আসলেই চান দেশের প্রকৌশলীরা একদিন মেগা প্রজেক্টগুলো নিজেরাই সামলাবেন? সেই পরিকল্পনা কই? এ জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে না? আমরা যদি দেশের প্রকৌশলীদের বড় কাজ করার জন্য প্রস্তুত না করি তবে তারা বড় কাজ কিভাবে করবেন? বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন তদানীন্তন পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের সাথেই কাজ শুরু করেছিল। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণেই আজ পাকিস্তানের আণবিক শক্তি কমিশন সফলভাবে পারমাণবিক পরীক্ষা করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। আমাদের সে রকম সিদ্ধান্ত ছিল না। তাই আমাদের বিজ্ঞানীরা পারেননি। আমি এখানে বিজ্ঞানীদের তো দোষ দেখি না। প্রকৌশলের মেগা প্রজেক্টের অভিজ্ঞতা তো আর রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছাড়া নিজে নিজে অর্জন করা যায় না।
বুয়েটকে এই দেশে সব কাজের কাজি মনে করা হয়। বুয়েটে যারা পড়াশোনা করে তারা মেধার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই এখানে আসেন। মেধাবী হিসেবে তাদের সুনাম আছে। কিন্তু শুধু মেধাবী হলেই প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধা করা যায় না। এ জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। বুয়েটের শিক্ষকদের বিশেষ কোনো কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ করে তোলার জন্য পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এমন নজির একটিও নেই। তারা নিজের উদ্যোগে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যান। যেখানে সুযোগ পান সেখানেই যান। এমনকি তারা যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন তা দেশের কাজে লাগবে কি না সেটি ভেবেও দেখেন না। তারা প্রমোশনের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু গবেষণাই করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা আমাদের এখানে হয় না বললেই চলে। কাজেই দেশের কারিগরি সমস্যার সমাধানে বুয়েটের সক্ষমতা নিয়ে জনমনে যে উচ্চ ধারণা প্রচলিত আছে, তার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই।
বিগত স্বৈরাচারী সরকারের আমলে বুয়েটে প্রকাশনা প্রণোদনার নামে টাকাপয়সা নয়ছয় হয়েছে। বিনিময়ে বুয়েট কী অর্জন করেছে তা আমার জানা নেই। আমরা খামোখাই র্যাঙ্কিং নিয়ে শোরগোল করি। যে সমস্ত ক্ষেত্রে যত্ন নিলে র্যাঙ্কিং বৃদ্ধি পেতে পারে সেদিকে আমাদের নজর নেই, সেখানে আমাদের বিনিয়োগ নেই। বুয়েটকে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে প্রথমেই দরকার সরকারের সদিচ্ছা ও একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা।
পাকিস্তান সরকার ১৯৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এঅ্যান্ডএম ইউনিভার্সিটির সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা চুক্তির আওতায় বুয়েট প্রতিষ্ঠা করেছিল বলেই বুয়েটের কারিকুলাম এবং নিয়ম-কানুন নিয়ে আমরা আজও গর্ব করতে পারি। সরকার ইচ্ছা করলে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বুয়েটের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার এমন আরেকটি প্রকল্প হাতে নিতে পারে। বিশেষ কোনো দক্ষতা অথবা সাফল্য অর্জনের লক্ষ্য সামনে রেখে পরিকল্পিত উপায়ে বিনিয়োগ না করেই বুয়েটের সমালোচনা করলে ভুল হবে। বাংলাদেশ যদি উদ্ভাবনের জাতি হওয়ার স্বপ্ন দেখে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সরকারকে শিক্ষা গবেষণা খাতে বাজেট বাড়াতে হবে। দক্ষ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে।
সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকেও বিনিয়োগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার শিল্প খাতে যে ভর্তুকি দেয় এবং কর-ছাড় দেয় তার বিনিময়ে ইন্টার্নশিপ ও গবেষণা খাতে বিনিয়োগের শর্ত থাকতে হবে। জার্মানি, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ানসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো শিল্প খাতে যে সুবিধা দেয় তার সাথে শ্রমশক্তি উন্নয়নে বিনিয়োগের শর্ত বাঁধা থাকে। কারণ, বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রসারের মূল ধারায় উদ্ভাবন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে, শিক্ষার্থীরা তা সাথে করে শিল্প ক্ষেত্রে নিয়ে যায় এবং মানুষের কল্যাণে তা বাজারে ছড়িয়ে দেয়। বেল ল্যাব, বার্কলে, স্ট্যানফোর্ডের মতো জায়গায় সেমি-কন্ডাক্টর প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে, ছাত্ররা তা নিয়ে গেছে ইন্টেল আর এনভিডিয়াতে।
শুধু স্নাতক প্রকৌশলীদের পক্ষে একা সব দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। প্রকৌশলীদের পক্ষে দেশের জন্য ফলপ্রসূ কিছু করতে হলে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও দক্ষ টেকনিশিয়ানদের সহায়তা দরকার। অথচ সেই জায়গায় এখন যুদ্ধ লেগে আছে। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা স্নাতক ডিগ্রিধারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন। আর স্নাতক অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা নেমেছেন ডিপ্লোমাদের বিরুদ্ধে।
বর্তমানে সরকারি চাকরিতে একজন স্নাতক প্রকৌশলীর বিপরীতে চারজন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কর্মরত আছেন। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা স্পষ্টভাবে সংখ্যায় বেশি। এ থেকে অনেকের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, প্রকৌশল খাতে ৮০ শতাংশ কাজই ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা করে থাকেন। কিন্তু অনুমান করা যায়, আগামী ১০-১৫ বছরে উৎপাদন ও অবকাঠামো খাতে রুটিন কাজে ব্যাপক অটোমেশন হবে। তখন প্রকৌশল খাতে সৃজনশীল চিন্তা ও ডিজাইন বিশ্লেষণমূলক কাজ হবে বেশি।
প্রকৌশলের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর ভালো দখল না থাকলে তখন উদ্ভূত কারিগরি সমস্যার সমাধা করা যাবে না। তখন এমনো হতে পারে, স্নাতক প্রকৌশলীদের বিপরীতে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সংখ্যা কমে আসবে। বিষয়টি মাথায় রেখে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর না হলে ভবিষ্যতে সঙ্কট আরো বাড়তে পারে।
লেখক : অধ্যাপক, যন্ত্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট