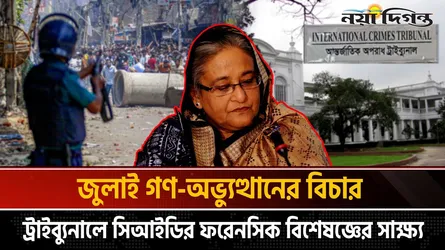এইচ এম জোবায়ের
বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামপন্থী দলগুলোর ভূমিকা দীর্ঘ দিনের। স্বাধীনতার আগে ইসলামী চেতনা ও রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল একটি শক্তিশালী ধারা, যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় থাকে। কিন্তু গত তিন দশকে একটি দৃশ্য বারবার দেখা গেছে, প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনের আগে ইসলামপন্থী দলগুলো নির্বাচনী জোট গঠনের চেষ্টা করে। প্রচার হয় ‘ঐক্যের পথে হাঁটা’র, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই জোট ভেঙে যায়। ব্যর্থতার পর শুরু হয় একে-অপরকে দোষারোপ, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ এবং রাজনৈতিক বিভাজন।
১৯৯১, ২০০১, এমনকি ২০০৮ সালের নির্বাচনেও ইসলামপন্থী দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা হয়েছিল। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনেও একাধিক বৈঠক হয়- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে, নেতাদের দীর্ঘ আলোচনা চলে। কিন্তু প্রতিবারই শেষ মুহূর্তে কোনো না কোনো দল আলাদা পথে চলে যায়। কেউ অভিযোগ করে, ‘অন্য দল অর্থের কাছে নত হয়েছে’, আবার কেউ বলে, ‘আমাদের আসন দাবি মানা হয়নি’। ২০২৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখেও একই প্রবণতা দেখা যায়- আলোচনা হয়, ছবি তোলা হয়; কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই ভাঙন!
বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে অর্থ এক বড় নিয়ামক। বিশেষত ছোট দলগুলোর পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সঙ্গতি না থাকায় নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে বড় দলের সহযোগিতা দরকার হয়। ক্ষমতাসীন বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি প্রায়ই অর্থ, পদ কিংবা ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে ছোট দলগুলোকে নিজেদের দিকে টেনে নেয়। ফলাফল- যে ঐক্যের ডাক এসেছিল সেটি ভেঙে যায়, আশাবাদী বাকি দলগুলো ক্ষুব্ধ হয়।
প্রতিটি জোট আলোচনায় মূল বিতর্ক থাকে আসন বণ্টন নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০১ সালের নির্বাচনে কিছু ইসলামপন্থী দল একসাথে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল; কিন্তু মাত্র দুই-তিনটি আসন নিয়েই দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ছোট দল মনে করে, তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রতীক দরকার, বড় দল মনে করে, বেশি আসন ছাড়লে নিজেদের শক্তি ক্ষুণ্ণ হবে। এই টানাপড়েন থেকে শেষ পর্যন্ত ঐক্যের বদলে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়।
ইসলামী রাজনীতির মূল শক্তি নীতিভিত্তিক অবস্থান হলেও বাস্তবে ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হয়ে দাঁড়ায়। দলীয় সভাপতি বা মহাসচিব অনেকসময় নেতৃত্বে ছাড় দিতে চান না, ফলে এক টেবিলে বসে সমঝোতা হলেও তা টেকে না। ২০১৮ সালের নির্বাচনে কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা শেষ মুহূর্তে ক্ষমতাসীন দলের সাথে ‘নীরব সমঝোতা’ করে জোট থেকে সরে আসেন- এটি জনমনে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
আগের ব্যর্থতা থেকে সৃষ্ট অবিশ্বাস জোট গঠনের পথে বড় বাধা। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, আসন পরিবর্তন, কিংবা নির্বাচনের আগে আকস্মিক সরে দাঁড়ানো- এসব ঘটনার ফলে দলগুলো একে-অপরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। অনেকসময় আলোচনার টেবিলে থাকা সত্ত্বেও গোপনে অন্য দলের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হয়, যা জোটের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়।
ইসলামপ্রিয় মানুষ মনে করে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আদর্শিক বিভাজন ও মতপার্থক্য যেমন- মাজহাব, তরিকা, আকিদা ইত্যাদিতে ছাড় দিতে হবে। দ্বীনের স্বার্থে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হবে। অতিরিক্ত ব্যক্তিনির্ভর রাজনীতি পরিহার করে দল এবং আদর্শকে প্রধান্য দিতে হবে। সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক আচরণ পরিহার করতে হবে। আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করা যাবে না। ইসলাম প্রতিষ্ঠার দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক লক্ষ্যে অটল-অবিচল থাকতে হবে। অর্থের জন্য বিদেশী সংস্থা বা বিতর্কিত উৎসের ওপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। জনমুখী ইস্যুতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে হবে। শুধু ধর্মীয় ইস্যুতে সীমাবদ্ধ না থেকে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ নিয়ে ভাবতে হবে। সাধারণ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বাস্তব সমস্যার সমাধানমুখী কর্মসূচি নিয়ে সামনে এগোতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক চাপ যেন কোনো অবস্থায়ই বৃহত্তর ইসলামী ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, সে ব্যাপারে সব দলকে সতর্ক থাকতে হবে।
আলোচনা ব্যর্থ হলে তার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে ভোটে। ইসলামপন্থী ভোটাররা বিভক্ত হয়ে পড়বে, ফলে পাস উপযোগী ম্যান্ডেট পাওয়া দুষ্কর হবে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালের নির্বাচনে অন্তত ২০-২৫টি আসনে ইসলামপন্থী ভোট বিভক্ত হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি সহজেই জয়ী হয়। অনেক সমর্থক এই পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে ইসলামী রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান, কেউ কেউ অন্য ধারার রাজনীতিতে যোগ দেন।
সুতরাং, বারবার ব্যর্থতা রোধে দরকার দীর্ঘমেয়াদি ও নীতিভিত্তিক সমঝোতা। অতীতের অভিযোগ ভুলে নতুন করে পারস্পরিক আস্থা গড়ে তুলতে হবে। আসন বণ্টন বা প্রতীকের প্রশ্নে ছাড় দেয়ার মনোভাব রাখতে হবে। নির্বাচনী তহবিলে স্বচ্ছতা আনতে হবে, যাতে অর্থের প্রলোভন ব্যর্থ হয়। শুধু নির্বাচনের জন্য নয়, পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনেও একসাথে কাজ করার চুক্তি করতে হবে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দল ও আদর্শকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ইসলামপন্থী দলগুলোর ঐক্য কেবল নির্বাচনী সাফল্যের জন্য নয়; বরং তাদের অস্তিত্ব ও প্রভাব বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। যারা ঐক্য ধরে রাখতে পারে, ইতিহাস প্রমাণ করেছে- তারাই দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবশালী হয়। আর যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অর্থের প্রলোভনে বিভক্ত হয়, তারা সময়ের সাথে সাথে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। তাই এখনই সময় দোষারোপ, অবিশ্বাস ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠে সত্যিকারের ইসলামপন্থী ঐক্য গঠনের- যা দেশের নৈতিক ও আদর্শিক নেতৃত্বের জন্য আবশ্যক। অন্যাথায় দীর্ঘমেয়াদে ইসলামী দলগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
লেখক : সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষক