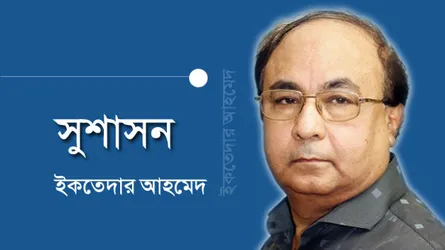সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ভারতবর্ষ ১৯০ বছর ব্রিটিশের অধীনে ছিল। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠা হয় ভারত এবং পাকিস্তান। এলিট হিন্দুরা পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে কখনোই মেনে নিতে পারেনি। একই সাথে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে বাংলাদেশের জনগণ বাধ্য হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। এ কারণেই স্বাধিকার বা সার্বভৌমত্বের স্লোগান দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান দ্রুতই জনপ্রিয় নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। উল্লেখ্য, সে সময়ও আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক ছিলাম। স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো ভোটের অধিকার। বাঙালিদের ভোটের অধিকার ছিল বলেই আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। যদিও শেখ মুজিব এবং তার সুযোগ্য কন্যার শাসনামলে আমাদের সেই ভোটের অধিকার ছিল না।
এবার আসা যাক মূল প্রসঙ্গে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বেশির ভাগই দুই ভাগে বিভক্ত, বিএনপিপন্থী এবং আওয়ামীপন্থী। যে কারণে সত্য ইতিহাস জানা খুবই দুষ্কর। ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ইতিহাস নিয়ে লিখেন কম।
বাংলাদেশের ইতিহাসের কিছু বিষয় পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায়, আমরা যেভাবে ইতিহাস জানি ঘটনাগুলো আসলে ঠিক সেভাবে ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হয়েছিল ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আকাক্সক্ষা নিয়ে। কিন্তু মুসলিম লীগের ব্যর্থতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। পরে এটি সেক্যুলার আওয়ামী লীগে রূপান্তরিত হয়। আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা সব সময় বলেন, জামায়াতকে বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসতে হলে ১৯৭১-এর ভ‚মিকার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনার আগে আমরা মুক্তিযুদ্ধপূর্ব কিছু ঘটনার দিকে নজর দেবো। পাকিস্তান ভাগ করার পক্ষে বিপক্ষে কারা ছিল?
১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবির কোথাও পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছিল স্বাধিকারের কথা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে শেখ মুজিবুর রহমান চারটি দাবি পেশ করেন পাকিস্তানিদের সাথে আলোচনায় বসার শর্ত হিসাবে। সেখানে কোথাও স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছিল সমান অধিকারের কথা। ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ দল হিসেবে কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি। শেখ মুজিব প্রকাশ্যেই অবিভক্ত পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। এ জন্যই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে অস্বীকার করেন এবং স্বেচ্ছায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।
তিনি মুক্তিযুদ্ধ অ্যাভয়েড করেছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর হামলার পর ২৬ মার্চ বাঙালি সেনাসদস্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন। মেজর ডালিমের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ও তারা এমন দ্বিধায় ভুগছিলেন যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে তারা কি স্বাধীন দেশ হিসেবে পাবেন, নাকি ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে? এ কারণেই ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো এবং মুসলিম লীগ পাকিস্তানের স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারতের কবজায় যেতে চায়নি। তারা পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ছিলেন। এটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় তাদের বিবেচনায় থেকে থাকতে পারে, তা হলো ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর ভারত কাশ্মির এবং হায়দরাবাদ গ্রাস করেছিল। এ ছাড়া ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সিকিমে এমন সরকার বসিয়েছিল যারা দেশটিকে ভবিষ্যতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ইতিহাস সাক্ষী, এর তিন বছর পরেই ইন্ডিয়া সিকিম গ্রাস করে।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা কারা চেয়েছিল? উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতের শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাড়া আর কোনো নেতা চাননি পূর্ব পাকিস্তান ভাগ হোক। ওই দুইজন এটা চেয়েছিলেন ব্যক্তিগত, দলীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে। অন্য দিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল মুসলিম লীগ। সে সময় পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর তেমন কার্যক্রম ছিল না, দল হিসাবেও শক্তিশালী ছিল না। সুতরাং স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতা করে বড় কোনো ভূমিকা পালন করার মতো শক্তি ১৯৭১ সালে তাদের ছিল না। যারা স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি ছিল তাদের বেশির ভাগই ছিল বিহারি এবং মুসলিম লীগার।
এবার আসি স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সংবিধান মোতাবেক নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের নয়। তিনি অসাংবিধানিকভাবে প্রথমে রাষ্ট্রপতি এবং পরে নিজেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন। এর পর পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্যদের দিয়ে ১৯৭২ সালে সংবিধান রচিত হয় এবং সেই সংবিধানটি ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদে পাস হয়। পরে সংবিধানের চরম লঙ্ঘন করে ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন কায়েম করে শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী থেকে জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়াই রাষ্ট্রপতি হয়ে যান এবং আজীবন রাষ্ট্রপতি থাকার ব্যবস্থা করেন।
আমরা যদি বিএনপির ইতিহাস দেখি, সেটিও খুব সুখকর নয়। অন্তত ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সর্বতোভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করে। সে সময় মাগুরার উপ-নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির কারণে তখনকার বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী মিলে প্রায় ১৭৩ দিন হরতাল দেয়। পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস করতে বাধ্য হয় বিএনপি। এর পর ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে অনেক কিছু করেছে। যেমন- বিএনপিপন্থী প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বানানোর জন্য ২০০৪ সালে সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর থেকে ৬৭ বছর করে। যেটা অবশ্যই ইতিহাসে একটি খারাপ উদাহরণ হয়ে থাকবে।
আজ যখন বলা হচ্ছে, জামায়াতকে ক্ষমতায় আসতে হলে ১৯৭১-এর ভ‚মিকার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে- তখন কেউ তো এমনও বলতে পারে যে, বিএনপিকে ১৯৯৬ সালে গণতন্ত্র ধ্বংসের চেষ্টা এবং ২০০৬ সালে জরুরি অবস্থার পরিবেশ তৈরি করে এক-এগারোর সরকার আনার কারণে রাজনীতিতে ফেরার আগে জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তারা আগের ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি করবে না।
আরেকটি বিষয়। একাত্তরের মুক্তি আন্দোলনের সাথে ২০২৪-এর মুক্তি আন্দোলনের চরম মিল আছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী লীগ দল হিসাবে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও সে সময়ের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সবচেয়ে বড় দল হিসেবে স্বাধীনতার পর তারাই স্বাধীনতার সুফল শতভাগ ভোগ করেছে। একইভাবে ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বিএনপি সরাসরি ঘোষণা দিয়ে অংশগ্রহণ না করলেও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর তারাও বড় দল হিসেবে এর পুরো কৃতিত্ব নিতে চাচ্ছে। এখানেই আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে মিল। আরেকটি মিল হচ্ছে মুসলিম লীগ যেভাবে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে একইভাবে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগও হয়তো একদিন পুরোপুরি বিলীন হয়ে যাবে।
এবার আসি যুদ্ধাপরাধীদের প্রসঙ্গে। যুদ্ধাপরাধী তাকেই বলা হয়, যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের উপর গণহত্যা চালায়। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যখন বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে তখন সেই বিভক্তি ঠেকানোর জন্য রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করলে সেটাকে যুদ্ধাপরাধ বলে না। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৯০ হাজার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বন্দী অবস্থায় ভারতে যায়, ভারত সরকার কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অথবা নিজস্ব কোনো বিচার ব্যবস্থায় কখনোই যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ নিয়ে আসেনি। তা হলে তাদের সহযোগীদেরকে কেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে যুদ্ধাপরাধী হতে হবে? কেন তাদের সাজানো বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারিক হত্যা করা হবে?
কাজেই আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে মেজর ডালিমের মতো আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধাই বলবেন যে, দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামী ’৭১ সালে যে ভূমিকা নিয়েছিল তা সময়ের বাস্তবতায় যথার্থ ছিল।
আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য; তা হচ্ছে ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী প্রধান দল ছিল না। তখনকার নেতৃস্থানীয় দল ছিল মুসলিম লীগ। পিস কমিটির প্রধান ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান, যিনি পরে জিয়াউর রহমানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গোলাম আযমের মতো নেতৃস্থানীয় জামায়াত সদস্যরাও আসলে আজিজুর রহমানের অধীনে কাজ করেছেন। আজ বিএনপির মতো রাজনৈতিক দল যখন বারবার জামায়াতের ওপর রাজাকারের তকমা লাগায়, তখন মনে হয় তারা তাদের সেই অতীত ভুলে গেছে যে, মূলত বিএনপিই ছিল তথাকথিত রাজাকারদের পুনর্বাসন কেন্দ্র।
২০১৯ সালের এক জরিপে দেখা যায়, ১০ হাজার রাজাকারের মধ্যে আট হাজারেরও বেশি ছিল আওয়ামী লীগে। অথচ জামায়াতে রাজাকারের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। পরে সেই জরিপ কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। সুতরাং আমরা আগেও দেখেছি কোনো রাজাকার আওয়ামী লীগে জয়েন করলে সে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায়। ঠিক তেমনি আজ বিএনপিও এমন এক মেশিনে পরিণত হয়েছে যেখানে রাজাকার ঢুকলে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায় এবং ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারাই আজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী। অথচ বর্তমান প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান কোনো ফ্যাক্টরই নয়, আমাদের সন্নিহিত শত্রু হচ্ছে ভারত। কাজেই যারা ভারতপ্রেমী তারাই আজকের দিনের সত্যিকারের রাজাকার তথা দেশবিরোধী।
উল্লেখ করা দরকার, দল হিসাবে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি। প্রবাসী সরকার আওয়ামী লীগের মুখপাত্র ছিল না। শেখ পরিবারের অনেক সদস্য যারা ভারতের তৈরি মুজিব বাহিনীর অংশ ছিল তারা সরাসরি তাজউদ্দীন সরকারের বিরোধী ছিল।
এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা বোঝাতে চাইছি যে, একটি স্বাধীন দেশের ভৌগোলিক বিভাজনের বিপক্ষে থাকা আর যুদ্ধাপরাধ এক নয়। কারো বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে গণহত্যার অভিযোগ প্রমাণ না হলে তাকে মানবতাবিরোধী অপরাধী বলে চিহ্নিত করা নিছক মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়। দেশের জনগণ হয়তো একদিন সঠিক ইতিহাস অনুধাবন করবে।
লেখক : সাবেক সেনা কর্মকর্তা