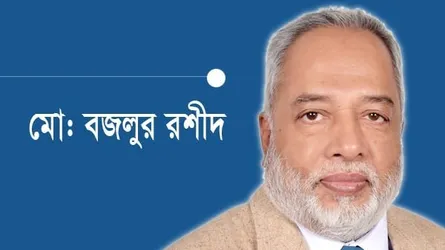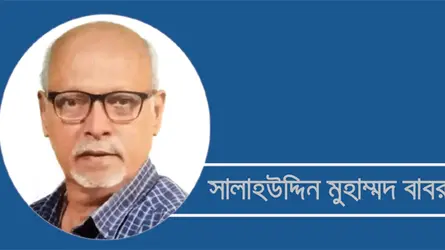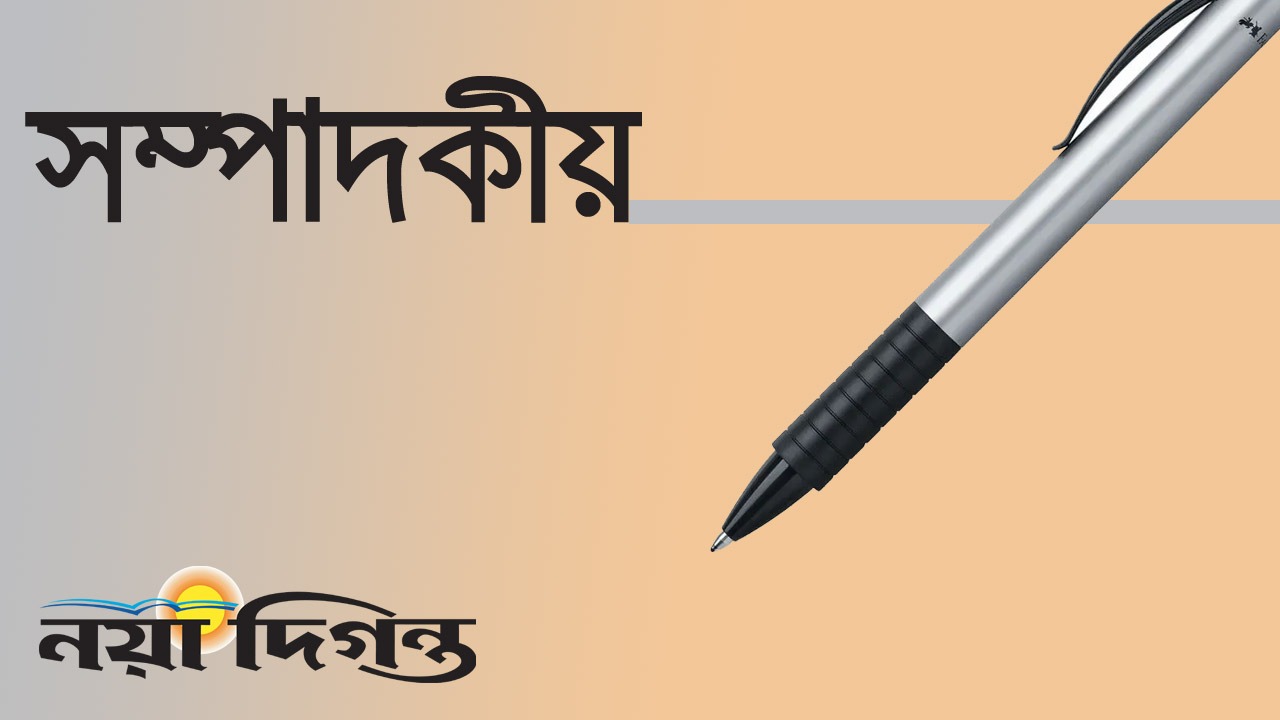বাংলাদেশ ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। এর প্রধান কারণ- ভৌগোলিক এবং টেকটোনিক প্লেটগুলোর সংযোগস্থলে অবস্থান। দেশের সিলেট, রাঙ্গামাটি, বান্দরবানের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কিছু এলাকা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, যেখানে ৭ দশমিক ৫ থেকে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ।
ভারতীয়, ইউরেশীয় ও মিয়ানমার মাইক্রো-প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশ। এ প্লেটগুলো সচল থাকায় এবং পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাওয়ায় এখানে সবসময় ভূতাত্তি¡ক চাপ (জিওলজিক্যাল স্ট্রেস) তৈরি হচ্ছে, যা বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় ও ইউরেশীয় প্লেট হিমালয়ের পাদদেশে আটকা পড়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে বড় ধরনের নড়াচড়া হয়নি। এ সঞ্চিত শক্তি যেকোনো মুহূর্তে মুক্ত হলে রিখটার স্কেলে ৮ বা এর বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে।
বাংলাদেশ বা এ ভূখণ্ডে বড় ভূমিকম্পের মধ্যে আছে ১৭৬২ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৮ দশমিক ৫। এটি ‘গ্রেট আরাকান আর্থকোয়েক’ নামে পরিচিত। এর ফলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ফেনী, এমনকি কুমিল্লা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এরপর ১৮৯৭ সালে আসামে সংঘটিত ভূমিকম্প ছিল ৮ দশমিক ৭ মাত্রার। ১৯১৮ সালে সিলেটের বালিসিরা উপত্যকায় ৭ দশমিক ৬ মাত্রায় এবং ১৯৩০ সালে আসামের ধুবড়িতে ৭ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়।
অতীতের ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার প্রবণতা থেকে দেখা গেছে, বড় ভূমিকম্পগুলো সাধারণত ১৫০ বছর পরপর ফেরার আশঙ্কা থাকে। এদিক থেকে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পগুলো ফেরত আসার সময় হয়ে গেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। লক্ষণীয়, দেশে গত কয়েক বছরে ছোট ও মাঝারি ভূমিকম্পের ঘটনা বড় ভূমিকম্পের দিকে নির্দেশ করে। তার আলামত মিলেছে গতকাল শুক্রবারের ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে। অবস্থা এমন হয় যে, এক ভূমিকম্প কাঁপিয়ে দিয়েছে গোটা বাংলাদেশকে। গতকাল সকালের এ ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিকে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ বলা হচ্ছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে গতকালের ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। মার্কিন ভূতাত্তি¡ক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) মাত্রা দেখিয়েছে ৫ দশমিক ৫। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদীতে, ভূ-পৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। এমন ভূমিকম্পের শঙ্কা বিশেষজ্ঞরা আগেই প্রকাশ করে আসছিলেন। এ ভূমিকম্প বাংলাদেশের জন্য সজাগ হওয়ার বার্তা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
ঢাকা শহরে মোট ২১ লাখ ভবন আছে। এর মধ্যে ছয় লাখ ভবন ছয়তলার উপরে। বাকিগুলো ছয়তলার নিচে। বড় ভূমিকম্প হলে এই ছয় লাখ ভবন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকবে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। রিখটার স্কেলে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকার এসব ভবনের সব কিছু ভেঙে পড়ার আশঙ্কা আছে।
রানাপ্লাজা ধসের পর দেশের গার্মেন্টস ভবনগুলো পরীক্ষা করে ভালো বা খারাপ নির্ণয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একইভাবে এখন রাজধানীর ভবনগুলো পরীক্ষা করতে হবে। কারণ, অনেক ভবন বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ করা হয়নি। যেহেতু ভূমিকম্পের কোনো পূর্বাভাস পাওয়ার এখনো কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়নি; তাই ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সবসময় প্রস্তুতি থাকা অত্যাবশ্যক। যাতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।