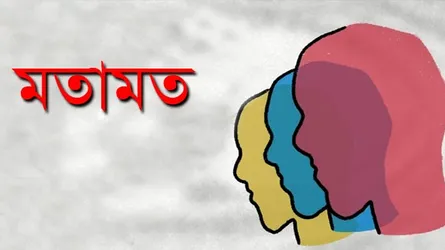কৃষি মন্ত্রণালয় দাবি করছে- “দেশে সারের ঘাটতি নেই।” কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কৃষকরা বলছেন উল্টো কথা। গত বোরো মৌসুমে বস্তাপ্রতি ২০০-৩০০ টাকা বেশি দিয়ে সার কিনতে হয়েছে, এবার আমন মৌসুমেও একই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে নন-ইউরিয়া সার (টিএসপি, ডিএপি, এমওপি) বাজারে অপ্রতুল।
সরবরাহ ও মজুদের অঙ্ক : কোথায় কমতি?
দেশে সারের বার্ষিক চাহিদা ৬০ লাখ টন। যার মধ্যে ইউরিয়া ২৭ লাখ টন (তুলনামূলক স্থিতিশীল) এবং নন-ইউরিয়া: টিএসপি, ডিএপি, এমওপি (সবচেয়ে বেশি সঙ্কট)। বর্তমানে সারের সরকারি মজুদ রয়েছে ৮.১৯ লাখ টন (গত বছর ছিল ১১ লাখ টন)।
সরকার বলছে নভেম্বর পর্যন্ত সমস্যা হবে না, কিন্তু বাস্তবে স্থানীয় পর্যায়ে সঙ্কট ও অতিরিক্ত দামে বিক্রি প্রমাণ করছে বাজারে কারসাজি হচ্ছে।
আমদানির চুক্তির ক্ষেত্রে কাগজে অগ্রগতি থাকলেও বাস্তবে বিলম্ব হচ্ছে। সরকার আট দেশের সাথে নন-ইউরিয়া আমদানির চুক্তি করেছে। এর মধ্যে মরক্কো ৬.৩ লাখ টন টিএসপি, ৪.৮ লাখ টন ডিএপি; সৌদি আরব ৬ লাখ টন ডিএপি; কানাডা ৫.২ লাখ টন এমওপি; রাশিয়া ৪.৫৫ লাখ টন এমওপি; চীন, তিউনিসিয়া, মালয়েশিয়া থেকেও চুক্তি রয়েছে।
সমালোচনা হচ্ছে মালয়েশিয়া নিজে সার উৎপাদন করে না, তবুও তাদের মাধ্যমে আমদানির চুক্তি করা হয়েছে। এতে কমিশনভিত্তিক কারসাজির অভিযোগ উঠছে।
বাড়তি দামে আমদানি : কে লাভবান?
২০২৩ সালে মরক্কো থেকে টিএসপি ও ডিএপি আনা হয়েছিল যথাক্রমে ৩৮০ ও ৪৭৮ ডলার/টন দরে। কিন্তু ছয় মাস বিলম্বে একই সার প্রায় ১০০ ডলার বেশি দামে আমদানি হয়েছে।
এ ছাড়া ডিসকাউন্ট কমিয়ে ১০ ডলার থেকে ৭ ডলার করা হয়েছে, যার ফলে সরকারকে বাড়তি ৩০ লাখ ডলার ব্যয় করতে হচ্ছে।
বেসরকারি খাতে আমদানি : স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন
কৃষি মন্ত্রণালয় সম্প্রতি সাড়ে ৯ লাখ টন আমদানির অনুমতি দিলেও সাধারণ টেন্ডারের বদলে নিজস্ব দর প্রস্তাব করেছে। আমদানিকারকদের অভিযোগ- এভাবে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা দেয়া হচ্ছে, প্রতিযোগিতা কমছে।
কৃষকের বাস্তব চিত্র : নির্ধারিত দাম বনাম বাজারদর
সরকারি নির্ধারিত ৫০ কেজি ডিএপি সালের মূল্য ১০৫০ টাকা। বাস্তবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১৪০০ থেকে ১৭০০ টাকা।
নীলফামারী, ঝিনাইদহ, রংপুরসহ বিভিন্ন স্থানে ডিলারদের অবৈধ মজুদ ধরা পড়েছে। কৃষকরা ক্ষুব্ধ হলেও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ দেখা যাচ্ছে না।
ডিলারশিপ সিন্ডিকেট : সঙ্কটের মূল শেকড়
সার ডিলারশিপ মূলত এখনো দলীয় প্রভাবশালীদের হাতেই রয়েছে। একই পরিবারে রয়েছে একাধিক লাইসেন্স। রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। কৃষকের কাছ থেকে বাড়তি দাম আদায় করছে এই সিন্ডিকেট।
বিশ্লেষণ : সঙ্কটের তিনটি প্রধান কারণ
১. আমদানিতে বিলম্ব ও অস্বচ্ছতা- বাড়তি দামে ক্রয় ও মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব।
২. নীতিগত জটিলতা- প্রতিযোগিতাহীন আমদানির অনুমোদন।
৩. সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ- রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ডিলার নেটওয়ার্কের কারসাজি।
ভবিষ্যৎ শঙ্কা
নভেম্বর-মার্চ হলো সারের পিক সিজন। যদি এর মধ্যে সঙ্কট সমাধান না হয় তাহলে কৃষি উৎপাদন ব্যয় বাড়বে, ধানসহ খাদ্যশস্যের দামও বাড়বে। আর কৃষক ও ভোক্তা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে
করণীয় : এখনই পদক্ষেপ জরুরি
বিশেষজ্ঞদের মতে, সারের ইস্যুতে এখনই কিছু পদক্ষেপ নেয়া দরকার। এর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক দর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বচ্ছ আমদানি; ডিলারশিপে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তি; স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নজরদারি এবং বেসরকারি খাতে খোলা প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা।
সার সঙ্কট কেবল কৃষি নয়, খাদ্যনিরাপত্তা ও জাতীয় অর্থনীতির হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে কৃষকের ক্ষোভ আরো বাড়বে, আর তার প্রভাব পড়বে বাজার ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতায়।