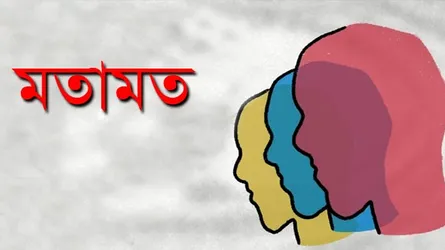বাংলাদেশের তৈরী পোশাক (আরএমজি) খাত দেশের মোট রফতানি আয়ের প্রধান উৎস হলেও মাত্র কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা খাতটির টেকসই অগ্রগতিকে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ফেলছে। যদিও বাজার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বৈচিত্র্য ও উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদনে মনোযোগ দিলে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে আরো প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে এবং আগামী কয়েক বছরে রফতানি আয়ের নতুন দিগন্ত খুলতে পারে।
বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে (২০২৪-২৫) দেশের পোশাক রফতানি আয়ের প্রায় ৮০.৮২ শতাংশ এসেছে মাত্র পাঁচটি পণ্য থেকে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে ট্রাউজার, টি-শার্ট, শার্ট, সোয়েটার ও অন্তর্বাস। সামগ্রিকভাবে নিট ও ওভেন পোশাক রফতানি থেকে গত অর্থ বছরে আয় হয়েছে ৩৯.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে পাঁচটি পণ্যের অবদান ৩১.৮০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ৩০টিরও বেশি ধরনের পোশাক রফতানি করলেও অল্প কয়েক ধরনের পণ্যেই আয়ের বেশির ভাগ নির্ভর করছে।
তথ্যে দেখা যায়, ট্রাউজার থেকে এসেছে ১২.৯৮ বিলিয়ন ডলার, টি-শার্ট থেকে ৮.৫৪ বিলিয়ন, সোয়েটার থেকে ৫.০৫ বিলিয়ন, শার্ট ও ব্লাউজ থেকে ৩.০৪ বিলিয়ন এবং অন্তর্বাস থেকে ২.১৭ বিলিয়ন ডলার। এর আগে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ পাঁচটি পণ্য থেকে আয় হয়েছিল ২৪.৪৯ বিলিয়ন ডলার, যেখানে মোট আরএমজি রফতানি আয় ছিল ২৮.০৯ বিলিয়ন ডলার।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাংলাদেশের পোশাক খাত মূলত তুলাভিত্তিক সাধারণ পণ্য উৎপাদন করে। অথচ বৈশ্বিক বাজারে দ্রুত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে কৃত্রিম আঁশ (ম্যানমেড ফাইবার বা এমএমএফ) ভিত্তিক পোশাকে। বর্তমানে বিশ্ববাজারে প্রায় ৭০ শতাংশ চাহিদাই এমএমএফভিত্তিক পণ্যের জন্য, অথচ বাংলাদেশ এখনো ৭০-৭৫ শতাংশ রফতানি তুলাভিত্তিক পোশাকের ওপর নির্ভরশিল।
বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান সতর্ক করে বলেন, বৈশ্বিক প্রবণতার সাথে বাংলাদেশকে তাল মেলাতে হবে। ভিয়েতনামের মতো প্রতিযোগীরা ইতোমধ্যে উচ্চমূল্যের এমএমএফ পোশাকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে আমাদের এখনো সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।
বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলি শামীম এহসান বলেন, আমরা মূলত সাধারণ পণ্য উৎপাদন করি। এর ফলে বৈশ্বিক চাহিদার তুলনায় বেশি উৎপাদনক্ষমতা তৈরি হয়েছে, যা দামের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন, “যদিও স্থানীয় কাঁচামাল ও অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার করে দেশের ভেতরে মূল্য সংযোজন বেড়েছে, তবে মুনাফার দিক থেকে মূল্য সংযোজন কমেছে। ফলে রফতানিকারকদের আয়ে সরাসরি চাপ পড়ছে বলে তিনি জানান।
বাংলাদেশের পোশাকের গড় ফ্রি অন বোর্ড (এফওবি) মূল্য দাঁড়ায় প্রতি পিসে ছয়-আট ডলার। অন্য দিকে কাট অ্যান্ড মেক (সিএম) অর্থাৎ কেবল সেলাইয়ের কাজ থেকেও কিছু ক্ষেত্রে ১২-১৫ ডলার আয় হয়। তবে বৈশ্বিক বাজারে এমন অনেক পণ্য রয়েছে, যেগুলো থেকে প্রতি পিসে ৩০ ডলার পর্যন্ত সিএম পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশ এখনো সেই উচ্চমূল্যের পণ্যে প্রবেশ করতে পারেনি।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কৃত্রিম আঁশভিত্তিক পোশাক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে। বর্তমানে দেশে মাত্র ১৯টি সিনথেটিক স্পিনিং মিল রয়েছে, যার মধ্যে আটটি অ্যাক্রিলিক। ফলে দেশের এমএমএফ সুতার চাহিদা পূরণ হয় না। এজন্য চীন ও ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ সুতা ও আঁশ আমদানি করতে হয়।
টেক্সটাইল খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে এবং বৃহত্তর বাজার অ্যাক্সেস ও শুল্কজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে এমএমএফ ও মিশ্র সুতা উৎপাদনে বিনিয়োগ অপরিহার্য। তবে আশার কথা হলো, বৈচিত্র্য আনার প্রচেষ্টা ধীরে হলেও এগোচ্ছে। বিশেষত ডেনিম, ডাইং ও ওয়াশিং সেগমেন্টে কিছু অগ্রগতি হয়েছে। গত এক দশকে পোশাক রফতানির শীর্ষ পাঁচ পণ্যের তালিকাতেও পরিবর্তন এসেছে। এর মধ্যে অন্তর্বাস/লাঞ্জারি নতুনভাবে প্রবেশ করেছে, যা ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।
সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ করপোরেশন (আইএফসি) ও বহুপক্ষীয় বিনিয়োগ গ্যারান্টি এজেন্সির (মিগা) এক যৌথ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ যদি অপ্রচলিত বাজারে প্রবেশ করে এবং কৃত্রিম আঁশভিত্তিক পোশাক উৎপাদনে জোর দেয়, তবে ২০২৯ সালের মধ্যে বছরে ৯৪ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত রফতানি আয় করতে পারবে। এই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতি বছর গড়ে ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন হবে। এজন্য বাণিজ্য, শিল্প ও আর্থিক খাতে সমন্বিত সংস্কার অপরিহার্য বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
বর্তমানে দেশের মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৮১.৫ শতাংশ পোশাক খাত থেকে আসে। এ খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা না গেলে সামগ্রিক রফতানি আয়ও ঝুঁকির মুখে পড়বে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, এখনই কার্যকর নীতি সহায়তা, কাঁচামাল উৎপাদনে বিনিয়োগ এবং নতুন বাজার অনুসন্ধানের উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হুমকির মুখে পড়বে।