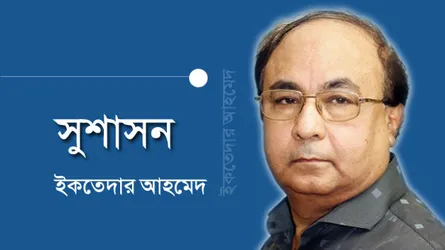বিশেষ সংবাদদাতা
বাংলাদেশের সামনে এখন এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মাইলফলক- মধ্য ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন। ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিষ্ঠার পর এ নির্বাচনকেই দেখা হচ্ছে গণতন্ত্র পুনর্গঠনের প্রথম বাস্তব পরীক্ষা হিসেবে। কিন্তু প্রশ্ন এখন একটাই : এই নির্বাচন কতটা মুক্ত, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক হবে?
বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তিগত স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এবং জনগণের প্রত্যক্ষ তদারকি প্রয়োজন।
প্রযুক্তিগত স্বচ্ছতা আস্থার প্রথম ধাপ : নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রথমেই কাজ আসে ভোটার তালিকার পূর্ণাঙ্গ যাচাই- মৃত ও ডুপ্লিকেট ভোটার অপসারণ এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যের সাথে সমন্বয় করা। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।
ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত এখনো নেতিবাচক। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে সফটওয়্যার অডিটের আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে কাগজভিত্তিক ব্যালটে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কাগজের ভোটকে কম্পিউটারে গণনা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে- যেটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে করা হয়েছে।
ফলাফল ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি কেন্দ্রে ভোট শেষে ফর্ম-৯ থেকে ফর্ম-১২ পর্যন্ত ডিজিটাল স্ক্যান ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করলে কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল পরিবর্তনের সুযোগ রোধ করা সম্ভব হবে। একই সাথে, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও লাইভ ফিড জেলা নির্বাচন কার্যালয়ে পাঠানো এবং ভোট গণনার সময় জনসম্মুখে ফলাফল প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখার দাবিও জোরালো হচ্ছে। সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে ২০ হাজার টাকা খরচ হওয়ার কথা। এতে সারা দেশে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হলেও এ অর্থ স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য খুব বেশি নয়। এ ছাড়া দায়িত্ব পালনরত পুলিশের বডি ওর্ন ক্যামেরার কথা বলা হয়েছে। এর ব্যবস্থা করা হলে যদি ঘটনার দিকে বডি ক্যামেরা তাক না হয় তাতে ওই রেকর্ডে কোনো লাভ হবে না।
প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা : আস্থার কেন্দ্রে রাষ্ট্রযন্ত্র : বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভোটের আগে ডিসি, এসপি, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ইউএনও, ওসি ও থানা নির্বাচন অফিসার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের রদবদল অপরিহার্য। এই রদবদল লটারির ভিত্তিতে করা যেতে পারে। এরপর ঘোষণা থাকতে হবে যে, এসব কর্মকর্তা নির্বাচনের পর নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকবেন না। এটি করা হলে নির্বাচনের সাথে যুক্ত এসব কর্মকর্তাকে অসাধু প্রার্থীরা ম্যানেজ করতে পারবেন না। অনেকে বিকল্প হিসেবে ভোটকালীন দায়িত্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, শিক্ষক বা অভিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্মকর্তার মতো অরাজনৈতিক প্রশাসককে রাখারও প্রস্তাব করেছেন। তবে এ নিয়ে অনেকে একমত না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
যেসব কর্মকর্তা ভালো নির্বাচন করবেন তাদের জন্য পুরস্কার এবং যারা ভালো করতে পারবেন না তাদের জন্য নির্বাচনোত্তর তিরস্কারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
ভোটের দিন নিরাপত্তা নিশ্চিতে সামরিক বাহিনীকে সহায়ক শক্তি হিসেবে রাখা যেতে পারে। আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বল প্রয়োগের আশঙ্কা রয়েছে এমন ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে ন্যূনতম তিন থেকে পাঁচজন সেনাসদস্যের প্রহরা মোতায়েন করা যেতে পারে। এ ধরনের কেন্দ্র দখল করে ভোটের সার্বিক ফল পরিবর্তনের অনেক নজির অতীতে দেখা যায়। সেনাসদস্য থাকলে সীমান্ত ও সঙ্ঘাতপ্রবণ এলাকায় ভোটকেন্দ্র দখল বা সহিংসতা ঠেকানো সহজ হবে।
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পর্যাপ্ত সদস্য না পাওয়ার আশঙ্কা করা হলে সেক্ষেত্রে একাধিক দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যে সেটি করা হয়।
নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহি ও জনতদারকি : নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে জনস্বচ্ছতা ও তদারকি বাড়াতে ইলেকশন মনিটরিং সেল গঠনের প্রস্তাব এসেছে। এই সেলে থাকবে মিডিয়া প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। কমিশনের প্রতিদিনের নির্দেশ, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও ভোটের অগ্রগতি লাইভ ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে জনগণের সামনে প্রকাশ করা গেলে আস্থা বাড়বে।
এ ছাড়া সব নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের জন্য নির্বাচনী কর্তব্য পালনে শপথের চালুর প্রস্তাব এসেছে, যাতে তারা পক্ষপাতহীনতার অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন।
আইনি কাঠামো ও নির্বাচনী সংস্কার : নির্বাচনের আগে আরপিও-এ সংশোধন এনে ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট ভর্তি বা অর্থ প্রভাবে ভোট কেনাবেচার দায়ে দ্রুত শাস্তির বিধান জরুরি। একই সাথে প্রতিটি দলের জন্য গণমাধ্যমে সমান সময় ও প্রচার সুযোগ আইনগতভাবে নিশ্চিত করা উচিত।
নির্বাচন-পরবর্তী বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল চালুর প্রস্তাবও এসেছে, যা ৯০ দিনের মধ্যে রায় প্রদানে বাধ্য থাকবে।
রাজনৈতিক সংলাপ ও আস্থার পুনর্গঠন : প্রযুক্তি বা প্রশাসনের পাশাপাশি আস্থার মূল ভিত্তি হলো রাজনৈতিক ঐকমত্য। বিশ্লেষকরা মনে করেন, ‘জুলাই সনদ’-এর নির্বাচন অধ্যায় বাস্তবায়ন এবং দলগুলোর মধ্যে জাতীয় সংলাপ আয়োজনই এই আস্থা ফেরাতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকার সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে মতবিরোধ মিটিয়ে সরকারের কাছে আসার কথা বলেছে। এতে ব্যর্থ হলে সরকারের একতরফা সিদ্ধান্ত ঘোষণায় কিছু বলার থাকবে না।
আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচন কেবল ক্ষমতার প্রতিযোগিতা নয়, এটি গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের পরীক্ষাও বটে। স্বাধীন প্রশাসন, স্বচ্ছ প্রযুক্তি ও জনগণের সরাসরি তদারকি- এই তিন স্তম্ভেই টিকে থাকবে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন। আগামী মধ্য ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন যেন সত্যিকার অর্থে মুক্ত, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক হয়- সে লক্ষ্যে এখনই জরুরি কারিগরি, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয়ার দাবি উঠেছে নাগরিক সমাজ ও নির্বাচনী বিশ্লেষকদের পক্ষ থেকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল রাজনৈতিক সদিচ্ছা নয়, একটি নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক কাঠামোই নিরপেক্ষ ভোটের ভিত্তি গড়ে দিতে পারে।
একজন সিনিয়র নির্বাচন বিশ্লেষকের ভাষায়- ‘মুক্ত নির্বাচন একদিনে তৈরি হয় না; এটি প্রস্তুতির ফসল। ফেব্রুয়ারির ভোটের আগে সেই প্রস্তুতির সময় এখনই।’