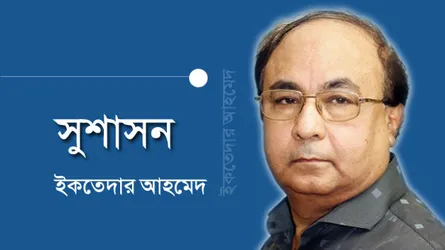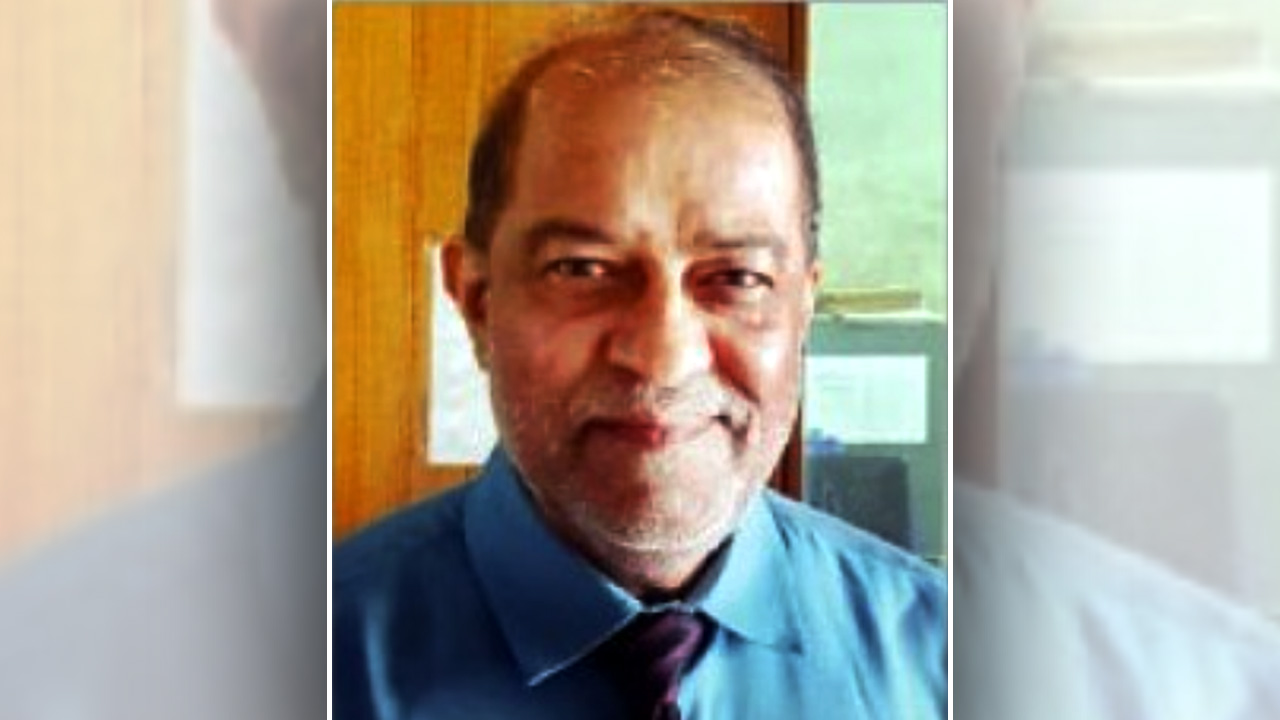ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের প্রধান এবং ইন্সটিটিউট অফ ইসলামিক ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স এন্ড ইকনোমিক্সের ডিরেক্টর, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক বলেছেন, দেশ নির্বাচনের দিকে আগাচ্ছে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হলে নতুন একটা ডাইনামিক্স তৈরি হবে ইনশা’আল্লাহ। সংস্কার এবংবিচার অগ্রাধিকার পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এবং সংষ্কারের জন্য কিছুটা স্পেস দেয়া হলেও, জাতির প্রত্যাশা পূরণ করে প্রাসঙ্গিক বিচারের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে মনে হয় না এই অন্তর্বতীকালীন সরকারকে সময় বা সুযোগ দেয়া হবে। অনিবার্যভাবেই বর্তমান এই ‘হ্যান্ডিক্যাপ্ড’ সরকারকে নির্বাচনটা প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে দেয়াটাকেই সর্বাগ্রগণ্য হিসেবে নিতে হচ্ছে। অনেকগুলো জিনিস চাইলেও সরকার করতে পারবে না, অথবা করতে দেয়া হবে না।
তিনি বলেন, আমাদের গৌরবময় তরুণরা যারা দেশেরগণ অভ্যূত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছে তাঁদের কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক অঙ্গনে জুলাই-এর ভাবধারা ধারণ করবে এমন একটি সুসংগঠিত তৃতীয় বা বিকল্প শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু নিছক তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্য আর উদ্দীপনায় দেশ গঠন বা পরিচালনা হয় না। তাই একদিকে তাদেরকে যোগ্যতার দিক থেকে যেমন নিজেদের সমৃদ্ধ বা উপযুক্তভাবে গড়ে উঠতে হবে, তেমনি প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতাকেও নতুন বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে সম্পৃক্ত করতে হবে। তা না হলে তাঁদের এই ঐতিহাসিক এবং গৌরবময় অর্জনের ফসল জাতির ঘরে নাও উঠতে পারে।
ড. ওমর ফারুক বিদেশি আধিপত্যমুক্ত রাজনীতি গড়ে তোলার জন্যে নিজেদের স্বকীয়তা সৃষ্টি ও স্বাধীনচেতা আত্মসম্মান ধারণ করার ওপর জোর দিয়ে বলেন, এজন্যে নিছক কাঠামোগত, আনুষ্ঠানিকতা বা লেবেলের পরিবর্তন নয়, আমাদের অপরিহার্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ‘সংস্কৃতি’র পরিবর্তন। শুধু রক্ত দিয়ে, সংগ্রাম করে যে অর্জন আসে তা টেকসই করা যাবে না যদি না আমরা স্বাধীনচেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারি, নিজেদের বিকশিত করতে না পারি।
নয়া দিগন্তকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে অধ্যাপক মোহাম্মদ ওমর ফারুক এসব কথা বলেন।
নয়া দিগন্ত : তরুণদের জন্যে আপনার পরামর্শ কি?
ওমর ফারুক : তরুণদের কমিটমেন্ট, সাহস, ত্যাগ আর এনার্জি থেকে তৈরী হওয়া মোমেন্টাম যেভাবে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনে কেন্দ্রীয়ভাবে ভূমিকা পালন করেছে, সেটা ধরে রাখা দরকার ছিল। অন্যরা যেমন নষ্ট করেছে, দুঃখজনক যেএই তরুণ প্রজন্মও সেটার অনেকটুকু অপচয় করেছে। বৈষম্যবিরোধী চেতনার ভিত্তিতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের এই কারিগররা সম্ভবত তাড়াহুড়া করে রাজনীতির অঙ্গনে এসে সুস্থ পলিটিক্সের একটি নতুন ধারা ও ঐতিহ্য গড়ার পরিবর্তে ‘পলিটিকিং’-এর পলিটিক্সে জড়িয়ে গেল।
এসব দিক থেকে গণ অভ্যুত্থানের প্রাণশক্তি, এই তরুণ প্রজন্ম অন্তর্ভুক্তিমুখী (ইনক্লুসিভ) ধারা রক্ষা করার পরিবর্তে আমাদের অসুস্থ রাজনীতিতে যা হয় সেই নোংড়ামী আর পংকিলতায় জড়িয়ে পড়ছে। আর এ কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জুলাইয়ের চেতনাটা তারা কতটুকু ধরে রাখতে পারছে এবং পারবে সেটা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। আসলে ভবিষ্যতে তাদেরকেই রোল প্লে করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মিসিং ফ্যাক্টর হচ্ছে যে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাখার যে কমন ডেনোমিনেটরগুলো সেগুলোর ভিত্তিতে কার্যকরী ঐক্য বজায় থাকা অপরিহার্য।
সংস্কার কমিশন যতটুকু এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পেরেছে, তা সত্বেও আমাদের জাতীয় ঐক্যের যে স্পন্দন আমরা ২৪-এর জুলাই-আগষ্টে দেখেছি তা অনেকটুকুই ক্ষীণ ও মলিন হয়ে এসেছে।
আগের মতই এই গৌরবময় তরুণ প্রজন্মের রাজনীতির অঙ্গনেও যদি জিরো-সাম খেলা চলে আর তাঁর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঐক্যের মূল ভাবধারাকে রক্ষা করা না যায়, তাহলে জাতির অনেক প্রত্যাশার আলোকে আমাদের ভবিষ্যত রচিত হবে কিনা তা আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে।
নয়া দিগন্ত : তার জন্যে তো পলিটিক্যাল উইজডম দরকার?
ওমর ফারুক : অবশ্যই দরকার। তরুণদের আরেকটা দুর্বলতা রয়েছে, যেটা একদিকে যেমন কিছুটা ফিলোসফিক্যাল, তেমনি বাস্তবিক। আল্লাহতায়ালা তো এক একটা জেনারেশনকে আলাদা আলাদা করে পাঠাননি। মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতাতেই এই দুনিয়াতে আমরা একসাথে কয়েকটি প্রজন্ম থাকি। তিন চারটা জেনারেশন দুনিয়াতে একসাথে থাকি, কাজ করি, বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাই। এবং তাদের সবারই দরকার আছে। তরুণদের মধ্যে যে পরিবর্তনটা আসল তাদের ত্যাগ, সাহস এবং অবদানে, তার মানে তো এইটা নয় যে শুধু তারাই দেশ চালাবে বা চালাতে পারবে, অথবা তারাই দেশের নেতৃত্ব দেবে। বুঝতে হবে আমাদের কোথায় কোন প্রজন্মের কি স্ট্রেন্থ।
বার্ধক্যে যেমন তারুণ্যের উদ্দাম এবং উচ্ছাস নেই, তেমনই তারুণ্যেরও জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে। এই জিনিসগুলোতে ভারসাম্য হতে হবে। সমন্বয় থাকতে হবে। এনসিপি’র যে ফেস জাতির সামনে, সেখানে তারা পুরোটাই ইয়াং জেনারেশন, এখানে ওল্ডার বা অভিজ্ঞ কোনো ফেস নাই। এভাবে তো একটা দেশ চালানোর মত ক্যাপাসিটি তৈরি হয় না। তারা যা অর্জন করেছে এবং তার ভিত্তিতে জাতিকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছে সেজন্য প্রজন্মগত দিক থেকে তাদের প্রয়োজন ছিল সঙ্গে ম্যাচিউর ব্যক্তিদেরও সম্পৃক্ত রাখা, যারা অন্তত তাদের সমর্থন দিতে পারবে, গাইড করতে পারবে, প্রয়োজনে ভুল ধরিয়ে দিতে পারবে।
আমাদের নিজেদের জানতে হবে যে কখন কোথায় আমরা আমাদের সর্বোত্তমটা দিতে পারব। প্রজন্ম হিসেবে সেটা প্রযোজ্য। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখন তার ‘বিদ্রোহী’ কবিতা লেখেন, মনে হবে যে তিনি একেবারেই অনন্তকালের যাত্রায় পারমানেন্টলি বিদ্রোহের মধ্যে ঢুকে গেছেন। কিন্তু আপনি শেষে যদি পড়েন সেখানে তিনি কখন শান্ত হবেন তা বলে দিয়েছেন। ‘আমি সেই দিন হব শান্ত …”। তিনি একদিন শান্ত হবেন যদি যে কারণে তাঁর বিদ্রোহ সে অবস্থার পরিবর্তনটা হয়। এখানে তারুণ্য-যৌবনের উদ্দামতা-নির্ভীকতার ভিত্তিতে বিদ্রোহের সাথে তার চিন্তা-স্বপ্নের ম্যাচিউরিটির শিক্ষণীয় প্রতিফলন ঘটেছে।
আমরা কখন রাজপথে থাকব, কখন ক্লাসে ফিরতে হবে, কখন আমাদেরকে মৃতপ্রায় প্রবীণদের ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে, আবার কখন তাদের নিয়ে সামনে এগুতে হবে, এই যে কখন, কি পর্যায়ে কি ভূমিকা পালন করতে হবে, কোনটার কোন জায়গায় কি কাজ, এগুলো সম্পর্কে প্রপার ম্যাচিউরড মূল্যায়নও থাকতে হবে। সবকিছু তারুণ্য ছাড়া যেমন হয় না, শুধু তারুণ্য দিয়েও হয় না। আমাদের সবাইকে লাগবে।
নয়া দিগন্ত : তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি নিজেদের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবার প্রস্তুতিও দরকার...
ওমর ফারুক : দেশের এই পরিবর্তনটার জন্যে আমরা অনেক সময় ধরে আশা করেছিলাম। দোয়া করেছি, চেয়েছি, যদিও জাতি হিসেবে তেমন কিছু করতে পারি নাই। কিন্তু এই দোয়া, আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশার পাশাপাশি যদি পরিবর্তন হয় তখন আমরা কি করব এটা নিয়ে কেউ ভাবেনি। কেউ প্রস্তুত ছিল না। সবাই পরিবর্তনের পর একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়েছে। পুরনো রাজনৈতিকগুলোর ব্যাপারে আমাদের যে ধরণের ঐতিহাসিক জঞ্জাল (ব্যাগেজ) আছে তা থেকে তারা কতটুকু নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে পারবে, তা জাতিকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু আমাদের নতুন বাংলাদেশে, নতুন ভবিষ্যত রচনায় নতুন, বিকল্প মুখ্য শক্তির দরকার আছে। এখন এনসিপি সেইটা কিনা তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে।
শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে এনার্জিটা তৈরি হয়েছিল সেটা অনেকটাই অপচয় হয়ে গেছে, তারপরও আমাদের নতুন জেনারেশনের দায়িত্ব আছে, তাদের সুযোগ আছে, আরো ম্যাচিউরড হয়ে কাজ করলে তারা ভবিষ্যতে দেশের জন্যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করতে পারবে।
কয়েকটা ফ্যাক্টর মনে রাখতে হবে।
প্রথমত, বাংলাদেশের ওপর ভারতের অশুভ ছায়া আছে, এই ছায়ায় যেই কাজ করবে, যারাই কাজ করবে তারা আসলে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্যে ভালো কিছু বিকল্প উপহার দিতে পারবে না। যদি এনসিপি ও অন্যান্য গ্রুপও ভারতসহ বিদেশী স্বার্থসংশ্লিষ্ট মৌলিক বিষয়ে কম্প্রোমাইজ করে, উদাসীন হয় তাহলে তাদের পক্ষে কাজ করা অসুবিধা হবে বা তারা শেষ পর্যন্ত পুরনো ফাঁদে পড়ে যাবে।
দ্বিতীয়ত, আমাদের পলিট্যিাকাল কালচারের পরিবর্তন দরকার। বেশিরভাগ পরিবর্তনের ভেতরে জীবনের বাস্তববোধ অনুপস্থিত। কোরআনে যেমন বলা হয়েছে শয়তানকে দোষ দিয়ে কেউ পার পাবে না। হাশরের ময়দানে অনেকে শয়তানকে দোষ দিয়ে পার পাবার চেষ্টা করবে যে সে আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। আমাদের দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের সমস্যা, দোষ ত্রুটিগুলো নিজেদেরই চিহ্নিত করতে হবে। সংশোধন করতে হবে। একটা জাতি যদি পরাধীন হতে না চায় তাহলে তাকে পরাধীন করে রাখা যায় না, তাদের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না।
এটা জাতীয় ব্যর্থতা যে ভারত আমাদেরকে এভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে। নেপাল বা শ্রীলঙ্কাকে তো করতে পারে নাই। এত স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি আর আমাদেরকেই তারা ব্যবহার করতে পেরেছে নিজেদের হীন স্বার্থ ও বিদ্বেষতাড়িত হয়ে। নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সংকল্প থাকতে হবে যে আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই কি না। সেই চাওয়া থেকে আমরা দিকনির্দেশনা পাব কেমন করে আমরা আগাতে চাই। এটা কেমন করে হয় যে একটা দেশের সামরিক-বেসামরিক অঙ্গনেরশীর্ষস্থানীয় পর্যায়ের ব্যাপারে অভিযোগ ওঠে যে তাঁদের মাঝে প্রাসঙ্গিক আত্মসচেতনা নাই, বিবেকবোধ নাই, আত্মসন্মান নাই, তারা অন্য একটা দেশের পদলেহী হয়ে কাজ করে। এমনি ভাবেই জাতির প্রভাবশালী সব গোষ্ঠিরকতটুকু নীচু মনমানসিকতা হলে এমন হয়! এগুলোর পরিবর্তন আসতে হলে যারা লিডারশিপে আছেন তাদের এক্সাম্পল সেট করতে হবে। আমাদের সামনে নতুন মডেল হয়ে আসতে হবে।
নয়া দিগন্ত : বিভক্তির সূত্রপাত হচ্ছে কিন্তু কিভাবে তা থেকে দূরে থাকা যায়?
ওমর ফারুক : শিক্ষার্থীদের নতুন এক্সাম্পল সেট করতে হবে। জুলাই আন্দোলনে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রোল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল জুলাই আন্দোলনের শেষের দিকে। কিন্তু যখন অভ্যূত্থানের পর আন্দোলনের নতুন রূপ দেওয়া শুরু হল, দেখা গেল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ ফ্রন্টফেসে নাই। আমরা তো ইনক্লুসিভ কালচার বিল্ড এবং ধারণ করার নতুন কালচার গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু সেটা করা হলো না। শুরুতেই সে ব্যাপারে আমাদের ভিশন, কমিটমেন্ট বা ম্যাচিউরিটির মৌলিক ঘাটতি দেখা গেল।
এরপরে পলিটিক্যাল ডায়নামিক্স দেখা গেল যে, ৭১-এর বিষয়টি বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে বিভাজনের হাতিয়ার হিসেবে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এই বৈষম্যবিরোধী গ্রুপগুলোও একই বিভাজনের রাস্তায় হাটা শুরু করেছে। সেই সাথে কারা আসলে জুলাইয়ের অর্জনের মাস্টারমাইন্ড তা নিয়ে নতুন জিরো-সাম গেম শুরু হয়েছে। নতুন দেশ গড়ার জন্যে ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তিগুলোর ইনক্লুসিভ ঐক্য খুবই জরুরি। কিন্তু বর্তমান বিভাজনের প্রবণতার পরও আমাদের মূল ধারায় থার্ড ফোর্সের দরকার আছে। এই ইয়াং ফোর্সের দরকার আছে।
আমি এখনো আশাবাদী এই জিনিসগুলো সামনে রাখলে ভবিষ্যত ভালো হতে পারে কিন্তু আমাদের সেল্ফ রিফ্লেকশন দরকার।
অন্যদের ভুল সহজে ধরতে পারি কিন্তু আমার নিজের কি ভুল থাকতে পারে সেটা অনুধাবণ এবং তা সংশোধনের দায়িত্ব নিতে হবে। বাস্তবতা এটাই যে নিজেকে এ্যাসেস করাটা খুব কঠিন।
সৌভাগ্যক্রমে যারা ইসলামে বিশ্বাস করি তাদের জন্য কোরআন এই শিক্ষাটাই দেয়।
সুরা নিসার ১৩৫ নম্বর আয়াতে সেটাই বলা হয়েছে যে, তোমরা সুবিচারের পক্ষে দাঁড়াও, যদিও তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটজন এমনকি নিজের বিপক্ষেও যায়।
নিজেদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়া করানো মানব সভ্যতায় এমন একটি সুউচ্চ মানদণ্ড যা আমরা ধারণ করতে পারি নাই। কিন্তু পারিনি বলেই পারব না তা তো বলা যাবে না।
নয়া দিগন্ত : তো অন্যদের দ্বারা মিসগাইডেড হওয়ার জন্যে তো জাতীয় জীবনে পিলখানা হত্যাকাণ্ড, শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের মত চরম মাশুল দিতে হয়েছে...
ওমর ফারুক : কিন্তু চরম মাশুল দিয়ে কি শিখলাম? এখনোতো দেখছি কিছু শিখি নাই। মূল প্রবলেম হচ্ছে এথিক্সের প্রবলেম। মৌলিক সমস্যা হচ্ছে, আমরা এমন কিছু অন্যকে বলব না যেটা আমরা নিজেরা করি না। আমাদের সে কনসিসটেন্সি নাই। শিক্ষকরা যে রাজনীতি করেন, তাদের যে দলীয় মানসিকতা তাতে শিক্ষার পরিবেশ কিভাবে থাকবে?
দলীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেবেন, সেটা যে দলেরই হোক না কেনো, এতে করে শিক্ষার পরিবেশ মেইনটেইন করা সম্ভব নয়। সেই দলীয়করণকে আবার নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করবেন তাও দলীয় স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে না।
সংস্কারের বিষয়টা শুধু স্ট্রাকচারের বিষয় নয় কালচারের বিষয়টাও আছে। এধরনের ছাত্ররাজনীতির একেবারেই বিরোধী আমি, আমেরিকায় ২৭ বছর ছিলাম ওখানে স্টুডেন্ট পলিটিক্স নেই তা নয় কিন্তু স্টুডেন্ট পলিটিক্স ইজ ফোকাসড অন স্টুডেন্ট রিলেটেড ইস্যুজ এন্ড নট এজ টুল্স অফ পলিটিক্যাল পার্টিজ। তারা ভিন্ন কোনো দেশের হয়ে, দলের হয়ে কাজ করে না, তারা স্টুডেন্টদের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এবং সেখানকার ফ্যাক্টর থাকে কে কত মেরিটোরিয়াস, তারা স্টুডেন্ট ইউনিয়নে ইলেকটেড হয়ে আসে, তারা এমার্জ হয়ে ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য বিকশিত হয়, তাদের অভিজ্ঞতা সিভিতে থাকে এটা ভিন্নরকম। আমাদের ছাত্ররাজনীতি ও জাতীয় রাজনীতির প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এত মারাত্মকধরনের দুর্বলতা রয়েছে- এটা কিন্তু শুধু যে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ তাদের মধ্যে আছে তা বলছি না, এটা ইসলামপন্থীদের মধ্যেও আছে। নীতিগতভাবে ছাত্ররাজনীতি এভাবে থাকা উচিত নয়।
নয়া দিগন্ত : রাজনীতিতে তো বিদেশি শক্তির প্রভাবও বেশ লক্ষ্যণীয়...
ওমর ফারুক : অবশ্যই। শুধু ভারতের কথা বলছি না, আমেরিকা আছে, চীনের বিষয় একটু ডিফারেন্ট, চীন প্রভাব ফেলে কমার্শিয়াল ইন্টারেস্টের মাধ্যমে। ভারতের ফ্যাক্টর আমাদের জন্যে মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে আমেরিকার ফ্যাক্টর এ দু’টিকেই ব্যালান্স করতে গেলে আমাদের নিজেদের স্বকীয়তা ধারণ করেই করতে হবে। নিজেদের অবস্থানটা ধরে রাখতে হবে। শুধু বলব এত জীবন দিয়েছি, এত রক্ত দিয়েছি, এত কিছু হয়েছে, সেই স্বাধীনচেতা মনটা তো আমাদের নাই।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামেও ঘাটতি রয়েছে। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই মারাত্মক একটা গ্যাপ আছে। ইন্ডাস্ট্রি, এমপ্লয়মেন্ট ও শিক্ষার মধ্যে কোনো কানেকশন নাই। ইন্ডাস্ট্রির ডিমান্ডের বিপরীতে কি ধরনের জনশক্তি হিসেবে শিক্ষার্থীদের তৈরি করি তা প্রপারলি ফোকাস করা দরকার।
কোন কোন সেক্টরে কোন কোন কোয়ালিফিকেশনের লোকবল দরকার সেটা আগেভাগে জানা থাকলে তাদের আরো দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়। যাতে তারা জবমার্কেটে যেয়ে অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় যোগ্যতার সাথে উত্তীর্ণ হতে পারে। দেখা যাচ্ছে কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং, মার্কেটিং, ফাইনান্স পড়ে এসব বিষয় রিলেটেড কোনো জব পাচ্ছে না।
গত দুই দশকে আমাদের জব মার্কেট বা কর্মসংস্থানও অনেকটা ক্ষীণ হয়ে গেছে। যেভাবে প্রয়োজন ছিল নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রি সেভাবে সেটআপ হয় নাই। অবকাঠামো যা হয়েছে তাতে কর্মসংস্থান হয়নি। যেসব সেক্টরে তরুণদের কর্মসংস্থান বাড়বে সেগুলোর প্রপার কোনো বাস্তবায়ন হয়নি। তরুণদের যে শিক্ষা দিচ্ছি তা তার জীবনে যদি কাজে না লাগে আর সে এমন শিক্ষা যদি না পায় যাতে সে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে সেই তাৎপর্যটা হারিয়ে ফেলেছি। কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ল’ইয়ার হোক, মানুষ হতে না পারলে সে দেশকে নেতৃত্ব দেবে কিভাবে? যে সব দেশ এগুলো এ্যাডড্রেস করতে পেরেছে ওরাই কিন্তু দুনিয়াতে লিড দিচ্ছে।
আমরা সে সব বিষয়ে ফোকাস করি, এনার্জি ব্যয় করি, রিসোর্স ব্যয় করি এগুলো আসলে একটা সোসাইটির ডেভেলপমেন্টের জন্যে যথেষ্ট না। এমনকি একই আদর্শে বিশ্বাসীদের মধ্যে আকিদা নিয়ে, মাযহাব নিয়ে যতধরনের বিস্তর পার্থক্য এগুলো সেক্যুলার এবং ধর্ম্ববিদ্বেষীদের শক্তিশালী করেছে। এই বিভেদের সুযোগ নিচ্ছে বিদেশি শক্তিরাও। মৌলিক ব্যাপারে নিজেরা যেখানে ঐক্যবদ্ধ না, সেখানে যেন একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি। যখন আমরা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করত পারব, অভিন্ন লক্ষ্যের মানুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ রেখে পথ চলতে পারব, চিন্তাভাবনার পার্থক্যকে বিভাজনের হাতিয়ার হতে দেব না, আমরাও মানব সভ্যতার টেবিলে আমাদের সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করতে পারব, আমাদের হতভাগা জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তনে আমরা যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারব। ইনশা’আল্লাহ, আমাদের পারতেই হবে।