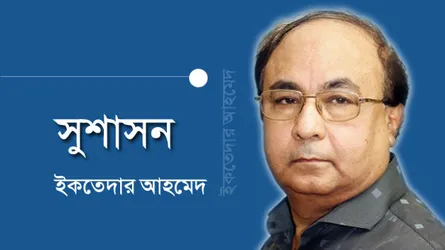ড. কাজল রশীদ শাহীন
বিশ^ ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ও অভাবিত ঘটনা হল ইতালীয় নবজাগরণ। যা ইউরোপীয় নবজাগরণ নামেও পরিচিত। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে ভারতবর্ষের অবিভক্ত বঙ্গেও একটা নবজাগরণ সঙ্ঘটিত হয়। যাকে বলা হয় বাংলার নবজাগরণ বা বঙ্গীয় নবজাগরণ। এই নবজাগরণের কালেই আরও একটি নবজাগরণ সেই সময়ের পূর্ববঙ্গে উন্মেষিত হয়ে বিকাশ ও পূর্ণতা পায়। আমরা এই নবজাগরণের নাম দিয়েছি বাংলাদেশের নবজাগরণ। আজকের বাংলাদেশই সেই নবজাগরণের উদ্গাতা। বাংলাদেশের নবজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র কাজী নজরুল ইসলাম। এই লেখা বাংলাদেশের নবজাগরণ ও নজরুলের অবদানকে একসূত্রে দেখার নিমিত্তে।
নবজাগরণ শব্দটা ইংরেজি রেনেসাঁ শব্দের বাংলা রূপ। রেনেসাঁকে কেউ কেউ ‘রেনেসন্স’ও বলেন, যেমন গোলাম মুরশিদ। রেনেসাঁ বা রেনেসন্স-এর সরাসরি বাংলা হলো পুনর্জাগরণ। আমরা এখানে পুনর্জাগরণ শব্দটাকে সরাসরি না নিয়ে নবজাগরণরূপে নিয়েছি, যা একটি বৃহৎ ক্যানভাস বা পাটাতনকে হাজির করে।
নবজাগরণ বলতে কী বোঝায়, আমরা কী বুঝছি। আমরা মনে করি, নবজাগরণ হলো কোনো ভুখণ্ড বা অঞ্চলের মানবসম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর মানুষের নতুন করে জাগরণ। যার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রশ্ন ও যুক্তিকে হাজির রেখে কোনো কিছু গ্রহণ বা বর্জন করার সংস্কৃতি। নবজাগরণের আলোয় সেই জাতি ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে শেখে যুক্তির নিরিখে। ঐতিহ্যের পথে হাঁটতে চাই নতুন বাতাবরণকে সাথে নিয়ে। তাদের তৈরি হয় বিজ্ঞানমনস্কতা। চর্চিত হয় ন্যায়বোধ। জাগরিত হয় সাম্য চিন্তা, মানবিক ভাবনা, সামাজিক ন্যায়বিচার। জাতীয়তাবাদের আদর্শে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে। স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়। গণতান্ত্রিক মন বিকশিত হয়। অপরকে আত্মীকরণ ও সাঙ্গীকরণের সংস্কৃতিতে ঠাঁই দেয়, বুঝে নেয়। নিজেকে বুঝে, অপরকে বুঝতে চায়, আলিঙ্গনের নিমিত্তে। প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশকে আপনার আলোয় আলোকিত করে। বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের মাঝে খুঁজে ফেরে নিজেকে। মোটাদাগে আমাদের নবজাগরণ ভাবনা এরকমই। বাংলাদেশের নবজাগরণ আসলে এ সবেরই মূর্ত প্রকাশ, সর্বৈবভাবে-সর্বোচ্চরূপে। এখন দেখা দরকার এই নবজাগরণের সাথে কাজী নজরুল ইসলামের যোগসূত্রতা, অবদান ও প্রভাবিত করার নোক্তা ও হরকতসমূহ।
জীবনের সব পর্যায়ে, সব লেখালেখিতে তা সাংবাদিকতা হোক, হোক সম্পাদকীয়তা। কিংবা গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, অভিভাষণ; সর্বত্রই তিনি বাংলাদেশের নবজাগরণকে ভাষা দিলেন, উচ্চকিত করলেন, সবার মাঝে হাজির করলেন প্রগাঢ়ভাবে। গানে গানে তিনি লিখলেন, ‘নমঃ নমঃ নমো বাঙলা দেশ মম/ চির- মনোরম চির-মধুর।/কোন নিরবধি বহে শত নদী/ চরণে জলধির বাজে নূপুর ॥ ... এই দেশের মাটী জল ও ফুলে ফলে,/ যে রস যে সুধা নাহি ভূমণ্ডলে,/ এই মায়ের বুকে হেসে খেলে সুখে/ ঘুমাব এই বুকে স্বপ্নাতুর।।’ কিংবা ‘মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।/ মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥/ এক সে আকাশ মায়ের কোলে/ যেন রবি-শশী দোলে,/ এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান ॥/ মোরা এক সে দেশের খাইগো হাওয়া, এক সে দেশের জল,/ এক সে মায়ের বক্ষে ফলে একই ফুল ও ফল। এক সে দেশের মাটীতে পাই/ কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই,/ মোরা এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান।।’ নজরুলের গানে রয়েছে, ‘আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান!/ মম চরণের তলে, মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান! ... জাপটি ধরিয়া বিধাতারে আজো পিষে’ মারি পলে পলে/ এই কালসাপ আমি, লোকে ভুল করে মোরে অভিশাপ বলে!’
দৃষ্টি দিই, নজরুলের সাংবাদিক জীবনে। যার প্রারম্ভে যুক্ত হন ‘নবযুগ’ পত্রিকার সঙ্গে। এখানে প্রকাশিত লেখাগুলো ‘যুগবাণী’ নামে যখন বই আকারে বের হওয়ামাত্রই- ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার তদানীন্তন সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। ‘নবযুগ’ বন্ধ হওয়ার পর নজরুল ‘সেবক’ পত্রিকার সাথে যুক্ত হন। ‘নবযুগ’ ও ‘সেবক’-এর অভিজ্ঞতায় নিজেই প্রকাশ করেন ‘ধূমকেতু’ পত্রিকা। এখানে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার নজরুলকে খুঁজে পাই প্রজ্ঞা ও সাহসে, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের গভীর প্রত্যয়ে, নবজাগরণের আলোয়।
কবিতায় বিশেষ করে ‘বিদ্রোহী’তে নজরুল যা উচ্চারণ করেছিলেন প্রতীক ও রূপকে, উপমা ও উৎপ্রেক্ষায়, মিথ ও পুরাণে ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় সাংবাদিক-সম্পাদক নজরুল সেই কথা বললেন একেবারে সরাসরি, কোনো প্রকার রাখঢাক ব্যতিরেকে। প্রথমবারের মতো পরাধীন ভারত থেকে উচ্চারিত হল সরাসরি স্বাধীনতার কথা। তিনি বললেন, স্বরাজ টরাজ বুঝি না, আমার স্বাধীনতা চাই।
৭ জানুয়ারি ১৯২৩-এ প্রেসিডেন্সি জেল, কলকাতায় কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, ‘আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্য স্বরূপ। ... আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনই অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে, কিন্তু কোনো কালে কোনো কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি - তার বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশি কেড়ে নিলেই সে বাঁশির সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আর এক বাঁশি নিয়ে বা তৈরি করে তাতে সেই সুর ফোটাতে পারি। সুর আমার বাঁশির নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশি সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশিরও নয় সুরেরও নয়; দোষ তার - যিনি আমার কণ্ঠে তার বাণী বাজান। সুতরাং, রাজবিদ্রোহী আমিও নই; প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বাণ-বাদক ভগবান। তাকে শাস্তি দিবার মতো রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাহাকে বন্দি করবার মতো পুলিশ বা কারাগার আজও সৃষ্টি হয় নাই।’ নবজাগরণের কবি বলেই এই উচ্চারণ সেদিন হাজির নাজিল করতে পেরেছিলেন নজরুল। তার এই লেখার মধ্যেই রয়েছে নবজাগরণ ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।
ঊনবিংশ শতকের বাংলায় সঙ্ঘটিত নবজাগরণ বিংশ শতকেও চলমান থাকে। পরাধীন ভারতবর্ষের ন্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে সেই নবজাগরণের পূর্ণতা পায়। বাংলার নবজাগরণ যখন চলমান তখন বঙ্গে আরও একটা নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে। এবং সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক নবজাগরণ। ঊনবিংশ শতকের শেষাশেষি এই নবজাগরণের বিভিন্নভাবে উন্মেষ হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে এই নবজাগরণ তার কাক্সিক্ষত লক্ষ্য অর্জন করে। এই নবজাগরণকে আমরা সংজ্ঞায়িত করেছি বাংলাদেশের নবজাগরণ নামে। কাজী নজরুল ইসলাম এই নবজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ এক মনীষা। এখানে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন, বাংলার নবজাগরণের সীমাবদ্ধতাই বাংলাদেশের নবজাগরণকে অনিবার্য করে তোলে।
বাংলার নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা হলো, এক. শুধু হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই নবজাগরণ। দুই. বাংলার নবজাগরণকে বাংলার নবজাগরণ বা বঙ্গীয় নবজাগরণ বলা হলেও এ নবজাগরণের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিন. বাংলার নবজাগরণ মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক এবং তার আশপাশের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। চার. বাংলার নবজাগরণ অবিভক্ত বঙ্গের সব প্রান্তের বিদ্বৎসমাজ ও সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমুখী ছিল না। পাঁচ. আয়তনিকভাবে অবিভক্ত বঙ্গের বড় একটা জনপদ পূর্ববঙ্গসহ দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গকে এ নবজাগরণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। ছয়. অবিভক্ত বঙ্গের মুসলিম জনসংখ্যা তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বা প্রায় কাছাকাছি হওয়ার পরও বঙ্গীয় নবজাগরণের সঙ্গে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য করার মতো সম্পৃক্ততা ছিল না। সাত. বঙ্গীয় নবজাগরণ বঙ্গের দুই প্রধান ধর্মগোষ্ঠীর মানুষের সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আগে ও পরে আশাপ্রদ কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। আট. বঙ্গের দুই প্রধান ধর্মগোষ্ঠীর হৃদয়ের বিভাজন রোধে কোনো প্রকার দফারফা করতে পারেনি। নয়. বাংলার নবজাগরণ জাতীয়তাবাদের স্বরূপ, বাস্তবতা ও প্রায়োগিকতা নিয়ে আশাব্যঞ্জক কোনো কিছু নির্মাণ করতে পারেনি। দশ. এ নবজাগরণ দেশ ভাগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেনি।
বঙ্গীয় নবজাগরণের এই সীমাবদ্ধতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো তিনটি সীমাবদ্ধতার কথা বলতে পারি, যা ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার বলেছেন। তিনি মনে করেন, এক. বাংলার নবজাগরণকে ‘বাংলার নবজাগরণ’ বলা হলেও এখানে পুরো বাংলাকে যুক্ত করা হয়নি। এটি ছিল মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক একটা নবজাগরণ। দুই. বাংলার নবজাগরণে মুসলমানদের সম্পৃক্ত করা হয়নি। নবজাগরণের নামে এটি ছিল মূলত হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণ। তিন. বাংলার নবজাগরণে পূর্ববঙ্গের সম্পৃক্ততা ছিল না। পূর্ববঙ্গকে এখানে উপেক্ষা করা হয়েছে।
আমাদের অনুসন্ধানে আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলার নবজাগরণ সর্বজনীন ছিল না। এমনকি লালন সাঁইয়ের মতো আলোকপ্রাপ্ত মনীষাকে বাংলার নবজাগরণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকি এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে আলোকপাত করার মতো গবেষণা নেই। কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের মতো সাংবাদিক-সম্পাদকও বাংলার নবজাগরণে নেই। যদিও অতি সম্প্রতি বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কিত একটা বইয়ে হরিনাথকে যুক্ত করা হয়েছে বিস্ময়কর হলেও সত্য, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের মতো নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃতের অবদানও বাংলার নবজাগরণে স্বীকৃত নয়। কাজী নজরুল ইসলামকেও বাংলার নবজাগরণে উল্লেখযোগ্য জ্ঞান করা হয় না। বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কিত গবেষণা ও লেখালেখিত কাজী নজরুল ইসলাম আজও উপেক্ষিত রয়েছেন। এর মধ্যে দিয়ে স্পষ্টত হয়, বাংলার নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা। স্পষ্টত হয় বাংলার নবজাগরণের মধ্যে দিয়ে কেন ও কোন প্রেক্ষাপটে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের নবজাগরণ।
আমরা মনে করি, বাংলাদেশের নবজাগরণের সূচনা ও ভিত্তিভূমি তৈরি হয় পূর্ববঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের একাংশ, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয়রা। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের অংশ হিসেবে জন্ম নেয় স্বদেশী আন্দোলন, স্বাদেশিকতা বোধ ও বিপ্লববাদ। যদিও এ আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে নানা ধরনের তর্ক জারি রয়েছে। কিন্তু এ আন্দোলনই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা, তা নিয়ে কোনো প্রকার দ্বিধা ও সংশয়ের অবকাশ নেই। বাঙালি জাতিয়তাবাদের উন্মেষকালেই দানা বেঁধে ওঠে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদই সর্বভারতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। তত দিনে জন্ম নিয়েছে দু-দুটো রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) ও সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ (১৯০৬)। বাংলায় জাতীয়তাবাদের এ চেতনা ক্রমেই প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। অবিভক্ত ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে কলকাতা থেকে দিল্লিতে যায়। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়।
দেশীয় ও বিশ^ রাজনীতির সেই উত্তুঙ্গ মুহূর্তে যুক্ত হয় বিশ্ব ইতিহাসের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অধ্যায়। এক. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ; যা ১৯১৪ তে শুরু হয়ে ১৯১৯-এ এসে শেষ হয়। দুই. রাশিয়ায় কমিউনিজমের জয়, যা বলশেভিক বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব হিসেবে সর্বজনমান্য। জারদের হটিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের শাসন ক্ষমতায় আবির্ভাব বিশ্ব ইতিহাসের মাইলফলক ঘটনাবিশেষ। তিন. জাতীয়তাবাদী নেতা ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে শুরু হয় আধুনিক তুরস্ক গড়ার আন্দোলন, পতন হয় অটোমান রাজতন্ত্রের বা সাম্রাজ্যের।
কবি নজরুল তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফেরত সৈনিক। আবাসিত হয়েছেন কলকাতায়। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে লিখলেন কালজয়ী কবিতা ‘বিদ্রোহী’। অ্যাকাডেমিশিয়ান, কবিতা প্রেমিকরা এ কবিতার প্রতীক, রূপক, উপম, উৎপ্রেক্ষা, মিথ, পূরাণ, ছন্দ, ভাষাভঙ্গি, শব্দ নির্বাচন, বাঙ্ময়তা, স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে অজস্র-অগণন কথা বলেছেন। আগামীতেও নিশ্চয় বলবেন। কিন্তু এ কবিতার মূল স্বর হলো জাতীয়তাবাদ। ‘বিদ্রোহী’ প্রধানত ও সর্বৈবভাবে জাতীয়তাবাদী কবিতা, যার অন্তর্গত অনুভবে ব্যক্ত হয়েছে দেশপ্রেমের সুর, বাংলাদেশের নবজাগরণের বীজমন্ত্রগুলো।
১৯২১-এর ডিসেম্বরে ‘বিদ্রোহী’ যে জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেছিল, ৪৭-এর দেশ বিভাগ ও ভারতভঙ্গ সেই জাতীয়তাবাদের কাক্সিক্ষত লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। বাঙালিকে বিভক্ত করা হয়েছে। হৃদয়ের বিভাজন ঘটিয়ে সেই ভাগকে কেবল পরিণত করা হয়নি, মান্যতাও দেয়া হয়েছে। বঙ্গীয় নবজাগরণের যে চ্যালেঞ্জ ছিল আঁতুড়ঘরেই। সেই চ্যালেঞ্জ উতরানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু ‘বিদ্রোহী’ কবিতার রচনাকালে যে নবজাগরণের বীজ রোপিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে, যে নবজাগরণের প্রথম পর্বের উন্মেষ ঘটেছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ‘শিখা’ পত্রিকাকে কেন্দ্রে রেখে। যে নবজাগরণের বিকাশ ঘটেছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে পুরোভাগে রেখে। দ্বিতীয় পর্বের এ নবজাগরণ ঢাকায় সংঘটিত হলেও এর সঙ্গে যুক্ত করেছিল পুরো দেশের মানুষকে। এক স্বর ও সুরে গেঁথেছি মাতৃভাষার ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার লড়াই। এ ন্যায্যতার প্রশ্নেই বাঙালি তার নবজাগরণের তৃতীয় পর্বে বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দেয়। ১৯২১-এ ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় আঁকা জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন পূরণ হয়ে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর।
নজরুল আগাগোড়াই একজন জাতীয়তাবাদী কবি, সাংবাদিক, সম্পাদক, লেখক, সাহিত্যিক, গীতিকার ও সুরকার। ওনার সৃজনসম্ভারের সবটাই নবজাগরণের আলোয় উদ্ভাসিত। নজরুলের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ এক সুলুকসন্ধান মেলে ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায়, যা অন্য কোনো সম্পাদক কখনো এভাবে ভেবে দেখিয়েছেন কি না সংবাদপত্রের ইতিহাস পাঠের অভিজ্ঞতায় আমাদের অনুসন্ধানে মেলেনি। পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা যে কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশ করত না। এ ব্যাপারে তাদের নীতি পাঠককেও অবহিত করা হয়েছিল। এসবের মূল লক্ষ্যই ছিল স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ। বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যাপারে তাদের ঘোষণা ছিল- এক. দেশের অনিষ্টকর কোনো বিলাতি বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। দুই. মদের বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন. অনাথ, বিধবা ও দেশের জন্য যাহারা জেল খাটিয়া আসিয়া সামান্য মূলধনের কারবার করিতেছেন, প্রয়োজন হইলে তাহাদের বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করা হইবে। ধূমকেতুর প্রাণ ছিল তার সম্পাদকীয়র মধ্যে। তার প্রমাণ মেলে একই সময়ে প্রকাশিত দ্বিভাষীয় পত্রিকা অমৃতবাজার-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে।
নজরুলের আপসহীন জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের প্রশ্নে ভীত হয়ে ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার শুরু থেকেই নজর রেখেছিল ধূমকেতুর ওপর। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বরের বারোতম সংখ্যায় সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত হয় নজরুলের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’। দীর্ঘ এ কবিতার প্রথম কয়েক চরণ হলো- ‘আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল?/স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।/দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি/ভূভারত আজ কসাইখানা-আসবি কখন সর্বনাশী?/দেবসেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,/রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই এলে কৃপাণ ধরে?’ ব্রিটিশ সরকার এ সংখ্যাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ওই বছরেরই ২৩ নভেম্বর কুমিল্লা থেকে নজরুলকে গ্রেফতার করে পরের দিন কলকাতায় আনা হয়। ২৫ নভেম্বর কোর্টে নেয়া হয়, ২৯ নভেম্বর পড়ে মোকদ্দমার দিন। বিচার চলাকালে নজরুল অনশন করেন, যা রবীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করে এবং তিনি অনশন ভাঙার জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটা তারবার্তা পাঠান, যা পৌঁছে না দিয়ে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সরকারের পুলিশ প্রশাসন ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে ফেরত পাঠায়। বিচারে নজরুলের এক বছরের কারাদণ্ড হয়। এর মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ভারতে তো বটেই, ব্রিটিশ উপনিবেশে প্রথম কোনো কবিকে কবিতা লেখার জন্য কারান্তরীণ হতে হয়। নজরুলের কারান্তরীণের মধ্য দিয়ে ধূমকেতু’র ভাগ্যেও নেমে আসে অমানিশার অন্ধকার। ১৯২৩ সালের মার্চে বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটি। তার আগে প্রকাশিত হয় নজরুল সংখ্যা। যেখানে স্থান পায় কবির রাজবন্দীর জবানবন্দী লেখাটি।
ধূমকেতুর উদ্বোধনী সংখ্যাতেই নজরুল স্পষ্ট করেন তার অভিপ্রায়। তিনি লেখেন : ‘রাজভয়- লোকভয় কোনো ভয়েই আমাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সেই তার ভয় পায়। আমার বিশ্বাস যে নিজেকে চেনে, তার আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না। অতএব যে মিথ্যাকে চেনে সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সেই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজেকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে, সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না; অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না।’ নবজাগরণের আলোয়-জাতীয়তাবাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত না হলে এভাবে বলা যায় না, সম্ভবও না।
১৯৪১ এর ৬ এপ্রিল মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে জীবনের শেষ অভিভাষণে নজরুল বলেন, ‘হিন্দু-মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ। মানুষের জীবনে এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য-ঋণ-অভাব; অন্য দিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তুপের মত জমান হয়ে আছে। এ অসাম্য ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে সংগীতে কর্মজীবনে অভেদ ও সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না। জীবন আমার যত দুঃখময় হোক, আনন্দের গান-বেদনার গান গেয়ে যাব আমি। দিয়ে যাব নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে। সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।’
বাংলাদেশের নবজাগরণে কাজী নজরুল ইসলাম অনিবার্য-অনিঃশেষিত এক নাম। আমরা যদি সত্যসত্যই বাংলাদেশকে রাষ্ট্রকে নির্মাণ করতে চই। বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণের পুণ্য নাম হলো বাংলাদেশের নবজাগরণ। যার আলোয় নির্মিত হতে পারে বাংলাদেশ। কাজী নজরুল ইসলাম তার বাতিঘর বিশেষ।