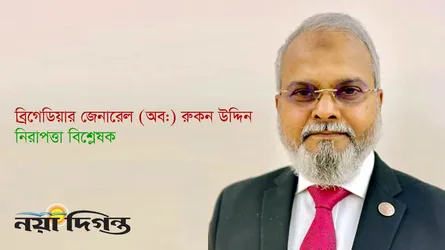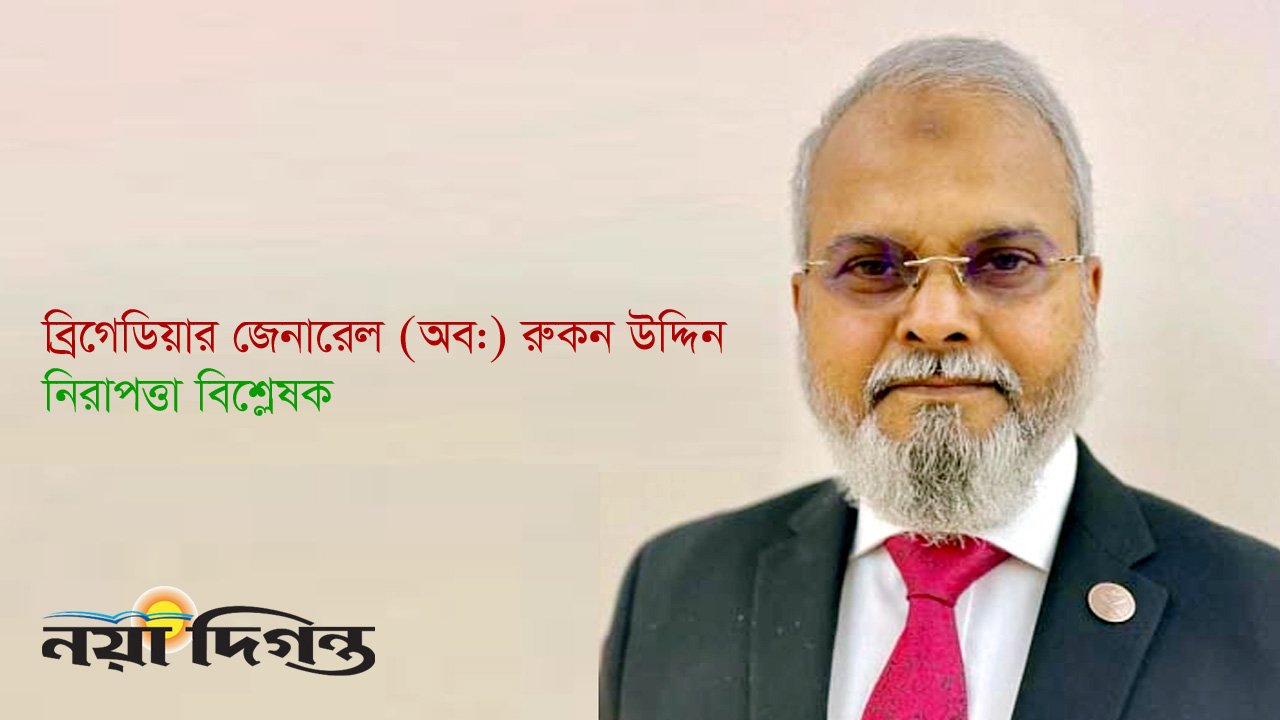বাংলাদেশের গণতন্ত্র শুরু থেকে এক ভয়াবহ বৈপরীত্যের শিকার। দেশের ইতিহাসে কোনো রাজনৈতিক দল কখনো ৪৯ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। তবু, বর্তমান ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট (এফপিটিপি) ব্যবস্থায় সেই দলগুলো দাবি করে, ‘আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত’। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যারা তাদের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে, সেই ৫১ শতাংশ নাগরিকের মতামত কোথায়? তাদের ভোট কি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বহীন?
আজকের বাস্তবতা হলো, ৪০-৪৯ শতাংশ ভোট নিয়ে একটি দল সংসদে গিয়ে সংবিধান পরিবর্তন করে, নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়। এটি কিভাবে যথার্থ গণতন্ত্র হয়; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অস্বীকার করার সাংবিধানিক বৈধতা নয় কি।
এফপিটিপি ব্যবস্থার পরিণতি
১. সংখ্যালঘুর শাসন সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর : বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য হলো, একটি দল যদি ৪০-৪৯ শতাংশ ভোট পায়, তবু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেতে পারে। অর্থাৎ- অর্ধেকের বেশি মানুষ সেই দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলেও এ দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দুর্বলতায় তাদের মতামত সংসদে কোনো গুরুত্ব পায় না। প্রকৃত বাস্তবতায় এটি আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর সংখ্যালঘুর শাসন। জনগণের বড় একটি অংশ নিজেদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য হতে দেখে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হন। এর ফলে রাজনৈতিক বিভাজন গভীর হয়, সামাজিক অসন্তোষ বাড়ে এবং রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা দুর্বল হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের মূলনীতি- ‘সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত জনগণের মতামত’, এখানে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যায়।
২. স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা : এফপিটিপি ব্যবস্থায় একবার সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে দলগুলো কার্যত সীমাহীন ক্ষমতা পেয়ে যায়। ইচ্ছে মতো সংবিধান সংশোধন করে নিজেদের স্বার্থে আইন তৈরি করতে পারে। বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, পুলিশ ও প্রশাসনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয় নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতা নষ্ট হয় এবং সেগুলো জনগণের সেবক না হয়ে শাসক দলের তলপিবাহক হয়ে ওঠে। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দমন, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ এবং নাগরিক স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা স্বাভাবিক চর্চায় পরিণত হয়। এ অবস্থায় গণতন্ত্রের আড়ালে একদলীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩. একদলীয় আধিপত্যের চক্র : বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা গেছে, যে দল একবার ক্ষমতায় আসে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, আমলাতন্ত্র, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত দলীয়করণ হয়ে পড়ে। ফলে একটি অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী একদলীয় আধিপত্যের চক্র তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলোর কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে, নির্বাচনী প্রতিযোগিতা অর্থহীন হয়ে যায়। নতুন রাজনৈতিক বিকল্প উঠে আসতে পারে না। শেষ পর্যন্ত জনগণের সামনে একমাত্র বিকল্প থেকে যায়, একই দল বা জোটকে বারবার ভোট দেয়া, অথবা নির্বাচনের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করা। এটি গণতন্ত্রকে নিস্তেজ করে এবং জনগণকে অনাগ্রহী ও হতাশ করে তোলে।
৪. ভোটের অপচয় : এফপিটিপি ব্যবস্থায় নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীর জন্য দেয়া ভোটের কার্যত কোনো মূল্য নেই। ফলে প্রায় অর্ধেক বা তারও বেশি মানুষের ভোট সরাসরি অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই ‘ভোট অপচয়’ জনগণকে হতাশ করে এবং তারা মনে করেন তাদের ভোট কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়। ফলস্বরূপ, ভোটারদের মধ্যে অনাগ্রহ বাড়ে, অনেকে আর ভোট দিতে যান না। গণতন্ত্র তখন সংখ্যার খেলা হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব অনুপস্থিত। জনগণের আস্থা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে রাজনৈতিক অচলাবস্থার দিকে ধাবিত হয়, যা সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।
কেন প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর)
১. প্রতিটি ভোটের মূল্যায়ন : পিআর ব্যবস্থার মূল শক্তি হলো, কোনো ভোট যেন অপচয় না হয়। এফপিটিপি পদ্ধতিতে একজন প্রার্থী ৪৯ শতাংশ ভোট পেলেও তিনি হেরে গেলে সেই বিপুল ভোট কোনো কাজে আসে না। বিপরীতে, পিআরে প্রতিটি ভোটের একটি ‘মূল্য’ থাকে, কারণ সেই ভোট যোগ হয়ে আসন নির্ধারণ করে। এর ফলে জনগণ মনে করেন, তাদের কণ্ঠস্বর সত্যি সংসদে প্রতিফলিত হচ্ছে। ভোটাররা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা ফিরে পান, অংশগ্রহণ বাড়ে এবং গণতন্ত্র প্রাণবন্ত হয়। এটি রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও হতাশা দূর করার কার্যকর একটি উপায়।
২. একদলীয় স্বৈরতন্ত্রের অবসান : বর্তমান ব্যবস্থায় যে দল ৪০-৪৫ শতাংশ ভোটে জয়ী হয়, সে দল সংসদের প্রায় সব আসন পায়। ফলে সরকারি দল সংবিধান সংশোধন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করে। পিআর চালু হলে কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। বাধ্য হয়ে জোট গঠন করতে হবে, অন্য দলের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং জাতীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে সমঝোতার মাধ্যমে। এতে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা হবে, স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা কমবে, জনগণের সত্যিকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।
৩. অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র : পিআর একটি ইনক্লুসিভ সিস্টেম। এ ব্যবস্থায় শুধু বড় দল নয়, ছোট দল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, নারী ও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের সংসদে প্রবেশের সুযোগ তৈরি হয়। এতে জাতীয় নীতি প্রণয়নে বৈচিত্র্য আসে। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, পেশাজীবী এবং প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে, সেখানে পিআর ব্যবস্থা তাদের কণ্ঠস্বর জাতীয় রাজনীতিতে জায়গা দেয়। এটি গণতন্ত্রকে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়; বরং সবার মতামতের প্রতিফলন করে।
৪. উন্নত বিশ্বের উদাহরণ : আধুনিক বিশ্বের অনেক উন্নত গণতন্ত্র ইতোমধ্যে পিআর বা মিশ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া- এসব দেশে কোনো দল এককভাবে সংসদে প্রাধান্য পায় না। ফলে সেখানে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দেশগুলোতে পিআর ব্যবস্থায় সরকার পরিচালিত হয় সমঝোতা, অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহির ভিত্তিতে। রাজনৈতিক দলগুলোর জনগণের স্বার্থে একে অপরের সাথে কাজ করতে হয়। এর ফলে এ দেশগুলো উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে বিশ্বে উদাহরণ তৈরি করেছে। বাংলাদেশ যদি একই পথে হাঁটে, তবে এখানেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিপক্বতা আসবে।
পিআরের বিরুদ্ধে প্রচলিত যুক্তির জবাব
কোনো দেশে পিআর প্রথম দিনে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হয়নি। রাজনৈতিক সংস্কার ও সময়ের সাথে এটি পরিপক্বতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশও পারবে। তাই ‘পিআর বাংলাদেশে কার্যকর নয়’- এমন কথার কোনো সারবত্তা নেই। এ-ও বলা হচ্ছে- ‘পিআর আনলে অস্থিতিশীলতা হবে’। আসলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয় ক্ষমতার একচ্ছত্র দখলদারিত্ব থেকে। বরং পিআর হলে ক্ষমতা ভাগাভাগি হবে এবং রাজনৈতিক সমঝোতা বাড়বে।
বাংলাদেশের জন্য একটি রূপরেখা
দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু : নিম্নকক্ষে এফপিটিপি বজায় থাকলেও উচ্চকক্ষে পিআর চালু করা যেতে পারে। এতে সংবিধান ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে সবার মতামত প্রতিফলিত হবে।
সংরক্ষিত ও পিআর-ভিত্তিক আসন : যারা সরাসরি নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি, তাদের ভোটও পিআরের মাধ্যমে সংসদে প্রতিনিধিত্ব পাবে।
সংবিধান সংশোধনে উচ্চকক্ষের অনুমোদন বাধ্যতামূলক : কোনো আইন, সংবিধান পরিবর্তন বা সাংবিধানিক নিয়োগ উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়া কার্যকর হবে না।
যদি পিআর চালু না হয়
৪০ শতাংশ মানুষের শাসন শতভাগ জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া চলতে থাকবে। এতে গণতন্ত্র থাকবে মুখোশ, ভেতরে থাকবে একদলীয় স্বৈরতন্ত্র। ফলে রাজনৈতিক মেরুকরণ আরো গভীর হবে। জনগণের আস্থা হারিয়ে নির্বাচনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে। পরিণতিতে অস্থিরতা ও সহিংসতার আশঙ্কা বাড়বে।
উপসংহার : সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে বাংলাদেশ আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বর্তমান ব্যবস্থা ৪০ শতাংশ ভোটকে শতভাগ জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়। এটি গণতন্ত্র নয়; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠকে উপেক্ষা করার বৈধতা।
প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন শুধু একটি নির্বাচনী সংস্কার নয়, এটি গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার পথ।
যদি আমরা সত্যি বিশ্বাস করি, ‘প্রত্যেক মানুষের ভোটের সমান মূল্য রয়েছে’, তা হলে পিআর চালু করার সময় এখনই। নইলে গণতন্ত্র বারবার স্বৈরতন্ত্রের মুখোশে পুনর্জন্ম নিতে থাকবে।
লেখক : নিরাপত্তা বিশ্লেষক