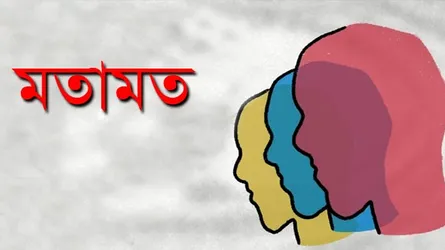আনুপাতিক হার (পিআর) পদ্ধতি এমন একটি নির্বাচনব্যবস্থা যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয়ভাবে তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার অনুযায়ী সংসদীয় আসন পায়। কোনো দল যদি ৩০ শতাংশ ভোট পায়, তবে সে দলটি ৩০ শতাংশ সংসদীয় আসন পাবে। পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো সরাসরি ভোট পদ্ধতি, যেটিকে ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (FPTP) পদ্ধতিও বলা হয়। এই পদ্ধতিতে বিজয়ী একজন ব্যক্তি হয়তো মাত্র ২৫-৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে একটি আসন জিততে পারে; ফলে জনমতের প্রতিফলন তেমন সুনির্দিষ্ট হয় না। পিআর পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো- প্রতিটি ভোটের মূল্য প্রায় সমান রাখা এবং যে দল যত ভোট পেয়েছে সে অনুযায়ী তার সংসদ সদস্য সংখ্যা বরাদ্দ করা।
পিআর পদ্ধতির দু’টি ধরনের মধ্যে, লিস্ট পিআর পদ্ধতিতে প্রতিটি দলের সাথে প্রার্থীদের একটি তালিকা জমা দেয় এবং ভোটাররা দলভিত্তিক ভোট দেয়; নির্বাচিতরা দলের তালিকা অনুসারে নির্বাচিত হন। অপর দিকে একক স্থানান্তরযোগ্য ভোট (এসটিভি) পদ্ধতিতে ভোটাররা তাদের প্রার্থীদের পছন্দের ক্রমে ভোট দেন এবং প্রার্থীরা নির্দিষ্ট কোটার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন; অতিরিক্ত বা কম প্রাপ্ত ভোটগুলো অন্যান্য প্রার্থীর মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ- এই পদ্ধতিতে ভোটাররা একাধিক প্রার্থীকে পছন্দক্রমে ভোট দেন, যা দলীয় গড় অনুযায়ী কাউন্ট করা হয়। বর্তমানে ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকা, এমনকি এশিয়ার দেশসহ মোট শতাধিক দেশে পিআর ব্যবস্থার প্রয়োগ রয়েছে। অনেক গবেষকের মতে, এই মডেল উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার এক অনন্য উদাহরণ (IDEA 2023)।
পিআর পদ্ধতিতে পুরো দেশ অথবা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মোট ভোট গণনা করা হয় এবং মোট ভোট শতাংশ অনুযায়ী আসন বরাদ্দ হয়। তবে অধিকাংশ পিআর ব্যবস্থায় একটি ইলেকট্রোরাল থ্রেশহোল্ড বা ন্যূনতম ভোটের হার নির্ধারিত থাকে। এই থ্রেশহোল্ড পূরণ না করলে কোনো দল সংসদে প্রবেশ করতে পারে না। এর পেছনে উদ্দেশ্য হলো- অতি ক্ষুদ্র দলগুলোর কারণে সংসদ অতিরিক্ত ক্ষতি না হয়। যেমন- জার্মানিতে এই হার ৫ শতাংশ, ইসরাইলে ৩.২৫ শতাংশ, তুরস্কে ৭ শতাংশ, নিউজিল্যান্ডে ৫ শতাংশ বা একটি আসন জয়। এই সীমা পূরণ করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট দল কোনো আসন পায় না, যদিও ভোট পেয়েছে।
পিআর পদ্ধতির নির্বাচনে আলাদাভাবে নিম্নকক্ষ, উচ্চকক্ষ এমনকি একই সাথে উচ্চ ও নিম্ন উভয়কক্ষের নির্বাচন করা সম্ভব। সংসদ যদি এককক্ষ বিশিষ্ট হয়, যেমন- সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডসসহ অনেক দেশে এ ধরনের কাঠামোয় সম্পূর্ণ সংসদ গঠনই পিআরভিত্তিক হয়। এই পদ্ধতিতে নেদারল্যান্ডসে ২০২৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে ১৫টি রাজনৈতিক দল সংসদে প্রবেশ করতে পেরেছে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ যেমন- জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় পিআর পদ্ধতি সাধারণত শুধু নিম্নকক্ষে ব্যবহৃত হয়। যেমন- জার্মানির নির্বাচনে ‘মিক্সড মেম্বার পদ্ধতি’ চালু রয়েছে, যেখানে অর্ধেক আসন সরাসরি ব্যক্তি নির্বাচনের মাধ্যমে এবং বাকি অর্ধেক পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এ ব্যবস্থায় ভোটাররা দু’টি ভোট দেন; একটি প্রার্থীর জন্য (ব্যক্তিগত) এবং অন্যটি দলের জন্য (পিআর)। উচ্চকক্ষ মূলত রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেখানে পিআর ব্যবস্থার কোনো প্রয়োগ নেই। ইতালির পিআর পদ্ধতির নির্বাচনে একই সাথে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের নির্বাচন হয়েছে বা নিয়মিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ভোটাররা পৃথক ব্যালটে দুই কক্ষের জন্য পৃথক ভোট দেন। এতে জনগণের ভোটের আনুপাতিক প্রতিফলন সংসদের উচ্চ ও নিম্ন- উভয় কক্ষে প্রায় সমানভাবে প্রতিফলিত হয়।
অন্য দিকে অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চকক্ষে পিআর বা এসটিভি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, আর নিম্নকক্ষে ব্যবহার হয় Instant Runoff Voting বা এক ধরনের বিকল্প ভোট পদ্ধতি। যদিও উভয় কক্ষের ভোট পদ্ধতি এক নয়, তবুও সেখানে নিয়মিতভাবেই একসাথে দু’টি কক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে ‘double dissolution’ নামে পরিচিত বিশেষ পরিস্থিতিতে দুই কক্ষেই একযোগে নির্বাচন বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। এতে দেখা যায় যে, ভিন্ন পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় একই দিনে দুই কক্ষের নির্বাচন আয়োজন সম্ভব। এ ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতীয় সংসদে নিম্নকক্ষে পূর্ণরূপে আনুপাতিক নির্বাচন হয় এবং উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তবে জাতীয় নির্বাচনের সময় একযোগে এই দুই প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়; যদিও জনগণ সরাসরি কেবল নিম্নকক্ষেই ভোট দেয়। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়ায় Parallel System; এখানে FPTP ও পিআর আলাদাভাবে গণনা হয়, ফলে বড় দলগুলোর আধিপত্য থেকে যায়। হাঙ্গেরি, বলিভিয়াতে Compensatory Mixed পদ্ধতি, যেখানে পিআর ব্যবস্থাটি সরাসরি এফপিটিপির ঘাটতি পূরণ করে।
পিআর পদ্ধতির সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ : প্রথমত, পিআর পদ্ধতির ভোটে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সর্বোচ্চ রক্ষা পায়, কারণ প্রতিটি ভোটই প্রতিনিধিত্বে রূপান্তর হয়। সরাসরি পদ্ধতিতে একটি দল ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬০ শতাংশ আসন পেতে পারে, কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে এমন বিকৃতি নেই। দ্বিতীয়ত, পিআর পদ্ধতিতে নারী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, পিআর ব্যবস্থায় ছোট দলগুলোর টিকে থাকার সুযোগ বাড়ে, রাজনৈতিক মতবৈচিত্র্য ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। ফলে ব্যক্তিগত অথবা দলীয় একনায়কতন্ত্রের ঝুঁকি কমে। চতুর্থত, ভোটারদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আইডিইএর ২০২৩ সালের জরিপ অনুযায়ী, পিআর-ব্যবহৃত দেশগুলোতে গড় ভোটার উপস্থিতি ৭০ শতাংশের বেশি, যেখানে সরাসরি ব্যবস্থায় এটি ৫৮ শতাংশ।
যদিও পিআর পদ্ধতি প্রতিনিধিত্বমূলক ন্যায়বিচার আনতে সক্ষম, তবে এর কিছু অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও রয়েছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো- অতি বেশি দল সংসদে প্রবেশ করায় একটি ক্ষতিকর রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি হয়। এর ফলে সরকার গঠনে দীর্ঘ সময় লাগে, জোট সরকার বেশি দেখা যায়, ফলে জোটে ভাঙন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ও নীতি বাস্তবায়নে দুর্বলতা দেখা দেয়। যেমন- কোনো একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় ইসরাইলে বিগত ছয় বছরে পাঁচটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, লিস্ট পিআর ব্যবস্থায় দলীয় নেতৃত্বই মনোনয়ন দেয়ায় দলীয় কর্তা বা লবিস্টদের প্রতি প্রার্থীদের নির্ভরতা বাড়ে, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। তৃতীয়ত, স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব দুর্বল হয়, কারণ ভোটার সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ভোট না দিয়ে; বরং একটি দল বা তালিকাকে দেয়। দলগুলোর রাজনৈতিক অপরিপক্বতা, সমঝোতার অভাব এবং পিআর ব্যবস্থার জটিলতা কারণে এমনটি হতে পারে।
বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতি নিয়ে বিভ্রান্তি : বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতির নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে বেশ কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। উল্লেখ্যযোগ্য বিভ্রান্তি হলো- প্রথমত, ‘পিআর পদ্ধতিতে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচিত হয় না, তাই এটি অগণতান্ত্রিক।’ বাস্তবতা হলো- পিআর পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ দলভিত্তিক হয়, আর দল অনুযায়ী সংসদে আসন বণ্টন করা হয়। এটি একপ্রকার ‘দলভিত্তিক গণতন্ত্র’ যেখানে জনগণের মোট ভোটের অনুপাতে দলগুলো সংসদে প্রতিনিধিত্ব পায়। এতে একটি মাত্র প্রভাবশালী দলের একচেটিয়া ক্ষমতার সুযোগ কমে যায় এবং ছোট দলগুলোও ভোটের ভিত্তিতে আসন পায়, যা গণতন্ত্রকে আরো অংশগ্রহণমূলক করে তোলে। যেমন- নেদারল্যান্ডস ও ইসরাইলে পুরোপুরি পিআর পদ্ধতি রয়েছে এবং সেখানে সরকারের গঠন সর্বদা বহুদলীয় ও পার্লামেন্টভিত্তিক সিদ্ধান্তে হয়।
দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিতে ‘স্থানীয় এলাকার জন্য কোনো প্রতিনিধি থাকে না, এলাকার সমস্যা কে দেখবে?’ বাস্তবতা হলো- পিআর পদ্ধতিতে যদিও সরাসরি এলাকার জন্য প্রার্থী থাকে না, তবে দলগুলো নিজ নিজ প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়ে থাকে। একই সাথে, অনেক দেশে ‘মিক্সড মেম্বার পদ্ধতি’ চালু আছে, যেখানে কিছু আসনে সরাসরি ভোট হয়, আর বাকিগুলো পিআর পদ্ধতিতে হয়। যেমন- জার্মানি ও নিউজিল্যান্ডে মিশ্র পদ্ধতিতে নির্বাচন হয় যেখানে অর্ধেক আসনে সরাসরি ভোট, বাকি অর্ধেক দলীয় অনুপাতে। এতে স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব ও জাতীয় ভারসাম্য দুটোই বজায় থাকে।
বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকারের ওপরে হস্তক্ষেপ একটি বাস্তবতা। এতে কিছু সুবিধা রয়েছে, যেমন- সংসদ সদস্যরা স্থানীয় প্রকল্পগুলোকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করতে পারেন; অনেক সময় দ্রুত ফান্ড মঞ্জুর, প্রকল্প অনুমোদন কিংবা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত আনতে পারেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য প্রতিবন্ধক। যেমন- সংসদ সংসদের হস্তক্ষেপে নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধি ও প্রশাসনের স্বাধীনতা খর্ব হয়, যা গণতান্ত্রিক বিকাশের অন্তরায়। একজন সংসদ সদস্য ও স্থানীয় চেয়ারম্যান বা মেয়রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে, যা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায়। বিশেষ করে সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ভিন্ন দলের হলে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। অনেক সময় সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক পক্ষপাত তৈরি করে, ফলে প্রকল্প বা সুযোগ বণ্টনে বৈষম্য দেখা দেয়। ফলে জবাবদিহি দুর্বল হয়।
তৃতীয়ত, পিআর পদ্ধতিতে ‘সরকার গঠন দুর্বল হয়, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়।’ বাস্তবতা হলো- এটা আংশিক সত্য হলেও, পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে গঠিত জোট সরকারগুলো সাধারণত অধিকতর আলোচনাভিত্তিক ও প্রতিনিধিত্বশীল হয়। স্বৈরতান্ত্রিক একদলীয় মনোভাব কমে এবং নীতিনির্ধারণে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে (নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক) পিআরভিত্তিক জোট সরকারই যুগের পর যুগ টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।
চতুর্থত, পিআর পদ্ধতি চালু করলে ‘দেশে দলীয় কোন্দল বাড়বে, জঙ্গিবাদ বা বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দেবে।’ বাস্তবতা বরং পিআর পদ্ধতিতে ছোট দলগুলোর বৈধ প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়। এতে দলগুলো রাস্তার রাজনীতি বা সহিংসতার পরিবর্তে সংসদে যুক্তি দিয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে পারে। ফলে রাজনৈতিক শান্তি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ বাড়ে। নেপালে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে পিআর পদ্ধতি চালু করে মাওবাদীদের রাজনৈতিক মূলধারায় আনা হয়েছে।
পঞ্চমত, পিআর পদ্ধতি একটি ‘জটিল পদ্ধতি, সাধারণ মানুষ বুঝবে না।’ বাস্তবতা হলো- এটি একবার প্রয়োগ করলে জনগণ খুব সহজেই বুঝতে পারে। কারণ জনগণ মূলত নিজের মত অনুযায়ী একটি দলকে ভোট দেয়। দল কত শতাংশ ভোট পেল, সেই অনুপাতে আসন পায়, এটি সহজ গণিত। বাংলাদেশে শিক্ষার হার ও ভোটারদের রাজনৈতিক সচেতনতা এখন অনেক বেড়েছে। যেমন- শ্রীলঙ্কাতে ১৯৭৮ সাল থেকেই পিআর পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে এবং সাধারণ মানুষ এতে বেশ অভ্যস্ত।
ষষ্ঠত, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হতে পারে, আনুপাতিক হার পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে পতিত ফ্যাসিস্ট দল তার প্রকৃত জনপ্রিয়তা হারিয়েও ক্ষমতায় ফেরার জন্য ছদ্মভাবে বেশ কিছু ছোট দল বা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করে জোটবদ্ধভাবে অংশ নিতে পারে। এতে তারা সরাসরি নির্বাচনী ক্ষোভ এড়িয়ে নানা নামে, নানা মোড়কে সংসদে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসন পেতে পারে। এই পদ্ধতি যদি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তাহলে এটি ফ্যাসিস্ট সরকারগুলোর জন্য একটি কৌশলগত নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে, বিশেষত যখন তারা সরাসরি নিজেদের ব্যানারে ভোটে জিততে অক্ষম। সুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্র ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে পিআর পদ্ধতি চালুর আগে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন, দলীয় অর্থায়নের স্বচ্ছতা, ছদ্মজোট শনাক্তকরণের ব্যবস্থা এবং প্রকৃত পরিচয় অনুযায়ী দলীয় নিবন্ধন ও মনোনয়ন যাচাই অপরিহার্য। নতুবা এটি জবাবদিহিহীন শাসনের নতুন উপায় হয়ে উঠতে পারে।
মোট কথা, পিআর পদ্ধতির নির্বাচনে কোনো ভোটই ‘নষ্ট ভোট’ হয় না; সবাই কোনো না কোনো প্রতিনিধিত্ব পাবে। একতরফা নির্বাচন কমবে, একক দলীয় এবং একচেটিয়া জয়ের প্রবণতা হ্রাস পাবে, ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ হবে; ফ্যাসিজম কায়েমের সম্ভাবনা কমবে। পাশাপাশি, সংসদ সংসদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ কমবে। সার্বিক বিবেচনায়, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এ ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পরিপক্বতার ওপর। যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুত নয়, তাদের জন্য পিআর হতে পারে দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জের। পক্ষান্তরে যারা সুসংগঠিত ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, তাদের জন্য এটি একটি কার্যকর ও ন্যায্য পদ্ধতি।
বাংলাদেশ যদি পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের দিকে এগোতে চায়, তবে তার আগে প্রয়োজন পর্যাপ্ত রাজনৈতিক সংলাপ, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা এবং ভোটার শিক্ষার বিস্তার। বিশেষ করে, ছদ্মবেশে ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতিনিধি যেন নির্বাচিত না হতে পারে- সে বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে।
লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট
[email protected]