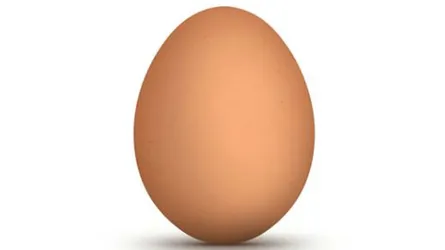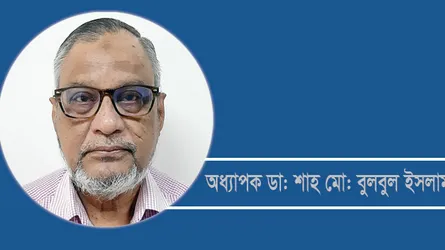মোঃ রাশেদুল হাসান আমিন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে সাথে নিয়ে গাজার জন্য তার ২০ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। ট্রাম্প দাবি করেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে যাচ্ছেন। তবে ট্রাম্পের এ পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনিদের কোনো ভূমিকা নেই। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করা হয়েছে, হামাসকে নিরস্ত্র করে গাজা থেকে বের করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর পশ্চিমতীর-কে ইরাইলের সাথে পুরোপুরি যুক্ত করা হবে না, এমন কোনো নিশ্চয়তাও নেই।
বাকি অংশ গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে, যা অনেকটা ইরাক যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠন পরিকল্পনার মতো; তবে এবার তা নিয়ন্ত্রণ করবেন ট্রাম্প ও ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। ফিলিস্তিন ভূখণ্ড নিয়ে ব্রিটিশদের সাথে ফিলিস্তিনিদের সম্পর্ক ইতিহাসের এক জটিল ও বেদনাদায়ক অধ্যায়; যেখানে প্রতিশ্রুতি, দ্বিচারিতা এবং রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্ঘাতে জন্ম নিয়েছে দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কট। এই বিশ্বাসঘাতকতার শিকড় রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ও পরবর্তী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে।
হুসেইন-ম্যাকমাহন চিঠিপত্র : স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৫-১৬ সালে ব্রিটিশ সরকার আরবদের সাথে একটি গোপন চিঠিপত্র বিনিময় করে, যা ‘হুসেইন-ম্যাকমাহন করেসপন্ডেন্স’ নামে পরিচিত। এতে ব্রিটিশরা প্রতিশ্রুতি দেয়, যদি আরবরা অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে- তবে যুদ্ধ শেষে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেন সহায়তা করবে। এই প্রতিশ্রুতি ফিলিস্তিনসহ বৃহত্তর লেভান্ট অঞ্চলের (বর্তমানে ইসরাইল, জর্দান, লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং দক্ষিণ তুরস্কের অংশ) জন্য প্রযোজ্য ছিল। আরবরা এই প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করে অটোম্যানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ নেয়। কিন্তু ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন।
বালফোর ঘোষণা : ইহুদি আবাসনের প্রতিশ্রুতি
১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব আর্থার বালফোর একটি চিঠিতে ঘোষণা দেন যে ব্রিটেন ‘ফিলিস্তিনে ইহুদি জনগণের জন্য একটি জাতীয় আবাসন প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করে।’ এই ঘোষণাটি ছিল সম্পূর্ণভাবে হুসেইন-ম্যাকমাহনের প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী। ফিলিস্তিনের আরব জনগোষ্ঠী, যারা স্বাধীনতার আশায় ব্রিটিশদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ করে দেখতে পেল যে তাদের ভূমিতে একটি ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা চলছে।
সাইক্স-পিকো চুক্তি : গোপন ভাগাভাগি
এরও আগে, ১৯১৬ সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি হয়- ‘সাইক্স-পিকো অ্যাগ্রিমেন্ট’- যার মাধ্যমে তারা অটোমান সাম্রাজ্যের আরব ভূখণ্ড নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার পরিকল্পনা করে। এই চুক্তিতে ফিলিস্তিনকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, যা আরবদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেয়।
এই তিনটি ঘটনা- হুসেইন-ম্যাকমাহন চিঠিপত্র, বালফোর ঘোষণা এবং সাইক্স-পিকো চুক্তি; একত্রে প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ সরকার আরবদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়ে পরে ভূখণ্ড ভাগাভাগি ও ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়েছে।
ব্রিটিশ ম্যান্ডেট ও শাসনকাল
১৯২০ সালে লিগ অব ন্যাশনস ব্রিটেনকে ‘ম্যান্ডেট ফর প্যালেস্টাইন’ প্রদান করে। এই সময় ব্রিটিশ প্রশাসন ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসনকে উৎসাহ দেয়, যা আরবদের মধ্যে ক্ষোভ ও প্রতিরোধের জন্ম দেয়। ১৯৩৬-৩৯ সালের আরব বিদ্রোহ এবং ১৯৪৪-৪৮ সালের ইহুদি বিদ্রোহ এই দ্ব›েদ্বর চূড়ান্ত রূপ। ব্রিটিশরা একদিকে ইহুদি অভিবাসনকে সহায়তা করেছে, অন্যদিকে আরবদের আন্দোলন দমন করেছে। ফলে ফিলিস্তিনিরা নিজেদের ভূমিতে পরিণত হয় রাজনৈতিকভাবে উপেক্ষিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীতে।
ফিলিস্তিন ভূখণ্ড নিয়ে ব্রিটিশদের বিশ্বাসঘাতকতা ছিল কৌশলগত, পরিকল্পিত এবং দ্বিচারিতায় পূর্ণ। স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা একদিকে আরবদের ব্যবহার করেছে, অন্যদিকে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পথ তৈরি করেছে। এই ইতিহাস শুধু অতীত নয়, আজকের ফিলিস্তিন-ইসরাইল সঙ্কটের ভিত্তি এই বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যেই নিহিত।
১০০ বছর পর এসে সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। আমেরিকার নেতৃত্বে কিছু পশ্চিমা নেতা সলাপরামর্শ করে ঠিক করলেন; যত দিন ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার পরিস্থিতি অনুকূলে না আসছে ততদিন এর শাসনভারের দায়িত্বে থাকবে আন্তর্জাতিক অন্তর্বর্তী প্রশাসন। আর এর নেতৃত্বে থাকবেন ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। তার সাথে পরিচালনা বোর্ডের প্রধান হিসেবে থাকবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখানে গাজাবাসীর চাওয়া-পাওয়া বলতে কিছু থাকতে যে পারে তা বিবেচনায়ই আনা হয়নি।
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকল্প প্রক্রিয়ায় টনি ব্লেয়ারের ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে। বিশেষ করে তার মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ততা এবং ইরাক যুদ্ধের নেতৃত্বে থাকা; এই দুই প্রেক্ষাপটে তাকে অনেকেই ‘যুদ্ধবাজ’ বা ‘নিরাপত্তা-অভিযানপন্থী’ নেতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকা তাই প্রশ্নবিদ্ধ এবং অনেকের চোখে ঔপনিবেশিক ধাঁচের পুনরাবৃত্তি।
মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রক্রিয়ায় টনি ব্লেয়ারের আগমন
২০০৭ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব ছাড়ার পর টনি ব্লেয়ারকে জাতিসঙ্ঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে ‘ছঁধৎঃবঃ ড়হ ঃযব গরফফষব ঊধংঃ’ বা মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রক্রিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তার দায়িত্ব ছিল ফিলিস্তিনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা কাঠামো এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠনের পথ সুগম করা।
তবে বাস্তবে দেখা যায়, ব্লেয়ারের কার্যক্রম ছিল মূলত পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরাপত্তাভিত্তিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক অধিকার, ভূমি পুনরুদ্ধার বা স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের মৌলিক প্রশ্নগুলো প্রায়শই উপেক্ষিত থেকেছে।
ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনায় ব্লেয়ারের পুনরাগমন
সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে গাজা নিয়ে যে ২০-দফা পরিকল্পনা উত্থাপন করা হয়, সেখানে টনি ব্লেয়ারকে ইড়ধৎফ ড়ভ চবধপব-এর সদস্য হিসেবে রাখা হয়। এই বোর্ড গাজা শাসনের জন্য আন্তর্জাতিক তত্ত¡াবধায়ক সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।
এই পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে, হামাসকে বাদ দিয়ে, গাজাকে ‘সন্ত্রাসমুক্ত অঞ্চল’ হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়া হয়। ব্লেয়ারের অংশগ্রহণ আবারো বিতর্কের জন্ম দেয়। অনেকেই বলেন, এটি ‘ঔপনিবেশিক চিন্তা’র আধুনিক রূপ, যেখানে ফিলিস্তিনিদের মতামত ও অধিকারকে পাশ কাটিয়ে বিদেশী নেতৃত্বে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা হচ্ছে।
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকল্প প্রক্রিয়ায় টনি ব্লেয়ারের ভূমিকা শান্তির চেয়ে নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা-অভিযানকেন্দ্রিক ছিল বলেই অনেক বিশ্লেষক মনে করেন। তার অতীত যুদ্ধ-সম্পৃক্ততা, পশ্চিমা নিরাপত্তা কাঠামোর প্রতি আনুগত্য এবং ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক অধিকার উপেক্ষা করার প্রবণতা তাকে ‘যুদ্ধবাজ’ ও ‘ঔপনিবেশিক চিন্তার ধারক’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়া তখনই সফল হবে, যখন তা হবে ফিলিস্তিনিদের নেতৃত্বে, তাদের অধিকার ও আকাক্সক্ষার ভিত্তিতে।
‘শুদ্ধ ঔপনিবেশিক চিন্তা’
জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের ফাঁকে ট্রাম্পের সাথে বৈঠক করা কাতার, তুরস্ক, জর্দান, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও সৌদি আরব একটি বিবৃতি দিয়েছে। সেখানে তারা ট্রাম্পের ‘চেষ্টা’কে স্বাগত জানালেও পরিকল্পনাটি সমর্থন করেনি। দেশগুলো পরিকল্পনার হঠাৎ প্রকাশিত খসড়ায় প্রো-ইসরাইলি পরিবর্তন দেখে হতবাক হয়েছে। তারা যখন ট্রাম্পের সাথে বৈঠক করেছিল, তখন এরকম কিছু তারা ভাবেনি।
‘প্রস্তাবটি মূলত ফিলিস্তিনি প্রতিনিধিত্বকেই শেষ করে দেয়। আরব ও মুসলিম নেতারা, এমনকি যারা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পক্ষে নন, তারাও চান কর্তৃপক্ষ থাকুক, সংস্কার হোক। কিন্তু যেভাবে বিষয়টি সাজানো হয়েছে, এতে পুরো ফিলিস্তিনি প্রতিনিধিত্বই ঝুঁকিতে।’ ‘এটাই নেতানিয়াহুর গত ২০ বছরের স্বপ্ন- একটি সমাধান যেখানে ফিলিস্তিনিদের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকবে না।’
বিচ্ছিন্নতা ও ফাঁদ
সাতজন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করা সাবেক ইসরাইলি কর্মকর্তা শালোম লিপনার একটি মন্তব্য করেছেন, ইসরাইল অনেক কিছু পেলেও ‘বড় ধরনের ফাঁদ’ রয়ে গেছে। পরিকল্পনাটি অনেক বিস্তৃত, কিন্তু বিশদ কম। বাস্তবায়ন খুব কঠিন হবে। তিনি উল্লেখ করেন, ইসরাইল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রমশ একঘরে হয়ে পড়ছে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও রিজার্ভ ডিউটির কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে।
অন্যদিকে, ট্রাম্প পরিকল্পনায় ‘রাষ্ট্র’ শব্দটি ফিরিয়ে এনেছেন বটে, কিন্তু সেটি কেবল একটি বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে- কোনো সীমান্ত বা কাঠামোর স্পষ্টতা ছাড়াই। এটি কেবল নেতানিয়াহুকে দায়মুক্ত রাখার কৌশল। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের পরোয়ানা তার বিরুদ্ধে থাকলেও, এই ধরনের পরিকল্পনা তাকে সময় দিচ্ছে। এভাবে প্রক্রিয়াটি দীর্ঘায়িত করে গাজার ঔপনিবেশায়ন চালানো হবে। গাজার মানুষকে কেবল রাজনৈতিক নাটক দেখানো হচ্ছে।
পরিতাপের বিষয় হলো, ১৯৪৭ সালে জাতিসঙ্ঘের পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনকে দুই ভাগ করে একটি ইহুদি ও একটি আরব (ফিলিস্তিন) রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল। ইহুদি রাষ্ট্রটি বহু আগেই প্রতিষ্ঠা পেলেও ৮০ বছর পরও স্বাধীন ফিলিস্তিন সেখানকার মানুষের স্বপ্নই রয়ে গেছে।