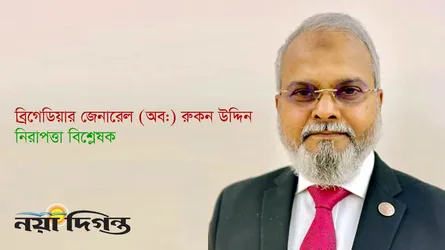দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি আল মাহমুদ লিখেছিলেন- ‘এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময় তার, সামনে নদী পেছনে সমুদ্র তার পিছু হটার নয় আর!’ খুব স্বাভাবিকভাবেই কবির এ পঙ্ক্তির বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে। যখন রাজনীতিবিদরা পরাজিত, সুশীল সমাজ বিতাড়িত এবং সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত তখন কোটা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অবশেষে গোটা জাতির উদ্ধারকারী হিসেবে আবির্ভূত হলো ছাত্রসমাজ। তারা যৌবনকে ধারণ করে। যুদ্ধে যাওয়ার সাহস, সংবেদনশীলতা ও অদম্য প্রেরণা তাদের প্রকৃতি। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার রক্ত লোলুপতার কাছে পরাজিত হয়নি তারা।
১৯৭১ সালে যেমন লাখো প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা, তেমনি আরেক নদী রক্ত পেরিয়ে অর্জিত হলো দ্বিতীয় স্বাধীনতা। প্রতিষ্ঠিত হলো জন-আকাক্সক্ষায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আর এমন এক ব্যক্তি জাতির কর্ণধার হিসেবে আবিভর্ূত হলেন যার রয়েছে জগৎজোড়া খ্যাতি। আকাশছোঁয়া আশায় আশায় এগিয়ে এলো মানুষ। যুবসমাজের সাহস, সাধারণ মানুষের অপার ভালোবাসা ও বিদ্বজনদের বিবেচনায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, সংস্কার ও নির্বাচনের পথে শুভযাত্রা শুরু করে। ‘সামনে নদী পেছনে সমুদ্র তার পিছু হটার নয় আর! তারা পরাজিত করেছে আমলাতান্ত্রিক, বিচারিক ও বাহিনীর ষড়যন্ত্র। নতুন স্বাধীনতার ভ্যানগার্ড হিসেবে এগোচ্ছিল তারা কিন্তু সময় যত যায় ততই পিছু হটার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
একটি বিপ্লব বা অভ্যুত্থান-পরবর্তী দেশ-জাতি-রাষ্ট্রে অস্থিরতা, অরাজকতা ও প্রতিবিপ্লবী ঘটনা অসম্ভব নয়। মানুষ নামের জীবগুলোর অন্তর্নিহিত দোষগুলো সাধারণ মানুষকে যেমন আক্রমণ করে, তেমনি তেজ প্রদীপ্ত বীর তরুণদের আরো আক্রমণ করে। আর সেই চিরায়ত কথাটি তো আছেই- ‘ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে। সার্বিক ক্ষমতা সার্বিকভাবেই মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে।’ পানির গতি যেমন নিচের দিকে, তেমনি ক্ষমতার গতি অর্থবিত্ত ও চিত্তের দিকে। মানুষ হিসেবে আমরা কেউই মানবিক দোষাবলি- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের ঊর্ধ্বে নই। মনীষী প্লেটো তার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ ‘জবঢ়ঁনষরপ’-এ এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে, দেশ শাসনের অধিকার কেবল ‘দার্শনিক রাজাদেরই আছে’। তার আদর্শ রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমধারায় পরিশুদ্ধ হবে দার্শনিক রাজারা। অবশেষে জীবন সায়াহ্নে তিনি অনুভব করেন যেহেতু দার্শনিক রাজারাও মানুষ, তারা মানবিক দোষাবলির ঊর্ধ্বে নয়, তাই ‘খধংি’ বা আইনের শাসনই শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবজ।
মানুষের রাষ্ট্রব্যবস্থা এখন আইনের শাসনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এই তাত্তি¡কতার উল্লেøখ করলাম এই কারণে যে, জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্বে দানকারী যুব তথা ছাত্রসমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ছিল আইনের শাসনে ফিরিয়ে নেয়া। প্রথমত, তারা আইন অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রত্যাবর্তন করবে। দ্বিতীয়ত, তারা একটি সংস্কার কাঠামোর অধীনে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। এটি বলতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করেনি। আর ছাত্রদের নেতৃত্ব ক্ষমতা এবং আন্দোলনের দ্বারা প্রতারিত ও প্রভাবিত হয়েছে। বদনামের যে অংশটুকু বেরিয়েছে আমরা বিশ্বাস করতে চাই, তা সত্য নয়। তাদের দৃশ্যমান দ্বিধা, দ্ব›দ্ব ও বিভাজন প্রত্যাশাকে হতাশায় পরিণত করেছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক দল গঠন প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস তথা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বিব্রত করছে।
অভ্যুত্থান-পরবর্তীকালে যথার্থভাবেই ছাত্ররা নিজেদের দায়িত্বে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছে। পাড়ায় পাড়ায় স্বেচ্ছাসেবক হয়ে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। পরবর্তীকালে তারা যথার্থ নির্দেশনার অভাবে আদর্শিক পদ থেকে অন্য পথে ধাবিত হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে এমন কোনো তৎপরতা এবং কঠিন আইনের শাসন লক্ষ করা যায়নি, যেখানে ছাত্ররা সত্যিকার অভিভাকত্বের দেখা পেয়েছে। ছাত্ররা যখন তাদের সম্মিলিত শক্তির জোরে ‘অটোপাস’ নিয়ে নিলো তখন শিক্ষা উপদেষ্টা শুধু উষ্মা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। এরপর চার ধরনের দুর্বলতা লক্ষ করা গেছে। প্রথমত ছাত্র নেতৃত্ব স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ অথবা অধ্যাপক তাদের হাতে অপমান-অপদস্ত হয়েছে (অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী দোসরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে এমনটি ঘটেছে)। দ্বিতীয়ত, ছাত্রনেতারা কিং মেকার হয়ে দেখা দিলেন। অভিযোগ রয়েছে, কোনো রকম বাছ-বিচার না করে তাদের সুপারিশে প্রতিষ্ঠান প্রধান তথা ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ পেয়েছে। শিক্ষা উপদেষ্টা কোনো সার্চ কমিটি অথবা নীতিমালা অনুসরণের প্রয়োজন অনুভব করেননি। একবার তিনি রাগ করে বলেছিলেন, সবাই ভাইস চ্যান্সেলর হতে চায়। তাদের আইনের শাসনে আনার চেষ্টা করেননি।
অবশেষে বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টা একটি সার্চ কমিটি গঠন করেছেন। ‘খধঃব নবঃঃবৎ ঃযধহ হবাবৎ’। তৃতীয়ত, ছাত্রনেতারা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের শূন্যস্থান পূরণ করেছে। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো যে- এ ক্ষেত্রে ছাত্রনেতাদের চেয়ে ভুক্তভোগীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ফুটপাথের হকার কিংবা দোকানের মালিক তাদের ব্যবসায় নিরাপত্তা চেয়েছে। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ যে নষ্ট কালচারের সৃষ্টি করে গেছে, বাস্তব অর্থেই সেখানে অভ্যুত্থান শক্তি বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। চতুর্থত, দেখা গেল ছাত্ররা গঠনতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে। ঢাকা শহরের দুটো এলাকা এ ব্যাপারে নাম কুড়িয়েছে। পুরান ঢাকার প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন সোহরাওয়ার্দী কলেজ বনাম কবি নজরুল কলেজ পরস্পর আক্রমণ করেছে। শামসুল হক কলেজের মতো ভালো প্রতিষ্ঠান ভাঙচুরের সম্মুখীন হয়েছে। ছাত্রদের আরেকটি মারামারির উজ্জ্বল ক্ষেত্র হচ্ছে নিউমার্কেট এলাকা। সেখানে ঢাকা কলেজ বনাম সিটি কলেজ, সিটি কলেজ বনাম আইডিয়াল কলেজ যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। এসব দেখে মনে হয়েছে, ওই সব প্রতিষ্ঠানের কোনো অধ্যক্ষ বা অভিভাবক নেই। অনেক ক্ষেত্রে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেখানে মন্ত্রকের কোনো ভূমিকা প্রদর্শন করতে পারেনি।
ছাত্র নেতৃত্ব যথার্থ উপদেশনা পরামর্শ ও শাসন পায়নি। তার ফলে তাদের মতো করে আন্দোলন ও সংগ্রামের আয়োজন করেছে। প্রফেসর ইউনূসের এই সরকারটি অন্তর্বর্তীকালীন। আওয়ামী লুণ্ঠনে দেশটি নিঃস্ব। একটি নির্বাচিত সরকার যে দায় দায়িত্ব নিতে পারে তা একটি অস্থায়ী সরকার নিতে পারে না। এই সরকারকে দাবি আদায়ের মোক্ষম কেন্দ্রে পরিণত করেছে সমস্যা জর্জরিত সব পক্ষ। ছাত্ররা একের পর এক আন্দোলন করেছে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বশ্যতা স্বীকার করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতজানু হয়েছে। ঢাকার সাত কলেজের দাবি মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রদের দাবিগুলো ছিল ন্যায়সঙ্গত। তবে সঙ্গত দাবি সমাধানের পরিবর্তে ছাত্রদের অবাস্তব কিছু দাবিও মেনে নিতে হয়েছে। তিতুমীর কলেজের ছাত্রদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। অবশেষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে দাবি মেনে নেয়া হয়েছে। প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে- ছাত্রদের দাবিগুলো উত্থাপনের আগে, সরকার বিব্রত হওয়ার আগে এমন কোনো শিক্ষা নেতৃত্ব কি নেই, যারা ছাত্রদেরকে যথার্থ পথনির্দেশনা দিতে পারে? এবার দেখছি জগন্নাথ কলেজের দেখাদেখি কবি নজরুল কলেজের ছাত্ররাও মিছিল বের করেছে ।
এ তো গেল রাজধানীর অবস্থা। দেশের সব সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অস্থিরতা, অচলাবস্থা ও অরাজকতা চলছে। কোথাও উপাচার্য অপসারণ, কোথাও ছাত্ররাজনীতির দৌরাত্ম্য, কোথাওবা নিজস্ব সমস্যা। এমনকি নাম পরিবর্তনের মতো ঠুনকো বিষয় নিয়ে আন্দোলন চলছে দিনের পর দিন। এই সময়ে অন্তত পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। শিক্ষার এমন সঙ্কটের কারণে শিক্ষা উপদেষ্টাদের দায়ী করছেন শিক্ষক মহল। প্রথম শিক্ষা উপদেষ্টা বয়সের ভারে এতই ন্যুব্জ ছিলেন যে তিনি যথার্থভাবে কাজ করতে পারেননি। মাঝখানে একজন বিজ্ঞ প্রতি-উপদেষ্টাকেও পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। বর্তমান উপদেষ্টা যথার্থভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এমন আশাবাদ অনেকের। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য ১১টি কমিশন গঠন করেছে। অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বিষয়ে কোনো কমিশন গঠন করা হয়নি। এখানে এখনো অনেক অভিজ্ঞ ও সমৃদ্ধ শিক্ষাবিদ রয়েছেন যাদের অভিজ্ঞতা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাজে লাগাতে পারে।
সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশের অনুপস্থিতি রয়েছে। ছাত্ররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখাপড়াবিমুখ। তারা আত্ম প্রতিষ্ঠা ও দল প্রতিষ্ঠায় নিমগ্ন। নাম পরিবর্তন নিয়ে গাজীপুরের ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছেন গত ফেব্রুয়ারি থেকে। এই সামান্য বিষয়টুকু দেখার কর্তৃপক্ষ নেই। নিজস্ব সমস্যা এমনকি ডাইনিংয়ের খাবারের মান ভালো নয় বলে আন্দোলন করছেন ছাত্ররা। পোষ্য কোটা বাতিলসহ রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন হয়েছে। এমন সব লোকদের ভাইস চ্যান্সেলর বানানো হয়েছে যারা ছাত্রদের মিছিলের আগে কোনো কিছু করেন না। আন্দোলন হলেই তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিপুষ্ট করার বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে না। সাত কলেজের আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে তুষ্ট নয় ছাত্র নেতৃত্ব। গত সপ্তাহে আবারো আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন তারা। এ দিকে তিতুমীর কলেজের ছাত্ররা আবারো দাবি জানাচ্ছেন, সাত কলেজ তিতুমীরকে আলাদা করে স্বতন্ত্র কাঠামো গঠনের জন্য। বিভিন্ন দাবিতে বেশ কিছু দিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। এর প্রায়শই তাদের শাটডাউন কর্মসূচির আলোকে সড়ক, মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ করছে। এতে জনমানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। একটা কিছু হলেই বাংলাদেশের মানুষের একটি অযাচিত কালচার হয়ে উঠছে এই সড়ক অবরোধ।
সামগ্রিক বিচারে গোটা শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা চলছে। ছাত্ররা ২০২৪ সালের গণ-আন্দোলনের মুখে সেই যে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেছে, তাদের লেখাপড়ামুখী করার কোনো নীতি ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি সরকার। অপর দিকে ছাত্রনেতাদের অভ্যুত্থানের পর ছাত্রসমাজকে পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। লেখাপড়া এবং সমাজ কল্যাণমুখী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তারা ছাত্রসমাজকে ব্যস্ত রাখতে পারত। সেখানে বড় ধরনের গ্যাপ রয়েছে। কোথাও কোথাও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈরী পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
আবার কোথাও বা শিক্ষকদের ছাত্রদের সাথে আন্দোলনে সক্রিয় দেখা যাচ্ছে। এই দুটোর একটিও সঙ্গত নয়। যে কারণে ছাত্ররা বিপথগামী হয়েছে। তবে এখনো সময় বয়ে যায়নি। বাংলাদেশ জাতির স্বার্থে তাদেরকে বিদ্যায়তনিক জগতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ জন্য সরকার, প্রতিষ্ঠান প্রধান, ছাত্র নেতৃত্ব সবাইকে সমন্বিত করে কার্য ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। শিক্ষাবিদরা মনে করেন, দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাহত করে আন্দোলন যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রয়োজনে ছাত্রদের এসব দাবি-দাওয়া মোকাবেলা করার জন্য ও পরামর্শ দেয়ার জন্য ‘নির্দেশনা সেল’ করা যেতে পারে। সার্বিকভাবে দেশের মানুষ উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা দেখে একেবারেই হতাশ। গ্রামের লোকেরা বলে ‘উল্টো রথে ঘোড়া টানে’। যেখানে ঘোড়া রথ টানবে সেখানে রথই যদি ঘোড়া টানে তাহলে পরে উল্টো যাত্রা হতে বাধ্য। পিতা তার মমত্ব, শুভকামনা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সন্তানকে পরিচালনা করবেন, পরিচর্যা করবেন এটিই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সন্তান যদি তার যৌবনের জোরে পিতাকে বশ্যতা মানাতে চায় তা ভালো ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে না।
লেখক : অধ্যাপক (অব:), সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়