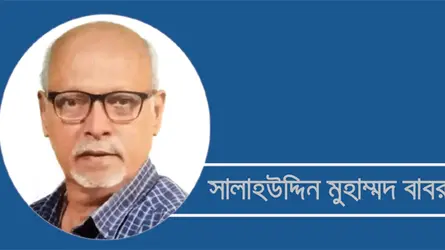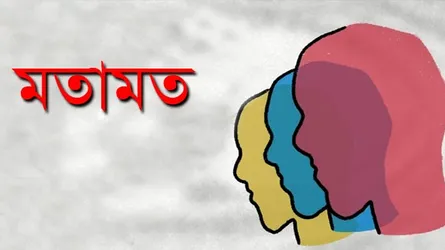ইতিহাসের পাতাজুড়ে ছড়িয়ে আছে রক্ত, আগুন আর ধ্বংসস্তূপের করুণ কাহিনী, যেগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে যুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ঠাণ্ডা যুদ্ধ, আফগানিস্তান-ইরাক সঙ্ঘাত, সিরিয়া সঙ্কট, ইসরাইলের ফিলিস্তিনে হামলা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা সর্বশেষ ইরান-ইসরাইল মুখোমুখি অবস্থানÑ এসব ঘটনাকে অনেকেই কেবল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও কূটনৈতিক ব্যর্থতার ফলাফল হিসেবে দেখেন। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি গভীর ও পুঁজিকেন্দ্রিক। অস্ত্র ব্যবসায়, ধ্বংসস্তূপে নির্মাণ খাতের পুনরুজ্জীবন, দখল করা ভূখণ্ডে প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ, নিরাপত্তা প্রযুক্তির রফতানি, এমনকি শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় দাতা সংস্থাগুলোর বাজেট বৃদ্ধিÑ সব কিছু মিলিয়ে যুদ্ধ এখন একটি সুসংগঠিত অর্থনৈতিক কাঠামো।
জাতিসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, কেবল ২০২৩ সালে বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় ছিল ২.৪ ট্রিলিয়ন ডলার, যা মানব উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা বা স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের তুলনায় বহুগুণ বেশি। যুদ্ধের নামে এই সুপরিকল্পিত ব্যবসায় মানবিক মূল্যবোধ ও আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে, যা শান্তি নয়, অশান্তিকে পুঁজি করে বাঁচে। এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করব কিভাবে যুদ্ধ রাজনৈতিক ছলনার চেয়ে বেশি একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে, কিভাবে রাষ্ট্র, করপোরেট সামরিক শিল্প ও ভূরাজনৈতিক খেলোয়াড়রা এর পেছনে লাভের অঙ্ক কষে এবং কিভাবে সাধারণ মানুষ এই জঘন্য মুনাফার মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে অবিচার, মৃত্যু ও দুর্ভোগের শিকার হয়।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) রাজনীতির সংঘর্ষ হিসেবে দেখলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। এটি ছিল আধুনিক ইতিহাসে প্রথম ‘শিল্পায়িত যুদ্ধ, যেখানে যুদ্ধের ময়দানের বাইরে আরো এক শক্তিশালী অদৃশ্য ফ্রন্ট তৈরি হয়েছিলÑ সেটি হলো যুদ্ধভিত্তিক ব্যবসায় বা এক লাভজনক রণ-শিল্পের সূচনা। এই যুদ্ধের সময় ইউরোপ ও আমেরিকায় অস্ত্র ও গোলাবারুদের চাহিদা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো নিরপেক্ষ দেশগুলো যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে সরাসরি অংশ না নিয়েও বিপুল অস্ত্র, গুলি, গ্যাস মাস্ক, খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসাসামগ্রী সরবরাহ করে মুনাফা অর্জন করে। যুদ্ধকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি বড় উৎস ছিল এই যুদ্ধ-চাহিদা।
রথচাইল্ডদের মতো কিছু ব্যাংকিং পরিবার যুদ্ধরত দেশগুলোর ঋণদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। অস্ত্র কেনা, সেনা মোতায়েন, যুদ্ধপথ নির্মাণ- এসবই ছিল বিপুল বিনিয়োগের ক্ষেত্র। বীমা কোম্পানিগুলোও যুদ্ধে ব্যবহৃত কার্গো এবং সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর বীমা দিয়ে লাভবান হয়। প্রায় এক কোটি মানুষের প্রাণহানি ও কোটি কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুতি এই যুদ্ধে ঘটলেও অস্ত্র কোম্পানি ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো এর পেছনে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং এর আর্থিক সুবিধা, এই বৈপরীত্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ‘লাভজনক শিল্পের’ প্রথম উদাহরণে পরিণত করে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ও ব্যাপক যুদ্ধ হলেও এটি শুধু রক্ত আর ধ্বংসের গল্প নয়- এটি ছিল এক বিরাট অর্থনৈতিক শিল্পও। যুদ্ধের এই নির্মম বাস্তবতা বহু করপোরেশন, ব্যাংক, অস্ত্র প্রস্তুতকারক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য এক লাভজনক ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের আগে থেকেই, সামরিক সরঞ্জাম রফতানির মাধ্যমে লাভবান হচ্ছিল। জেনারেল মোটরস, লকহিড, বোয়িং, ডগলাসসহ অসংখ্য কোম্পানি যুদ্ধবিমান, ট্যাংক, বোমা ও রাডার তৈরি করে বিলিয়ন ডলার আয় করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদিত হয়েছিল।
যুদ্ধ-লাভবানরা যুদ্ধকালীন সময়েই নিজেদের সম্পদ কয়েক গুণ বাড়িয়ে নেয়। আমেরিকান ব্যাংকিং জায়ান্টগুলো সরাসরি অস্ত্র উৎপাদন ও সরকারি ঋণের মাধ্যমে বিপুল মুনাফা করে। নাৎসি জার্মানির ক্ষেত্রেও জায়ান্ট কোম্পানিগুলো সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিল। যুদ্ধ শেষে ইউরোপের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশগুলোর পুনর্গঠনে মার্শাল প্ল্যান (১৯৪৮) নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সহায়তা দেয়, তা এক দিকে মানবিক সাহায্য হলেও অন্য দিকে এটি ছিল মার্কিন শিল্পপতিদের জন্য এক নতুন বাজারের দ্বার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রমাণ করেছে, যুদ্ধ শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই নয়; বরং এটি একটি পরিকল্পিত লাভের ব্যবসায়ও হতে পারে। যেখানে অস্ত্র বিক্রেতা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নির্মাণ কোম্পানি ও প্রযুক্তি শিল্প- সবাই এক অদৃশ্য শিল্পে পরিণত হয়, যাকে বলা যায় ‘মৃত্যুর বিনিময়ে মুনাফা’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকান সামরিক-শিল্প জোট যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি যুদ্ধপীড়িত অঞ্চলগুলোতে নানা দেশের করপোরেট গোষ্ঠী, অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদারি কোম্পানি ও রাজনৈতিক লবিগুলোর জন্য এসব যুদ্ধ পরিণত হয়েছে মুনাফার কারখানায়।
ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫-৭৫) ছিল মার্কিন ইতিহাসে অন্যতম দীর্ঘতম ও ব্যয়বহুল যুদ্ধ। এতে আনুমানিক ৭৩৫ বিলিয়ন ডলার (বর্তমান মূল্যে) খরচ হয়। কিন্তু এই বিপুল ব্যয়ও কিছু করপোরেট গোষ্ঠীর জন্য বিশাল মুনাফার উৎস হয়ে ওঠে। লকহিড, বোয়িং, ডগলাসের মতো অস্ত্র কোম্পানিগুলো এই সময়ে হাজার হাজার যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার ও গোলাবারুদ সরবরাহ করে। সেনা পরিবহন ও খাদ্য সরবরাহের জন্য বেসরকারি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো লাখো কোটি ডলার আয় করে।
আফগানিস্তান যুদ্ধ (২০০১-২১) দুই দশকব্যাপী এই যুদ্ধ ছিল মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের যুদ্ধ, যার মোট ব্যয় ছিল আনুমানিক ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। বেসরকারি সামরিক ঠিকাদারি কোম্পানিগুলো সেনা লজিস্টিকস, ঘাঁটি নির্মাণ, নিরাপত্তা ইত্যাদির নামে শত শত বিলিয়ন ডলারের চুক্তি পায়। লকহিড, বোয়িং, ডগলাসের মতো অস্ত্র নির্মাতারা প্রতিনিয়ত নতুন ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র, রাডার ও সাঁজোয়া যান সরবরাহ করে। মার্কিন কংগ্রেসে লবিস্টদের মাধ্যমে এসব কোম্পানি বাজেট বাড়াতে প্রভাব বিস্তার করে।
ইরাক যুদ্ধ (২০০৩-১১) ইরাক আক্রমণের পর প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে হালিবারটন একটি বহুজাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানি একাই প্রায় ৩৯ বিলিয়ন ডলারর সরকারি চুক্তি পায় তেল অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, বৈদ্যুতিক কেন্দ্র ও স্কুল নির্মাণের দায়িত্ব পায় মার্কিন কোম্পানিগুলো, কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ প্রকল্প ছিল অসমাপ্ত বা দুর্নীতিপূর্ণ। ইরাকের তেল খাতে এক্সোনমবিল, বিপি এবং সেলের মতো বড় কোম্পানিগুলো প্রবেশাধিকার পায়, যা যুদ্ধের অন্যতম পরোক্ষ উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয়। প্রাইভেট মিলিটারি কন্ট্রাক্টরস যেমন- ব্ল্যাকওয়াটার, হাজার হাজার ‘নিরাপত্তাকর্মী’ নিয়োগ করে, যারা অনেক সময় আইনের বাইরে থেকে কার্যক্রম চালায়। লিবিয়ায় ন্যাটো হস্তক্ষেপের (২০১১) মাধ্যমে মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে অপসারণের পর লিবিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, যার সুযোগে পশ্চিমা তেল কোম্পানিগুলো লিবিয়ার তেলক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণে নেয়। সিরিয়া ও ইয়েমেন সঙ্ঘাতে ওই অঞ্চলে প্রক্সিযুদ্ধের মাধ্যমে তেল এবং প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর রাজনীতিকে সামরিক বাণিজ্যের অংশে পরিণত করা হয়েছে।
ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ ২০২২ সালে শুরু হয়ে চলছে। এই যুদ্ধকে ঘিরে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলো বিপুল অস্ত্র রফতানি করেছে ইউক্রেনে। আমেরিকা ইউক্রেনকে ১০৬ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে। ইউক্রেনকে দেয়া মার্কিন সামরিক সহযোগিতার ৭০-৯০ শতাংশ মার্কিন অর্থনীতিতে গেছে, ফলে ৩০-৩৮টি রাজ্যে প্রযুক্তি শিল্পে হাজার হাজার কর্মসংস্থান হয়েছে। ইউরোপীয় জ্বালানি বাজারে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হওয়ার ফলে আমেরিকা এলএনজি রফতানি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। সর্বোপরি ৩০ এপ্রিল ২০২৫ স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী, ইউক্রেনি সম্পদের রাজস্বের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভবিষ্যতে মার্কিন অংশীদারত্বের অধিকার পাচ্ছে।
ইসরাইল-ফিলিস্তিনের ২০২৪-২৫ সালের সরাসরি সংঘর্ষে গাজা উপত্যকার ওপর ইসরাইলের সামরিক অভিযানের সময় ইসরাইলি ড্রোন, ‘আয়রন ডোম’ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং হাইটেক নজরদারি প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এসব প্রযুক্তি বিভিন্ন দেশে রফতানির মাধ্যমে ইসরাইলের প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য ব্যাপক আয়ের পথ খুলে দেয়। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতারসহ উপসাগরীয় দেশগুলো নতুন করে নিরাপত্তা চুক্তি করে এবং মার্কিন ও ইউরোপীয় অস্ত্র ক্রয়ে আগ্রহ দেখায়। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমা অস্ত্র প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়।
মুসলিম বিশ্বের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো গত শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এ ধরনের অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবসার মূল টার্গেটে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের মোট প্রমাণিত তেলের প্রায় ৬০ শতাংশ রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে। মুসলিম দেশ, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ-বিশ্ব অস্ত্র রফতানির ৭০ শতাংশ গ্রাহক হলো মুসলিম দেশ, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর নিজস্ব সামরিক উৎপাদন না থাকায় প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র কিনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও ইসরাইলের সামরিক শিল্পকে টিকিয়ে রাখছে। মুসলিম তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো আজকের বিশ্বের এক চরম যুদ্ধ-নির্ভর বাণিজ্যের শিকার। তেলসম্পদ যেন আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ আর সামরিক হস্তক্ষেপে ধ্বংস হচ্ছে সভ্যতা, অথচ পেছনে রয়েছে অস্ত্র বিক্রেতা দেশের লাভের অঙ্ক।
আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের অন্যতম নিয়ামক হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন- তেল ও হীরা। কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা ও সিয়েরালিওনের মতো দেশে হীরা ও খনিজ সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেই দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ চলেছে, যার পেছনে ছিল বহুজাতিক করপোরেশন ও অস্ত্র সরবরাহকারী দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ। শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যযুদ্ধের বিস্তার যুদ্ধকে আরো ব্যবস্থাপনা-নির্ভর ও মুনাফামুখী করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীনসহ বড় রাষ্ট্রগুলো আধুনিক অস্ত্র, ড্রোন, নজরদারি সিস্টেম রফতানি করে বৈশ্বিক অস্ত্র বাজারে প্রভাব বিস্তার করছে। অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে গবেষণাকারি বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান ঝওচজও-এর তথ্য মতে ২০২৩ সালে, বৈশ্বিক অস্ত্র বাজারের মূল্য ছিল প্রায় ৫৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই ৩৯ শতাংশ অস্ত্র রফতানির অংশীদার। এই অস্ত্রের বেশির ভাগই যাচ্ছে সঙ্ঘাতপীড়িত অঞ্চলগুলোতে, যেগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদের দখল নিয়ে যুদ্ধ চলছে।
জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য- যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র বিক্রেতা। এদের হাতে ‘ভেটো’ ক্ষমতা থাকায় তারা নিজেদের ভূরাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষায় শান্তি প্রচেষ্টাকে প্রায়ই আটকে দেয়। উদাহরণস্বরূপ গাজা, সিরিয়া বা ইউক্রেন সঙ্কটে বহুবার দেখা গেছে, কিভাবে একটি ভেটো বিশ্বজনমত ও মানবিক আবেদনকেও অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ চালু রাখে। এই ভেটো ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা এক দিকে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, অন্য দিকে অস্ত্র বাণিজ্য ও রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখে। বিশ্বে যত সঙ্ঘাত চলমান, তার বেশির ভাগেই এ ভেটোধারী দেশগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ রয়েছে। জাতিসঙ্ঘের কাঠামোগত পক্ষপাত ও ভেটো-নির্ভর রাজনৈতিক কৌশল বিশ্বশান্তিকে জিম্মি করে রাখছে একটি অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী ব্যবসায়িক স্বার্থের কাছে। যদি জাতিসঙ্ঘ সত্যিকারের বিশ্বশান্তির সংরক্ষণকারী হয়ে উঠতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমেই ভেটো ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে- নচেৎ যুদ্ধ চলবে, ব্যবসায় হবে, আর শান্তি থাকবে কেবল কাগজে।
এই ব্যবসার স্বার্থে মানবিক মূল্যবোধ, শান্তির আকাক্সক্ষা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রহেলিকায় পরিণত হচ্ছে। যুদ্ধের মাধ্যমে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক চক্রের ফলে বহু দেশের সাধারণ মানুষ দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়, কিন্তু সেই একই সময় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও করপোরেট জায়ান্টরা বিপুল মুনাফা অর্জন করে। তাই যুদ্ধ যখন ব্যবসায় রূপ নেয়, তখন মানবতা ও ন্যায়বিচার হারিয়ে যায়; যুদ্ধ তখন আর বাস্তব শত্রুতা নয়, এক পণ্য যা প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে সারা বিশ্বে বিক্রি হয়। এই প্রেক্ষাপটে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের অর্থনৈতিক ভিত্তি চ্যালেঞ্জ করা এবং যুদ্ধপণ্যের শিল্প ও ব্যবসায়িক সম্পর্কগুলো খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি। কারণ যত দিন যুদ্ধকে ব্যবসার অংশ হিসেবে দেখা হবে, তত দিন সত্যিকারের স্থায়ী শান্তি অর্জন স্বপ্নই থেকে যাবে।
উপসংহারে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা ক্রমেই স্পষ্ট করে তুলছে যে, যুদ্ধ কেবল রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা ভূখণ্ডগত স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয় নয়- এটি একটি বহুমাত্রিক, গভীর ও সুচিন্তিত ব্যবসায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে সর্বশেষ ইসরাইল-ইরান সংঘর্ষের দিকে তাকালে বোঝা যায়, এসব যুদ্ধে অস্ত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, জ্বালানি ব্যবসায়ী, কূটনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং পুনর্গঠনমুখী বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর বিশাল অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত। শত্রুতা তৈরি এবং তা উসকে দেয়ার কৌশলগুলো প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনোবিজ্ঞানকে টার্গেট করে, যেখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণকে ন্যায়সঙ্গত, অপরিহার্য বা আত্মরক্ষামূলক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর নিজেদের দেশে তেমন কোনো যুদ্ধ নেই; বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা প্যাকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোকে পুঁজি করে প্রক্সিযুদ্ধ করে। এক দিকে তারা অস্ত্র বিক্রি করে, অন্য দিকে তাদের যুদ্ধের খরচগুলো বিবদমান দেশগুলো থেকে বহুগুণে আদায় করে নেয়। এই প্রক্রিয়া এতই জটিল ও শক্তিশালী যে, ভুক্তভোগী দেশগুলোর এককভাবে তেমন কিছু করার নেই, তবে বিষয়গুলো সম্মিলিতভাবে ভাবলে একসময় সমাধান আসতে পারে।
লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট
[email protected]