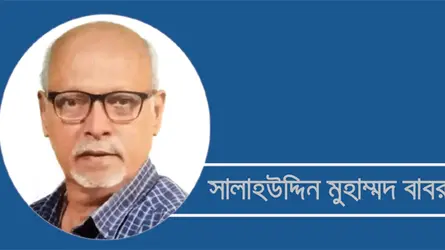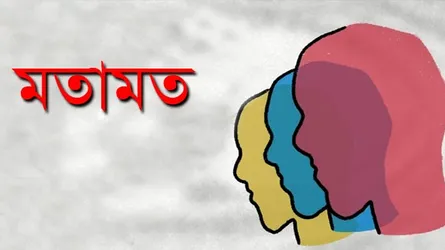ড. মিহির কুমার রায়
২১ নভেম্বর, শুক্রবার। সকালে ভূমিকম্প গোটা দেশকে কম্পিত না করলেও এতে নাড়া খেয়েছেন দেশের প্রতিটি মানুষ। কেননা বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে এত তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয়নি। এত বেশি হতাহত ও ভবন-ফাটলের ঘটনাও ঘটেনি। এর উৎপত্তিস্থল ঢাকার খুব কাছে হওয়ায় বহুতল ভবনে ঘেরা রাজধানীবাসীর ঝুঁকি অনেক বেশি বেড়ে গেছে, এমনটি বলা চলে। তাই ভূমিকম্প তথা দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়টি এখন সব কিছুর আগে আলোচিত হচ্ছে।
মানুষের জীবনে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে কিছু নেই। তাই কয়েক সেকেন্ডের ভূমিকম্প গোটা দেশের মানুষকে মুহূর্তে একটি সুনির্দিষ্ট দুশ্চিন্তার ভেতরে টেনে নিয়ে গেছে। সেটি হলো পরবর্তী ভূমিকম্প কবে হবে, কতটা তীব্র হবে এবং এ থেকে আমরা কিভাবে রক্ষা পেতে পারি।
বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। মার্কিন ভূতাত্তি¡ক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) মাত্রা দেখায় ৫ দশমিক ৫। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদীতে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে এমন ভূমিকম্প হওয়ারই কথা। রিখটার স্কেলে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প হলে বড় আকারের ধ্বংসের আশঙ্কা আছে। যদি ৫ দশমিক ৭ না হয়ে ৭ বা ৮ স্কেল হতো, তাহলে ঢাকা শহর বিপর্যস্ত হতো। শুক্রবারের ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিকে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ বলা হচ্ছে। এ ভূমিকম্প বাংলাদেশের জন্য সজাগ হওয়ার বার্তা।
ভূমিকম্পের প্রভাবে ঢাকার বংশালের কসাইটুলিতে পাঁচতলা একটি ভবনের রেলিং ভেঙে পড়লে তিন পথচারী নিহত হয়েছেন। ভূমিকম্পের সময় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার গোলাকান্দাইল এলাকায় একটি ভবনের দেয়াল ধসে ১০ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহত শিশুর মা এবং প্রতিবেশী আরেক নারী আহত হয়েছেন। যে নরসিংদী জেলায় উৎপত্তি ভূমিকম্পের, সে জেলাতে প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচজন। এর মধ্যে সদর উপজেলার চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলী এলাকায় একতলা ভবনের ছাদ ধসে নিহত হয়েছেন বাবা-ছেলে।
জেলার পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের কাজীরচর গ্রামের নয়াপাড়া এলাকায় ভূমিকম্পের তীব্র ঝাঁকুনির সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এক বৃদ্ধ। একই উপজেলার চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকায় মাটির দেয়াল ধসে আরেক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের আজকিতলা গ্রামে ভূমিকম্পের সময় গাছ থেকে পড়ে গিয়ে নিহত হন এক যুবক।
এ দিকে রাজধানীর গুলশান-বাড্ডা লিংক রোডের একটি ভবন হেলে পড়ে। উত্তর বাড্ডা, খিলগাঁও, ধানমন্ডিসহ বিভিন্ন এলাকায় ভবনে ফাটলের খবর পাওয়া গেছে। মেরুল বাড্ডার বাসিন্দারা ভূমিকম্পের পর সবাই বাসা থেকে বের হয়ে আসেন। তাদের নিজ বাসায় ক্ষতি না হলেও আশপাশের কিছু বাসায় ফাটল দেখা গেছে। অনেকে বাসায় ঢুকতে ভরসা পাচ্ছেন না।
ফায়ার সার্ভিসের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ জানিয়েছে, আরমানিটোলার কসাইটুলিতে একটি বহুতল ভবনের পলেস্তারা ও ইট খসে পড়েছে। খিলগাঁওয়ে নির্মাণাধীন ভবন থেকে ইট পড়ে পাশের ভবনের একজন আহত হয়েছেন। সূত্রাপুর ও কলাবাগানে দু’টি ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে।
কেবল ঢাকা নয়, সারা দেশে বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় ভবনে ফাটল, দেয়াল ধস, ছাদ ধসসহ দেয়াল হেলে পড়ার খবর মিলেছে। ঢাকার বাইরে বিপুল মানুষ আহত হয়েছেন গাজীপুর ও নরসিংদীতে। গাজীপুরে ভূমিকম্পের সময় একটি কারখানা থেকে তাড়াহুড়া করে বের হতে গিয়ে শতাধিক শ্রমিক আহত হন। নরসিংদীতে সরকারি দুই হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন শতাধিক আহত ব্যক্তি। গত শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে ঢাকাসহ সারা দেশে। দেশের বাইরে কলকাতাসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকাতেও তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকা আনন্দবাজার।
বাংলাদেশে বা এ ভূখণ্ডে বড় ভূমিকম্পের ইতিহাসে আছে। ১৭৬২ সালে ঘটেছিল ভয়াবহ ভূমিকম্প, রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৮ দশমিক ৫। এটি ‘গ্রেট আরাকান আর্থকোয়েক’ নামে পরিচিত। এতে চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এরপর ১৮৯৭ সালে আসামে সংঘটিত ভূমিকম্প ছিল ৮ দশমিক ৭ মাত্রার।
বাংলাদেশের আশপাশে ও দেশের ভেতরে ছোট বা মাঝারি আকারের ভূমিকম্প বাড়ছে। আবহাওয়া অধিদফতরের হিসাবে, ২০২৪ সালে দেশে ও আশপাশের এলাকায় ৫৩টি ভূমিকম্প হয়েছে। এভাবে ছোট বা মাঝারি ভূমিকম্পের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াকে বড় ভূমিকম্পের পূর্বলক্ষণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভূমিকম্পের পরম্পরা এবং সাম্প্রতিক বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করে তারা এমন আশঙ্কা করছেন।
বাস্তবে ঢাকার বহুতল ভবন ও সুপার মার্কেটগুলো ভূমিকম্প সহনীয় করে গড়ে তোলা হয়নি। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, সরঞ্জাম ও উদ্ধার যন্ত্রপাতিও প্রায় নেই বললে চলে। এসব বিবেচনায় নিয়ে ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিতে জরুরি ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর জন্য জরুরি উদ্যোগ ও অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান সুনামি বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস দিতে পারলেও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস এখনো অজানা।
ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় একটি সুষ্ঠু ভূতাত্তি¡ক পরিকল্পনা থাকতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি সীমিত রেখে ঝুঁকি কমাতে পারি। বাংলাদেশের ভূত্বক নরম পাললিক শিলা দিয়ে গঠিত। ছোট বা মাঝারি মাত্রার হাই-ফ্রিকোয়েন্সি (দ্রুতলয়) ভূকম্পনে শক্তি দ্রুত দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু উচ্চমাত্রার লো-ফ্রিকোয়েন্সি (ধীরলয়) কম্পনে পাললিক শিলায় ‘কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ারেন্সে’র কারণে শক্তিমাত্রা বাড়তে পারে এবং ধ্বংসাত্মক রূপ নিতে পারে। ভূগর্ভস্থ জলসম্পৃক্ত পাললিক স্তর তরলীকৃত হয়ে স্থাপনা দেবে যাওয়ার ঝুঁকিও তৈরি করে।
একটি বিষয় অদ্ভুত, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে ঢাকার দূরত্ব মাত্র ১০ কিলোমিটার। ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্য অঞ্চল বলতে মূলত ‘রিং অব ফায়ার’ ও ‘আলপাইন-হিমালয়ান’ অঞ্চলকে বোঝায়।
বাংলাদেশ ‘আলপাইন-হিমালয়ান’ অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশের ভূমিকম্প প্রবণতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণায় দু’টি ভূগাঠনিক জোন চিহ্নিত হয়েছে, পূর্বাঞ্চলীয় সাবডাকশন জোন ও উত্তরাঞ্চলীয় ডাউকি ফল্ট জোন। এসব স্থানে অনিবার্যভাবে ভূমিকম্প সংঘটিত হবে। এখন প্রশ্ন- ভূমিকম্পের ঝুঁকি কিভাবে হ্রাস করা যায়?
ঝুঁকি হ্রাসে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি তিন ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে-
১. পূর্বপ্রস্তুতি : জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, নির্মাণস্থান ও নির্মাণকৌশল ঠিক করা, বিধিমালা মানা, ফল্ট-জোন ম্যাপিং করা, বড় স্থাপনায় ঝুঁকিপূর্ণ স্থান পরিত্যাগ করা, ভূতাত্তি¡ক ম্যাপিংয়ের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা।
২. দুর্যোগের সময় : মানুষের জীবন রক্ষায় প্রশিক্ষণ, মহড়া, সচেতনতা কার্যক্রম।
৩. দুর্যোগ-পরবর্তী : উদ্ধার-তৎপরতার পরিকল্পনা, টেকসই গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি-পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা।
দীর্ঘমেয়াদে দ্রুত বর্ধনশীল অপরিকল্পিত নগরায়ণে বিকেন্দ্রীকরণ আনতে হবে। ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলীয় নগরগুলো ভূমিকম্পপ্রবণ হওয়ায় রাজধানীকে ধীরে ধীরে কম ভূমিকম্পপ্রবণ পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরের পরিকল্পনাও প্রয়োজন।
মোট কথা, ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় সুষ্ঠু ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা জরুরি। এখন আমাদের প্রস্তুতি যথেষ্ট নয়। কিছু কাজ হলেও তা অপ্রতুল। বিপদের অভিজ্ঞতা না থাকলে মানুষের বোধোদয় হয় না। কিন্তু প্রশিক্ষণ, প্রচার ও মহড়ার মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো সম্ভব। যে বাড়িওয়ালা পাঁচতলা ভিত্তির ওপর আটতলা ভবন তুলেছেন, তাকে ঝুঁকি বোঝানো জরুরি। এটি ভীতি তৈরি নয়, সচেতনতা তৈরি। এসব কাজ দ্রুত করতে হবে।
লেখক : অর্থনীতির অধ্যাপক ও সাবেক পরিচালক, বার্ড (কুমিল্লা)