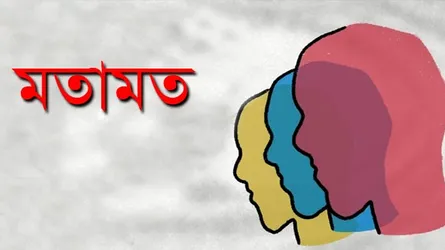প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তির অন্যতম। গ্রামীণ জনপদ থেকে শহর কিংবা রাজধানী পর্যন্ত আর্থসামাজিক অগ্রগতির নেপথ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থের বিশাল অবদান আছে। বর্তমানে প্রায় এক কোটি ১০ লাখ বাংলাদেশী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত, যাদের বড় অংশ অনিয়মিত হলেও দেশে টাকা পাঠান। রেমিট্যান্স প্রবাহের বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৈধ পথে বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০ দশমিক ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চেয়ে ২৬ দশমিক ৮ ভাগ বেশি। হুন্ডি বা অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে পাঠানো অর্থের পরিমাণ ছিল আনুমানিক আরো ৭-৮ বিলিয়ন ডলার। প্রকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৩৫-৪০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হলেও সরকার লাভবান হয় শুধু বৈধ অংশ থেকেই।
রেমিট্যান্স সরাসরি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, মুদ্রার স্থিতিশীলতা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, ভোক্তা ব্যয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশ্বব্যাংকের ২০২৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, রেমিট্যান্স খরচের ৮০ শতাংশই চলে যায় আহরণকারীর পরিবারের খাতে, বাকি ২০ শতাংশ বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ে ব্যবহৃত হয়। এদের পরিবার গড়ে ৩২ শতাংশ বেশি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে এবং ২৫ শতাংশ বেশি শিক্ষায় ব্যয় করে। দেখা যায়, বিদেশে একজন রেমিট্যান্স যোদ্ধা আছে, এমন পরিবারগুলো অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্পসময়ে কৃষিভিত্তিক থেকে ব্যবসাভিত্তিক পরিবারে রূপান্তরিত হয়েছে। ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের গবেষণার তথ্য বলছে, প্রবাসী আয়প্রাপ্ত পরিবারগুলোর মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৭ শতাংশ কম। রেমিট্যান্স খাত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ জনগণের সাথে সম্পর্কিত এবং এ আয় ব্যাপকভাবে বিতরণ হয়। ২০২৪ সালের অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, দারিদ্র্য হ্রাসে রেমিট্যান্স সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, যেখানে রফতানি খাত মূলত নগরভিত্তিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করে।
দেশের রফতানি খাতও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম বড় উৎস। এই খাতেই সরাসরি ৪০ লাখের বেশি মানুষ নিয়োজিত, যাদের ৮০ শতাংশ নারী। বিভিন্ন পণ্য রফতানির মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ৪৯ বিলিয়ন ডলার আয় করে যা পূর্ববর্তী ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে প্রায় ১০ ভাগ বেশি। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের একক আয় মোট রফতানির প্রায় ৮৫ ভাগ। রফতানি আয়ের এই বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে প্রায় পাঁচ হাজার শিল্পপতি, যাদের শীর্ষ ১০০ জন আয় করেন মোট আয়ের প্রায় ৬৫-৭০ ভাগ। এদের অনেকেই একাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের মালিক। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রফতানিকারকদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে শূন্য দশমিক ৩ ভাগ থেকে সর্বোচ্চ ১০ ভাগ পর্যন্ত নগদ সহায়তা দিয়েছে, যা আগে ছিল এক থেকে ২০ ভাগ। এ ছাড়াও রফতানিকারক শিল্পপতিদের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর ছাড়, নগদ প্রণোদনা, ব্যাংক ঋণ ছাড়, কর অবকাশ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বরাদ্দ, এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) থেকে স্বল্পসুদে ডলার ঋণ, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-র মাধ্যমে কূটনৈতিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এসব সহায়তা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আসে, যার সুবিধাভোগী হচ্ছেন বড় শিল্পপতিরা। অথচ অনেক ক্ষেত্রে এসব শিল্পপতি শ্রমিকদের মজুরি দিতে দেরি করেন, এনআইডি হীন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চালান, এমনকি নানা কৌশলে কর ফাঁকি দেন।
এ ছাড়াও রফতানি আয়ের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হলো অর্থপাচার বা আন্ডার ইনভয়েসিং। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এবং গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, আন্ডার-ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ বছরে ৮-৯ বিলিয়ন ডলার হারায়। অর্থাৎ কিছু রফতানিকারক রফতানি পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন করে বিদেশ থেকে কম অর্থ নিয়ে আসে এবং বাকি অর্থ বিদেশেই রেখে দেয়। এই অর্থপাচার দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমিয়ে দেয় এবং বৈধ চ্যানেলে আয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
তুলনামূলকভাবে যদি রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সাথে রফতানি শিল্পপতিদের অবদান বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে, প্রবাসী আয়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব অনেক বিস্তৃত। একজন রেমিট্যান্স যোদ্ধা নিজের আয়ের প্রায় পুরোটা সরাসরি দেশে পাঠান। এতে তৃণমূল পর্যায়ের অর্থনীতিতে তাৎক্ষণিক ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। অন্য দিকে রফতানি আয় মূলত শিল্পপতিদের হাতে কেন্দ্রীভ‚ত থাকে এবং তার বড় অংশ রি-ইনভেস্ট অথবা অফশোর বিনিয়োগে ব্যবহৃত হয়। যদিও এই খাত দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, তবুও এভাবে সামাজিক বৈষম্য ও কেন্দ্রীকরণ বেড়ে যায়। এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয় যে, একজন প্রবাসী শ্রমিক গড়ে মাসে ৪০০-৫০০ ডলার আয় করে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য দেশে পাঠান, যেখানে একজন রফতানিকারক মাসে কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় আয় করেও বড় অংশ বিদেশে রেখে দেন। অথচ রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের জন্য সরকার মাত্র ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখে, আর রফতানিকারকদের জন্য নগদ প্রণোদনা ও বিভিন্ন কর ছাড় মিলিয়ে ব্যয় হয় প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। এই বৈষম্য আর্থিক ন্যায়ের প্রশ্ন তোলে।
প্রবাসী শ্রমিকরা বিদেশে নানা চ্যালেঞ্জ ও সমস্যায় পড়েন, যা তাদের আয় ও জীবনযাত্রায় প্রভাব রাখে। অনেক প্রবাসী কর্মী বাহুল্য ভাড়া বা ভিসা ফি, নিয়োগ এজেন্টদের মাধ্যমে অতিমাত্রায় ফি দিয়ে যান। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট অনুযায়ী, রিক্রুটমেন্ট এজেন্টরা অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ১২০০-৬০০০ ডলার পর্যন্ত ফি নেয়, যা অনেক শ্রমিককে ঋণের জালে আটকে ফেলে। হুন্ডি ব্যবস্থায় জটিলতা কম, এটি দ্রুত এবং গ্রামীণ এলাকায় সহজে পৌঁছায়। ফলে অনেক প্রবাসী শ্রমিক ব্যাংক চ্যানেল এড়িয়ে যায়। এতে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উচ্চ রেমিট্যান্স খরচ ও বিনিময় হার বৈষম্য সৃষ্টি হয়, যেমন ২০২৪ সালে বাংলাদেশী শ্রমিকরা প্রতি ১০০ ডলার রেমিট্যান্সে প্রায় ৯ দশমিক ৪ ডলার হারিয়েছেন (ফি ও বিনিময়ের কারণে), যা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ এবং ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় প্রায় তিনগুণ।
বিদেশে শ্রমিকরা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা তথা দূতাবাসের সহায়তা কমই পান। বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের ৭৯ শতাংশই স্বল্পদক্ষ। মাত্র ১৭ শতাংশ দক্ষ এবং ৫ ভাগেরও কম প্রফেশনাল হিসেবে বিদেশে গিয়েছেন। ফলে তারা কম উপার্জনশীল পেশায় যুক্ত হন। নিয়মিত বেতন না পাওয়া, চাকরি না থাকা, চিকিৎসা না পাওয়া, আবাসন না থাকা, দূতাবাসের অসহযোগিতার মতো সমস্যায় ভোগেন। সরকার এসব সমস্যার যথাযথ সমাধান করলে রেমিট্যান্স প্রবাহ আরো বেড়ে যাবে।
সরকার বায়রা ও বিএমইটির মাধ্যমে নিয়োগ এজেন্টদের নিয়ন্ত্রণ, ফি নির্ধারণ এবং সিন্ডিকেট ভেঙে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এজেন্ট ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দুর্নীতি ও অতিরিক্ত খরচ হ্রাস সম্ভব। দূতাবাস পর্যায়ে কার্যকর ‘হেল্পডেস্ক’, জরুরি হোমলাইন, আইনি ও চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করা দরকার। এ ধরনের উদ্যোগ প্রবাসীদের বিপদে সময়মতো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে প্রবাসীরা দ্রুত, কম খরচে এবং নিরাপদভাবে টাকা ট্রান্সফার করতে পারবে। ইনস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল রেমিট্যান্স অ্যাপ ব্যবহার করলে বৈধ চ্যানেলগুলো জনপ্রিয় হবে এবং হুন্ডির প্রলোভন কমবে।
সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংস্থা ও কর্ম সংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় ৬৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালাচ্ছে, যেখানে ৮৬ হাজার ৪৩৭ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; যদিও এখনো দক্ষতার হার ১৫-২০ ভাগ মাত্র।
প্রবাসী শ্রমিকগণ কেবল অর্থনীতি গঠনেই নয় বরং দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ গণবিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়, যার পেছনে দেশের জনগণের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ করে প্রবাসী শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারা প্রমাণ করেছেন, দেশের সীমান্তের বাইরে থেকেও একজন নাগরিক দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে পারেন। বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী শ্রমিকরা এই বিপ্লবের সময় সরাসরি মাঠে থাকতে না পারলেও অনলাইনে এবং বিপ্লবে অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ করে ফ্যাসিস্ট সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিপ্লবের পক্ষে প্রচারণা, বিদেশী সংবাদমাধ্যমে তথ্য সরবরাহ এবং আন্তর্জাতিক মহলে জনমত গঠনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসীরা বিভিন্ন দেশে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। এই অব্যাহত সমর্থন দেশের আন্দোলনকারীদের মানসিক শক্তি ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে সহায়ক হয়।
বিপ্লবে সফলতার পর অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রবাসীদের আন্তরিক সমর্থনের ফলে আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত, রেমিট্যান্স প্রবাহে রেকর্ড বৃদ্ধি ঘটে। এর প্রধান কারণ ক্যাশ ইনসেন্টিভ ২ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত করা হয় এবং ২০২৫ সালে এ হার অপরিবর্তিত রাখা হয়। হুন্ডির ব্যবহার ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করায় বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে আস্থা অর্জিত হয়। নভেম্বর ২০২৪ থেকে শাহজালাল বিমানবন্দরে প্রবাসী লাউঞ্জ চালু করা হয়, যেখানে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য খাবার, নামাজের ঘর ও শিশু পরিচর্যা সুবিধাসহ আধুনিক পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। প্রবাসী কল্যাণে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়।
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স যোদ্ধা এবং রফতানিকারকরা দেশের প্রবৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে যুগপৎ অবদান রেখে চলেছে। রফতানি খাতের আয় রেমিট্যান্সের চেয়ে দ্বিগুণ হলেও রেমিট্যান্স মানুষের জীবনে সরাসরি অবদান রাখে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টেকসই সমর্থন দেয়। তবে তুলনামূলকভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ প্রধানত মানবিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল ও অস্থির বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, যেখানে রফতানি খাত প্রযুক্তি, দক্ষতা ও নীতিনির্ভর কাঠামোয় ধীরে ধীরে আরো শক্তিশালী ও টেকসই হয়ে উঠছে। অথচ রেমিট্যান্স যোদ্ধারা এখনো বঞ্চনা, দুর্নীতি ও অবহেলার শিকার হচ্ছে।
অর্থনীতির ‘অদৃশ্য হিরো’ রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের নিরাপত্তা, দক্ষতা উন্নয়ন ও মর্যাদা নিশ্চিত করা দরকার। তারা পরিবার, গ্রাম ও ক্ষুদ্র প্রকল্পে মূলধন নিয়ে আসে, আর্থিক স্থিতিশীলতা ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা ধরে রাখে।
লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট