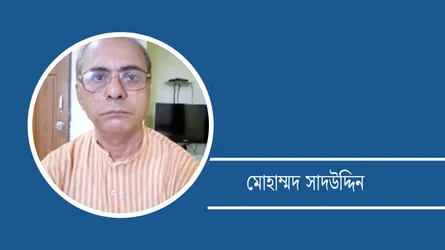১১ মে ২০২৫, অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর একটি সংশোধনী পাস করে, যা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালগুলোকে মানবতাবিরোধী অপরাধ বা অন্যান্য গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধে অভিযুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা দিয়েছে। এটি আইনি নীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নির্দেশ করে। এর আগে ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার অনুরূপ একটি সংশোধনী প্রস্তাব করেছিল, যেখানে তৎকালীন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক একটি খসড়াও প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধবিষয়ক রাষ্ট্রদূত স্টিফেন জে র্যাপের আপত্তিতে পরিকল্পনাটি বাতিল করা হয়; যেখানে তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, এমন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আন্তর্জাতিক আইনি মানকে দুর্বল করতে পারে। কর্তৃত্ববাদী বলে অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ সরকারও যেখানে সংশোধনীটি বাস্তবায়ন করেনি, সেখানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ পদেক্ষেপ গ্রহণ করাকে বিশেষভাবে বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। এ নিবন্ধে সংশোধনীটির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা এবং এটি আইনি পর্যালোচনার মুখোমুখি হলে টিকে থাকতে পারবে কি না, সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
১০ মে ২০২৫, অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল হঠাৎ ঘোষণা দেন, উপদেষ্টা পরিষদ আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন (আইসিটি আইন) সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। ১০ মের আগে এ সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনো প্রকাশ্য বিতর্ক হয়নি। তাহলে অন্তর্বর্তী সরকার কেন এ সংশোধনী নিয়ে এলো?
ছাত্রসমাজ এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্যদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা রাজপথে বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে সংশোধনীটি গৃহীত হয়, যে বিক্ষোভে পরবর্তী সময়ে হেফাজতে ইসলামসহ অন্যান্য প্রভাবশালী ইসলামপন্থী দল যোগদান করে। তাদের প্রধান দাবি ছিল রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা, যে দলটিকে তারা অতীতের বর্বরতা ও দমন-পীড়নের জন্য দায়ী করে। এ প্রতিবাদ দ্রুত গতিশীল হয়ে ওঠে এবং অন্তর্বর্তী সরকারের স্থিতিশীলতায় হুমকি সৃষ্টি হয়। তবে সরকার দেশের অন্যতম বৃহৎ ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধের দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক ছিল। সরাসরি দায়িত্ব নেয়ার পরিবর্তে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে : আইসিটি আইন সংশোধন করে সে দায় বিচার বিভাগের ওপর স্থানান্তরিত করে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা দিয়ে সরকার কার্যত নিজেকে এ সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এবং সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এ পদক্ষেপটি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যতটা না, তার চেয়ে বেশি ছিল ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে নিজেদের টিকিয়ে রাখার একটি রাজনৈতিক কৌশল। মূলত সংশোধনীটি ছিল একটি রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ, নির্বাহী বিভাগের ওপর থেকে দায়িত্ব সরিয়ে বিচার বিভাগের কাঁধে চাপিয়ে একটি জটিল পরিস্থিতি শান্ত করার প্রয়াস।
এ ছাড়াও আইসিটি আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সাধারণত যখন আইনি কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়, তখন সরকার আইনবিশারদ, সাংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতির সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে থাকে। এ ধরনের পরামর্শ প্রস্তাবিত আইনকে আইনগতভাবে সঠিক ও গণতান্ত্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তবে এ ক্ষেত্রে এমন কোনো পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। আইনজীবী, বিচারক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সংশোধনী সম্পর্কে জানানো হয়নি বা তাদের মতামত দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। পুরো প্রক্রিয়ার নীরবতা ইঙ্গিত দেয়, সরকার সম্ভবত সচেতনভাবে উন্মুক্ত বিতর্ক এড়িয়েছে। কারণ তারা জানত যে, আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত্য এ ধরনের একটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে যাবে।
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আইসিটি আইন সংশোধনের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালকে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রদানের এটি প্রথম উদ্যোগ নয়। ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার এ ধরনের একটি সংশোধনী আনার কথা বিবেচনা করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। তবে পদক্ষেপটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকমণ্ডলীর বিশেষত যুদ্ধাপরাধ-বিষয়ক মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিফেন জে র্যাপের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রদূত র্যাপ সংশোধনীটির আইনি ও প্রক্রিয়াগত প্রভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সতর্ক করে উল্লেখ করেন, এটি আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের মানদণ্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সেই সাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যে বিভাজনরেখা ম্লান করে দিতে পারে।
এ ধরনের উদ্বেগ সত্ত্বেও বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সংশোধনীটির বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার সময় র্যাপের পূর্ববর্তী আপত্তিগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে বা তার জবাব দিয়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই; বরং এর মাধ্যমে সরকার ২০১৪ সালের প্রস্তাবিত সংশোধনীর আইনি এবং নৈতিক বিতর্কগুলো পুনরুজ্জীবিত করেছে। এ বাস্তবতা অর্থাৎ পূর্ববর্তী সতর্কতাগুলোর উপেক্ষা, সরকারের অভিপ্রায় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড রক্ষার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।
যদিও অন্তর্বর্তী সরকার গত বছরে সংশোধনী প্রস্তাব প্রবর্তনের মাধ্যমে আইসিটি আইনটিকে আন্তর্জাতিক আইনগত মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, তথাপি ২০২৫ সালের এ সাম্প্রতিক উদ্যোগ সে ধারা থেকে একেবারে ভিন্ন পথে যাত্রা করেছে। বর্তমান সংশোধনী, যা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার অনুমতি দেয়, তা আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন সম্পর্কিত বর্তমান প্রবণতাগুলোর সাথে বিরোধপূর্ণ।
আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো যেমন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ও অন্যান্য আধুনিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল মূলত কোনো ব্যক্তির অপরাধে সমষ্টিগত শাস্তি বা প্রতিষ্ঠানগত নিষেধাজ্ঞা নয়; বরং ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার ওপর গুরুত্ব দেয়। একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করতে একটি বিধান প্রবর্তন করে, সরকার এ প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে, যা প্রক্রিয়াগত ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইনে প্রচলিত ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে প্রণীত ন্যুরেমবার্গ সনদের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক অপরাধে জড়িত সংগঠনগুলোকে অপরাধী ঘোষণা করা যেত। ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল, ৯ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গেস্টাপো এবং এসএসসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে অপরাধী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছিল। যখন কোনো প্রতিষ্ঠানকে অপরাধী ঘোষণা করা হতো, তখন চার্টারের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ সে ধরনের প্রতিষ্ঠানে সদস্যপদ থাকার জন্য শুধু ব্যক্তিদের বিচার করার অনুমতি ছিল।
তবে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের পর আইনি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ১৯৪৯ সালে আমেরিকান জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ল-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক কুইন্সি রাইট ন্যুরেমবার্গ কাঠামোর দিকটির সমালোচনা করেন। তিনি আন্তর্জাতিক আইনের তৎকালীন অবস্থাকে ‘আদিম আইনি ব্যবস্থা’ বলে অভিহিত করেন, কারণ সেটি ‘সম্পর্কের ভিত্তিতে দোষারোপ’ অর্থাৎ ব্যক্তির নিজের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে কেবল অপরাধী ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের কারণে দোষী সাব্যস্ত করার ধারণা সমর্থন করত।
প্রফেসর রাইট ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করলেও, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ ‘সম্পর্কের ভিত্তিতে দোষারোপ’ নীতির ওপর নির্ভরতা থেকে সরে এসেছে। তিনি এ পরিবর্তনকে একটি পরিপক্ব ও ন্যায়ভিত্তিক আইনি ব্যবস্থার দিকে উত্তরণের অপরিহার্য ধাপ হিসেবে দেখেছেন যেখানে ব্যক্তির নিজস্ব কর্মকাণ্ড ও অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে দায়বদ্ধতা নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ ‘ব্যক্তিগত অপরাধ দায়বদ্ধতা’র নীতি প্রতিষ্ঠা পায়। ফলে ১৯৪৯ সালে আইনবিশারদরা সংগঠনকে অপরাধী ঘোষণা করা এবং শুধু সদস্যপদের ভিত্তিতে কাউকে শাস্তি দেয়ার ধারণাকে অপরিণত বা কর্তৃত্ববাদী আইনি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করেন।
আধুনিক আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন এখন সংগঠনকে অপরাধী ঘোষণা করার ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি), সাবেক যুগোস্লাভিয়ার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটিওয়াই), রুয়ান্ডার জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (আইসিটিআর), সিয়েরা লিওনের বিশেষ আদালত (এসসিএসএল) এবং কম্বোডিয়ার আদালতের ব্যতিক্রমী চেম্বার (ইসিসিসি) এসব ট্রাইব্যুনালের আইনি কাঠামোতে বিবর্তনের প্রতিফলন। এই ট্রাইব্যুনালগুলো শুধু ব্যক্তিকে বিচারের আওতায় আনার ক্ষমতা রাখে, কোনো রাজনৈতিক দল, সামরিক ইউনিট, কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নয়। এদের বিধিগুলো ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার নীতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত।
তাহলে সম্প্রতি বাংলাদেশে আইসিটি আইনে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সংগঠনকে অপরাধী হিসেবে ঘোষণা ও শাস্তি দিতে পারে, তা প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-পদ্ধতির সাথে সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক। আধুনিক কোনো আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের এ ধরনের ক্ষমতা নেই; যার মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠানকে অপরাধী ঘোষণা করতে পারে। বাস্তবে, এ সংশোধনী আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত একটি অপ্রচলিত আইনি দৃষ্টিভঙ্গিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অধ্যাপক কুইন্সি রাইট ১৯৪৯ সালেই উল্লেখ করেছিলেন, সংগঠনকে অপরাধী ঘোষণা করা এবং শুধু সদস্য হওয়ায় ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া ‘প্রাথমিক পর্যায়ের আইনি ব্যবস্থার’ (প্রিমিটিভ লিগ্যাল সিস্টেমস) বৈশিষ্ট্য। এ পরিত্যক্ত দৃষ্টিভঙ্গি পুনরায় আইনে সংযুক্ত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ এমন একটি মডেলের দিকে ঝুঁকছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের আধুনিক মানদণ্ডের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।
নিশ্চয় অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তি উপস্থাপন করবে, আইসিটি আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনী কেবল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে কোনো সংগঠন যেমন রাজনৈতিক দলকে অপরাধী ঘোষণা করার ক্ষমতা দিচ্ছে। তারা দাবি করতে পারেন, এটি ন্যুরেমবার্গ সনদে যেমন কোনো সংগঠনকে অপরাধী ঘোষণার পরে শুধু সদস্য হওয়ার ভিত্তিতে ব্যক্তিকেও বিচারের আওতায় আনা হতো, এটি তেমন নয়। ওই যুক্তির ভিত্তিতে সরকার বলতে পারে, এ সংশোধনী ‘সম্পর্কের ভিত্তিতে দোষারোপ’ করে না।
তবে এ যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ। কর্নেল ল স্কুলের ডিন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন বিশ্লেষক অধ্যাপক জেন্স ডেভিড ওহলিন তার গোষ্ঠীগত দায় সম্পর্কিত বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছেন, মানুষ স্বাভাবিকভাবে তাদের নৈতিক মূল্যায়ন সরাসরি গোষ্ঠীটির প্রতি নির্দেশ করে যা কৃতজ্ঞতাও হতে পারে বা বিরাগও হতে পারে। যখন কোনো গোষ্ঠী নৈতিক আচরণ করে, তখন আমরা পুরো গোষ্ঠীর প্রশংসা করি। একইভাবে যখন কোনো গোষ্ঠীকে নিন্দিত বা অপরাধী ঘোষণা করা হয়, তখন সে রায় প্রায়ই সামাজিক ও নৈতিকভাবে গোষ্ঠীর সব সদস্যের ওপর প্রভাব ফেলে, তারা ব্যক্তিগতভাবে অপরাধে জড়িত না থাকলেও। ফলে সংশোধনীটি যদি কোনো নিষিদ্ধ বা অপরাধী ঘোষিত সংগঠনের সাবেক সদস্যদের বিরুদ্ধে সরাসরি আইনি ব্যবস্থা না নেয়, তবু সে সংগঠনকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে এর সাবেক সদস্য ও সমর্থকদের ওপর সামাজিক, নৈতিক ও মর্যাদাগতভাবে গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এভাবে সংশোধনীটি আনুষ্ঠানিক আইনগত শাস্তির মাধ্যমে নয়; বরং সামাজিকভাবে ‘সম্পর্কের ভিত্তিতে দোষারোপ’ নীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে যা আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের এক পরিত্যক্ত ধারণা।
সুতরাং, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) সংশোধন আইন, ২০২৫ যা ট্রাইব্যুনালকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করার কারণে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রদান করে, তা আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলোর থেকে একটি উল্লেখযোগ্য এবং উদ্বেগজনক বিচ্যুতি। সংশোধনীটি ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের পর গঠিত বৈশ্বিক ঐকমত্যকে উপেক্ষা করে যার মূল ধারণা হলো অপরাধের দায় অবশ্যই ব্যক্তিগত হতে হবে এবং সম্পূর্ণ সংগঠনকে অপরাধী ঘোষণা করা আইনি ও নৈতিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। ‘সম্পর্কের ভিত্তিতে দোষারোপ’ নামক বাতিলকৃত মতবাদকে পুনরায় সংযুক্ত করার মাধ্যমে, সংশোধনীটি বাংলাদেশের আইনি কাঠামোকে একটি পুরনো এবং আদিম বিচারব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করছে। এ সংশোধনী আন্তর্জাতিক প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
লেখক : বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এবং হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের নিবন্ধিত কৌঁসুলি