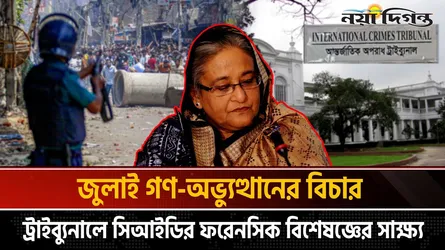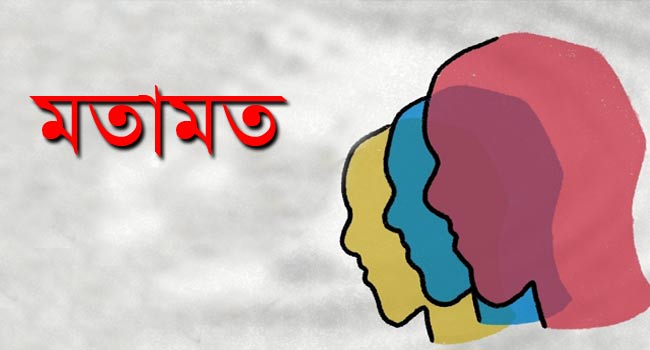সাম্প্রতিককালে মনোবিজ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঢেলে সাজাতে শুরু করেছে। এখন আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি বিচারকমণ্ডলী কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সাথে কিভাবে তারা বাহ্যিক উপাদানগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হন। রাজনৈতিক প্রভাব এবং আর্থিক দুর্নীতি হলো বিচারকের সিদ্ধান্তকে নেতিবাচকভাবে প্রভাব বিস্তারকারী দু’টি প্রধান বাহ্যিক কারণ। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, পরিবেশ, দিনের সময়, এমনকি বিচারকের কাছে সরবরাহ করা মুদ্রিত নথির মানের মতো অন্যান্য কারণও তাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এটি অনাকাক্সিক্ষত। উদীয়মান প্রযুক্তি যেমন চ্যাটজিপিটি ও ডিপসিকের মতো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এ ধরনের প্রবণতা হ্রাসে সহায়ক হতে পারে।
নোবেলজয়ী মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল কাহনেম্যান তার গ্রন্থ থিংকিং ফাস্ট অ্যান্ড স্লোতে ব্যাখ্যা করেছেন, মানব মস্তিষ্ক কিভাবে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কাহনেম্যানের মতে, আমাদের চিন্তা দু’টি ভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করে। প্রথমটি ‘সিস্টেম-১’ নামে পরিচিত, যা আমাদের প্রতিদিনের বেশির ভাগ ভাবনা সুচিন্তিত কোনো প্রচেষ্টা ছাড়া পরিচালনা করার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় এবং সহজভাবে কাজ করে। সিস্টেম-১ যদিও কার্যকর, তথাপি প্রায়ই ভুল করে, কারণ এটি মানসিক শর্টকাট, বদ্ধমূল ধারণা এবং অবচেতন প্রভাবের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল। সিস্টেম-১ বিভিন্ন ধরনের পক্ষপাতের প্রতি সংবেদনশীল। উদাহরণস্বরূপ, ‘প্রাইমিং’ তখন ঘটে, যখন আগের অভিজ্ঞতা নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। অনুরূপভাবে, ‘হ্যালো ইফেক্ট’ আমাদের একটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে সার্বিক মূল্যায়ন করতে প্ররোচিত করে, যেমন কেউ শারীরিকভাবে আকর্ষণীয় হলে ধরে নেয়া হয় যে, সে বুদ্ধিমানও বটে। আরেকটি সাধারণ প্রবণতা হলো ‘অ্যাঙ্করিং’, যেখানে অপ্রাসঙ্গিক তথ্য, যেমন একটি এলোমেলো সংখ্যা বা অবান্তর পরামর্শ, অজান্তে আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। এমনকি আমাদের মেজাজও একটি ভূমিকা পালন করে; যখন আমরা ভালো বোধ করি, তখন সিস্টেম-১ আমাদের সহজে কোনো ধারণা গ্রহণে উৎসাহিত করে, যাকে কাহনেম্যান ‘cognitive ease’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অন্য দিকে, ‘সিস্টেম-২’ সুচিন্তিত, বিশ্লেষণধর্মী এবং যৌক্তিক। এটি তখন কার্যকর হয় যখন আমরা জটিল সমস্যার মুখোমুখি হই অথবা যখন সিস্টেম-১ একটি স্পষ্ট সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়। তবে, সিস্টেম-২-এর জন্য প্রয়োজন হয় মনোযোগ ও মানসিক শক্তি, যার ফলে আমাদের মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবে সিস্টেম-১-এর দ্রুত ও সহজ পথ বেছে নিতে চায়।
কাহনেম্যানের ধারণা অধ্যয়নের আগে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ মূলত সিস্টেম-২-এর একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু কাহনেম্যান বেশ উদ্বেগজনকভাবে দেখিয়েছেন যে, তা নয়। বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মতো এমন ঘটনাবলি ও পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং প্রায়ই হয়ে থাকে, যেগুলোর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। ইসরাইলি বিচারকদের ওপর পরিচালিত এক গবেষণার ফলে দেখা যায়, দুপুরের খাবারের পর তাদের প্যারোল দেয়ার সম্ভাবনা বেশি দৃষ্ট হয়। জার্মানিতে, দোকানে চুরির একটি মামলার রায় ঘোষণার আগে বিচারককে পাশা ছুড়তে বলার একটি ঘটনা বেশ আলোচিত। দেখা গেছে, তাদের সিদ্ধান্ত সেই পাশার ফল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কাহনেম্যান আরো একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে কিছু কাউন্সিলরকে অনুরোধ করা হয়েছিল একটি শিক্ষাবর্ষ শেষে শিক্ষার্থীদের গ্রেডের পূর্বাভাস দিতে।
কাউন্সিলররা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ৪৫ মিনিট করে সাক্ষাৎকার নেন এবং তাদের কাছ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল, বিভিন্ন বুদ্ধমত্তা পরীক্ষার ফল ও ব্যক্তিগত বিবৃতি গ্রহণ করেন। অন্য দিকে, একটি অ্যালগরিদম (অর্থাৎ ধাপে ধাপে নির্দেশনা) কেবল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল এবং একটি মেধা পরীক্ষার ফল ব্যবহার করেছিল। তথাপি এটি ১৪ জন কাউন্সেলরের মধ্যে ১১ জনের চেয়ে সঠিক পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হয়। এ ফল প্যারোল ভঙ্গের পূর্বাভাস এবং পাইলট প্রশিক্ষণে সাফল্যের ক্ষেত্রে পুনরায় মিলিয়ে দেখা হয়েছে এবং একই রকম ফল পাওয়া গেছে।
তাহলে এই ফল আইনপেশা এবং বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর কী প্রভাব ফেলে? কাহনেম্যানের তথ্য ব্যবহার করে কি মামলার ফলের পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব? সাধারণভাবে বলতে গেলে, আদালতের কার্যক্রম মূলত এভাবে চলে : বিচারকরা আইনজীবী বা মামলার পক্ষগুলোর কাছ থেকে কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেন বিষয়টি বিচারিক হস্তক্ষেপের উপযুক্ত কি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা মোটামুটি স্থির থাকে এবং প্রায়ই একই বা একই ধরনের প্রশ্ন বিচারকরা করে থাকেন অর্থাৎ প্রমিত প্রশ্ন। তাই স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব, যা থেকে নির্দিষ্ট উত্তর বা আরো ভালোভাবে বললে, ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ধরনের সরাসরি উত্তর পাওয়া যেতে পারে।
আইনের কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অ্যালগরিদম প্রকৃতপক্ষে বিচারক ও আইনজীবীদের তুলনায় আরো কার্যকর হতে পারে, বিশেষ করে যখন আইনি বিধানাবলি স্পষ্ট এবং সিদ্ধান্ত কেবল একটি সহজ ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ ধরনের উত্তরের ওপর নির্ভর করে। এসব ক্ষেত্রে, অ্যালগরিদম ব্যবহারের মাধ্যমে আইনি সিদ্ধান্তের গতি ও নির্ভুলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, চেকের টাকা অনাদায়ের অপরাধ যা একটি ফৌজদারি অপরাধের বিষয়। এ ধরনের মামলার আইনি নির্দেশনা সুপ্রতিষ্ঠিত, তবু হাজার হাজার মামলা এখনো বিচারিক ও আপিল আদালতে ঝুলে আছে। এর মধ্যে অনেক মামলার ফল মাত্র কয়েকটি সরল প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে সহজে পূর্বাভাস দেয়া যেতে পারে।
প্রমিত বা আদর্শ প্রশ্ন ব্যবহার করে রিট পিটিশনের ‘রক্ষণযোগ্যতা’র পূর্বাভাস দেয়াও সম্ভব হতে পারে। ‘রক্ষণযোগ্যতা’ হলো একটি প্রক্রিয়া, যেখানে আদালত নির্ধারণ করে যে, আবেদনকারী রিট দায়েরের যোগ্য কি না। বিচারকরা অনেক রিট আবেদন প্রাথমিক পর্যায়ে বাতিল করে দেন, কারণ সেগুলো সংবিধান বা বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করে না। তবে সব দুর্বল আবেদন আগে ছেঁটে ফেলা যায় না। কখনো বাতিলযোগ্য আবেদনও পাস হয়ে যায়, বিশেষ করে যদি সেগুলো কোনো প্রবীণ আইনজীবী উপস্থাপন করেন বা অত্যন্ত সুবিন্যস্ত যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। এর ফলে অসঙ্গত ও অন্যায্য পরিণতি ঘটতে পারে, যেখানে আইনগত গুরুত্বের ভিত্তিতে নয়, কেবল উপস্থাপনার ভিন্নতায় একরকম মামলার ভিন্ন রায় হয়।
একটি অ্যালগরিদম একজন মানব বিচারকের মতো আবেগপ্রবণ উপস্থাপনা বা আইনজীবীর খ্যাতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এটি শুধু একটি স্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নমালার ভিত্তিতে কাজ করবে, যেমন আবেদনকারীর অবস্থান আছে কি না, বিকল্প কোনো প্রতিকার আছে কি না, কিংবা কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ এ মামলায় জড়িত কি না এবং প্রাপ্ত উত্তরের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে মামলাটি এগিয়ে নেয়া উচিত কি না। এ প্রক্রিয়া ব্যবহারের ফলে বিচারিক সিদ্ধান্তে বৈষম্য অনেক কমে যাবে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি আরো স্বচ্ছ ও ন্যায্য হয়ে উঠবে।
আদর্শ প্রশ্নের ভিত্তিতে তৈরি অ্যালগরিদম ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে প্রতিবাদ থাকবে। যেমনটি কাহনেম্যান উল্লেখ করেছেন, যখন বিষয় দাঁড়ায় মানুষ বনাম মেশিন, তখন আমাদের সহানুভূতি সবসময় মানুষের পক্ষে থাকে। কার্যকর পরিবর্তন সত্ত্বেও আইনজীবীসমাজ ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তনের বিরোধিতা করে এসেছে। আইনজীবীদের পক্ষ থেকে এ চ্যালেঞ্জ হবে প্রবল, কারণ এটি হবে মূলত তাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা। এ ক্ষেত্রে বিচারকদের দিক থেকেও নিঃসন্দেহে বিরোধিতা আসবে। বিচারকরা যুক্তি উপস্থাপন করবেন, এটি তাদের বিচারিক বিবেচনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে।
বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় অ্যালগরিদম ব্যবহারের একটি বড় সুবিধা হলো এটি বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক পক্ষপাত দূর করতে সহায়ক হতে পারে। মানব বিচারকরা তাদের সর্বোত্তম সদিচ্ছা সত্ত্বেও বাহ্যিক চাপ থেকে পুরোপুরি মুক্ত নন, আর রাজনৈতিক প্রভাব একটি স্থায়ী সমস্যা। সর্বশেষ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে, বিরোধী দল বিএনপির নেতাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মামলাগুলো প্রত্যক্ষ করলে আদালতের মামলাগুলোর পরিচালনা পদ্ধতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
২০০৪ সালে বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, যিনি পরবর্তী সময়ে প্রধান বিচারপতি হন, একটি সুসঙ্গত যুক্তিনির্ভর হাইকোর্টের রায় দেন, যেখানে চলমান ফৌজদারি মামলার বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দায়েরের সুযোগকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তার রায়টি ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী নজিরের ভিত্তিতে দেয়া হয়। দেশবরেণ্য আইনজীবী মাহমুদুল ইসলাম মামলাটি পরিচালনা করেছিলেন; কিন্তু যখন বিএনপি নেতা তারেক রহমান ২০১০ সালে সেই একই রায়ের ভিত্তিতে নিজের বিরুদ্ধে করা ফৌজদারি মামলাগুলো চ্যালেঞ্জ করতে চাইলেন, তখন পরিস্থিতি একেবারে বিপরীত হয়ে যায়। ওই রায়ের লেখক-বিচারক নিজে তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেন, যেন তারেক রহমান সুবিধা না পান।
আওয়ামী লীগ সরকারের সময় রাজনৈতিক পক্ষপাতের আরেকটি স্পষ্ট উদাহরণ হলো, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় আদালতের ভিন্ন ভিন্ন আচরণ। যখন আওয়ামী লীগ নেতা ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর কারাগারে ছিলেন, তখন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তাকে সম্পদের বিবরণ জমা দেয়ার একটি নোটিশ পাঠায়। আপিল বিভাগ সেই নোটিশকে অবৈধ ঘোষণা করেন এই মর্মে যে, কারাগারে থাকা অবস্থায় কেউ সঠিকভাবে জবাব দেয়ার সুযোগ পান না। এ সিদ্ধান্তের ফলে আওয়ামী লীগের আরো কিছু নেতা, যেমন শেখ ফজলুল করিম সেলিম, একই যুক্তির ভিত্তিতে দুদকের তদন্ত থেকে মুক্তি পান। কিন্তু এরপর হঠাৎ করে এ নীতি বদলে যায়। যখন দুদক আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া বন্ধ করে দেয়, তখন আদালত আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। বিএনপি নেতা মওদুদ আহমদ কারাগারে থাকা অবস্থায় একই ধরনের একটি নোটিশ পেলে, আপিল বিভাগ জানান যে, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল এবং কারাগারে থাকলেও দুদক এমন নোটিশ দিতে পারে এবং জবাব চাওয়া বৈধ।
বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেও অনেকে আশঙ্কা করছেন, বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ আচরণ করছে কি না। ২০২৪-এর জুলাই গণহত্যার পর বেশ কয়েকজন পেশাজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। তাদের বেশির ভাগ আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থক। দেখা যাচ্ছে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান অভিযোগ দায়েরে প্রভাব ফেলছে।
সাবেক সরকারের সাথে সম্পর্কিত কাউকে জামিন না দেয়ার বিষয়ে আদালত চাপ অনুভব করে। এমনকি বিচারকরা সচেতনভাবে না হলেও প্রভাবিত হতে পারেন। এটিকে কাহনেম্যান ‘হালো ইফেক্ট’ বলেন, যখন কোনো ব্যক্তির একটি নেতিবাচক দিক, যেমন তার রাজনৈতিক সমর্থন, অন্য ক্ষেত্রে, যেমন সে কোনো অপরাধে দোষী কি না, সেই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্যায্যভাবে প্রভাবিত করে।
মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, বিচারকরা অন্যান্য মানুষের মতো বাহ্যিক প্রভাব ও পক্ষপাত দ্বারা প্রভাবিত হন। এ অসচেতন ও ভুলপ্রবণ চিন্তাধারা যেটিকে ড্যানিয়েল কাহনেম্যান ‘সিস্টেম-১’ নামে বর্ণনা করেছেন। রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর বা উচ্চ-প্রোফাইল মামলায় বিশেষভাবে অন্যায্য ও অসঙ্গত সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আইনি প্রক্রিয়ায় অ্যালগরিদম সংযুক্ত করার মাধ্যমে আমরা এ মানবিক পক্ষপাত কমাতে পারি এবং আরো বস্তুনিষ্ঠ ও সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করতে পারি। তদুপরি এ অ্যালগরিদমগুলো চ্যাটজিপিটি বা ডিপসিকের মতো উন্নত এআই মডেল দ্বারা পরিচালনা করতে পারলে কেবল ন্যায়বিচার ও সামঞ্জস্যের নিশ্চয়তাই নয়; বরং দীর্ঘসূত্রতা ও মামলার জট দূর করে পুরো বিচারব্যবস্থা আরো কার্যকর ও গতিশীল করাও সম্ভব হবে।
লেখক : বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এবং হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের নিবন্ধিত কৌঁসুলি