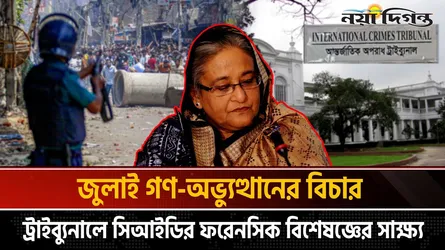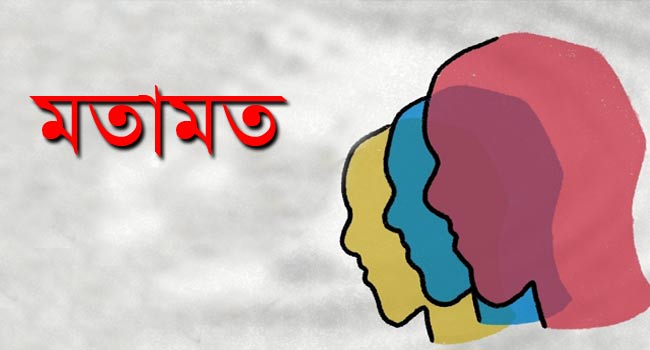’৮০-এর দশকের দিকে আমার নিবাস ছিল শেরেবাংলা নগরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের চত্বরে চিকিৎসকদের আবাসনে। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল ভবনে তখন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, মানসিক রোগ ইনস্টিটিউট এবং সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মেলবন্ধন। বর্ষাকালে আবাসিক ভবন থেকে হাসপাতালে যেতে হতো হাঁটুপানি মাড়িয়ে। অনেক সময় হাসপাতাল ভবনের মেঝেতে বন্যার পানি উঠে যেত। বর্ষার আগমনে বর্ষণমুখর দিনে ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে লোকজন মাছ ধরতে জাল নিয়ে ছুটত মানিক মিয়া এভিনিউতে। মানিক মিয়া এভিনিউ তখন পানিতে থৈ থৈ। হাসপাতালের সামনের মিরপুর সড়ক বর্ষার বন্যার পানির নিচে। সড়কের ওপারে বাবর রোডসহ সব এলাকায় থৈ থৈ পানি। এরই মাঝে কখনো বিকেলে মেঘ ভেঙে সূর্যের আলো দেখা দিলে শিশু হাসপাতালের মাঠ সোনালি রঙের বিচ্ছুরণে হয়ে উঠত বর্ণাঢ্য। সোনা ব্যাঙের মেলা বসত এখানে। হাজার হাজার সোনাব্যাঙ কোথা থেকে হাজির হতো, কে জানে! সাথে ছিল অবিশ্রান্তভাবে গলা ফুলিয়ে ব্যাঙের ডাকের আওয়াজ। এটা এখন কল্পনাতেও মানায় না।
এখন ঢাকায় বৃষ্টির সমাগম নেই। ঢাকার সব আবাসিক এলাকা ইটপাথরের ছোঁয়ায় আকাশচুম্বী ভবনে রূপান্তরিত। আশির দশকে যা ছিল ডুপ্লেক্স বাড়ি এবং সবুজের ক্যানভাসে মোড়া। এখন ঢাকা মহানগরী ছেড়ে সাভার বা মানিকগঞ্জের রাস্তায় অথবা ঢাকা দিনাজপুর হয়ে পঞ্চগড় মহাসড়ক দিয়ে গেলে দেখা যাবে বৃক্ষহীন এক প্রান্তর। একসময়ের জলাধারগুলোর জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন শিল্পকারখানা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা। এলাকার নদীগুলো হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে প্রকৃতি। একসময়ের বহমান নদীগুলো কোথাও ধু-ধু বালুচর অথবা স্থাপনার ভারে হারিয়ে গেছে। ঢাকার পাশের নদীগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় নদীগুলো ভালো নেই। অথচ এই নদীই মানব সভ্যতার প্রাণ।
ক’দিন আগের দুটো সংবাদের কথা উল্লেখ করতেই হয়। কোনো এক স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাদের ছাত্রছাত্রীদের স্টিমারে বুড়িগঙ্গা নদীতে ভ্রমণ করিয়েছেন। উদ্দেশ্য তাদের নদী দেখানো এবং নদীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। নদীমাতৃক দেশে নদী দেখার আয়োজন করতে হয় এ সংবাদে নদীরক্ষা কমিশন বা পরিবেশ অধিদফতরের ঘুম না ভাঙলে জাতির সামনে দুর্দিন ঠেকাবে কে? আরেকটি সংবাদ হলো পরিবেশ উপদেষ্টা আর একজন প্রভাবশালী উপদেষ্টাসহ কক্সবাজারে গিয়েছিলেন বাঁকখালী নদীর দখল এবং দূষণ দেখতে। অবস্থা দেখে তাদের ভিরমি খাবার জোগাড়। প্রশ্ন হচ্ছে, ঘরের পাশে বুড়িগঙ্গা বুড়িয়ে ক্ষীণকায় হয়ে বন্ধের পথে, এটা খেয়াল না করে তারা গেলেন কক্সবাজারে নদী দখল ও দূষণ দেখতে, বলার কিছু নেই। উত্তরবঙ্গের অবস্থা আরো শোচনীয়। উত্তরবঙ্গে নদীর সংখ্যা এমনিতেই হাতেগোনা। কিছু কিছু ছোট শাখা নদী উপনদী শীর্ণ হলেও সারা বছর প্রবহমান ছিল। স্থানীয় লোকজনের গৃহস্থালি এবং কৃষিকাজে এগুলোর পানি ব্যবহৃত হতো। সারা বছর এসব জলাধার থেকে মাছের জোগান হতো। এখন এসব নদী বিরান প্রান্তর, ফসলের ক্ষেত। নদীর বুকে প্রবাহ বন্ধ করে গড়ে উঠেছে ইটভাটা। এগুলো বছরের পর বছর ধরে পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র পেয়েছে-বুক ফুলিয়ে চালিয়েছে তাদের কাজ, এখনো চলছে। এসব ইটভাটার কল্যাণে উজাড় হয়েছে বনভূমি। এগুলো দেখার কেউ নেই। নদী কমিশনের সর্বশেষ তালিকায় এসব নদীর নামও মুছে গেছে।
দু’দিন আগে পরিবেশ উপদেষ্টা উল্লেখ করেছেন, দেশের ৫২ মিলিয়ন মানুষ বন্যার ঝুঁকিতে। অবশ্যই এটা আতঙ্কের বিষয়। বন্যার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে, এটাও তিনি উল্লেখ করেছেন। মার্কিন পরিবেশ অধিদফতরের সাথে বন্যার আগাম সতর্কতার জন্য সমন্বিত কার্যক্রমের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরিবেশের এই ভয়াবহতা প্রতিহত করার জন্য কী কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন তার কোনো পরিকল্পনার কথা তিনি উল্লেখ করেননি। দেশের কৃষিজমির ওপর এবং নদীর প্রবাহ বন্ধ করে গড়ে ওঠা ইটভাটা ও এর বদৌলতে নির্বিচারে গাছ কাটার ব্যাপারে দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম নেই। প্রতিটি মহাসড়ককে কেন্দ্র করে সবুজায়ন প্রকল্প কেন জানি দৃশ্যমান নয়। উন্নয়নপ্রক্রিয়ার নামে শতবর্ষী গাছগুলো নির্বিচারে কাটার অপচেষ্টার ক্ষেত্রে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অথচ পৃথিবীর বহু দেশেই গাছ সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টোটা। নদী দখল, নদীদূষণ, নতুন নতুন ইটভাটা তৈরি, বৃক্ষনিধন দেখে মনে হয়, দেশে পরিবেশ মন্ত্রণালয় বা অধিদফতরের আদৌ অস্তিত্ব আছে কি! নদী দখল, দূষণ অবারিত ইটভাটার অনুমোদন এবং এসব ইটভাটার জ্বালানি হিসেবে নির্বিচারে গাছপালা ব্যবহার দেশের মরুকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।
বৃষ্টির পরিমাণ কমেছে আশঙ্কাজনকভাবে। বেড়েছে তাপমাত্রা। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে দ্রুত। লবণাক্ততা এখন ফরিদপুর ছুঁই ছুঁই করছে। বেড়েছে বজ্রপাত এবং বজ্রপাতে নিহতের সংখ্যা। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। একদিকে বন্যা-জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়ের রক্তচক্ষুু, অন্যদিকে মরুকরণ প্রক্রিয়ার দ্রুতগতি। এর মোকাবেলায় প্রয়োজন পর্যাপ্ত আপৎকালীন ব্যবস্থা। সাথে দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণের কর্মপরিকল্পনা। দেশের বিস্তৃত সড়ক মহাসড়কজুড়ে দ্রুত বনায়ন কর্মসূচি পরিবেশের প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে নিঃসন্দেহে। সড়ক মহাসড়কের পাশে দেশীয় ফলদ এবং বনজ গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে একদিকে যেমন দ্রুত তাপমাত্রা বৃদ্ধি খানিকটা হলেও রোধ করা যাবে। সাথে সাথে হারিয়ে যাওয়া পাখপাখালির ফিরে আসার সম্ভাবনাও তৈরি হবে। দেশীয় ফলদ গাছ একই সাথে খাদ্য সংস্থানের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। এর সাথে বিদ্যমান গাছকাটার ব্যাপারে কঠোর আইনি ব্যবস্থার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যেন কেউ কোনো অবস্থাতেই গাছ কাটতে না পারে। একই সাথে দেশের সব জলাধার উদ্ধার এবং সংস্কার করে মাছ চাষের জন্য ইজারা দেয়া যেতে পারে। রান্নার কাজে কাঠের বা বাঁশের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করা দরকার। শুধু রান্নার কাজেই প্রতি বছর সারা দেশে লাখ লাখ টন লাকড়ির প্রয়োজন হয়। এর প্রায় সবটাই আসে বৃক্ষ নিধনের মাধ্যমে। এর ফলে একদিকে শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন অসুখ যেমন কমবে, তেমনি কার্বন নিঃসরণও কমবে।
স্কুল কলেজে বনায়নপ্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা গেলে তা বনায়নপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে পারে। টেলিভিশনে পরিবেশ, কার্বন নিঃসরণ এবং জনজীবনের ওপর এর প্রভাব বিষয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠানমালা জনস্বার্থে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা এখন সময়ের দাবি। সড়ক থেকে ২০ বছরের বেশি পুরনো গাড়ি জরুরি ভাবে তুলে দেয়া দরকার। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার যে কোনো মূল্যে ঠেকাতে হবে। যান্ত্রিক সভ্যতার জয়যাত্রায় সাধারণ মানুষের জীবন যেন দুঃসহ না হয়ে পড়ে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। এক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং অধিদফতরের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। প্রয়োজন পরিবেশ সুরক্ষা আইনের সংস্কার করে সময়োপযোগী করা। পরিবেশজনিত অভিঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রোডম্যাপ তৈরি জরুরি ভিত্তিতে নেয়া দরকার। সিঙ্গাপুর মডেল এক্ষেত্রে অনুকরণীয় হতে পারে।
লেখক : চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ
[email protected]