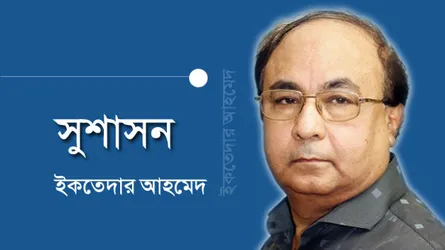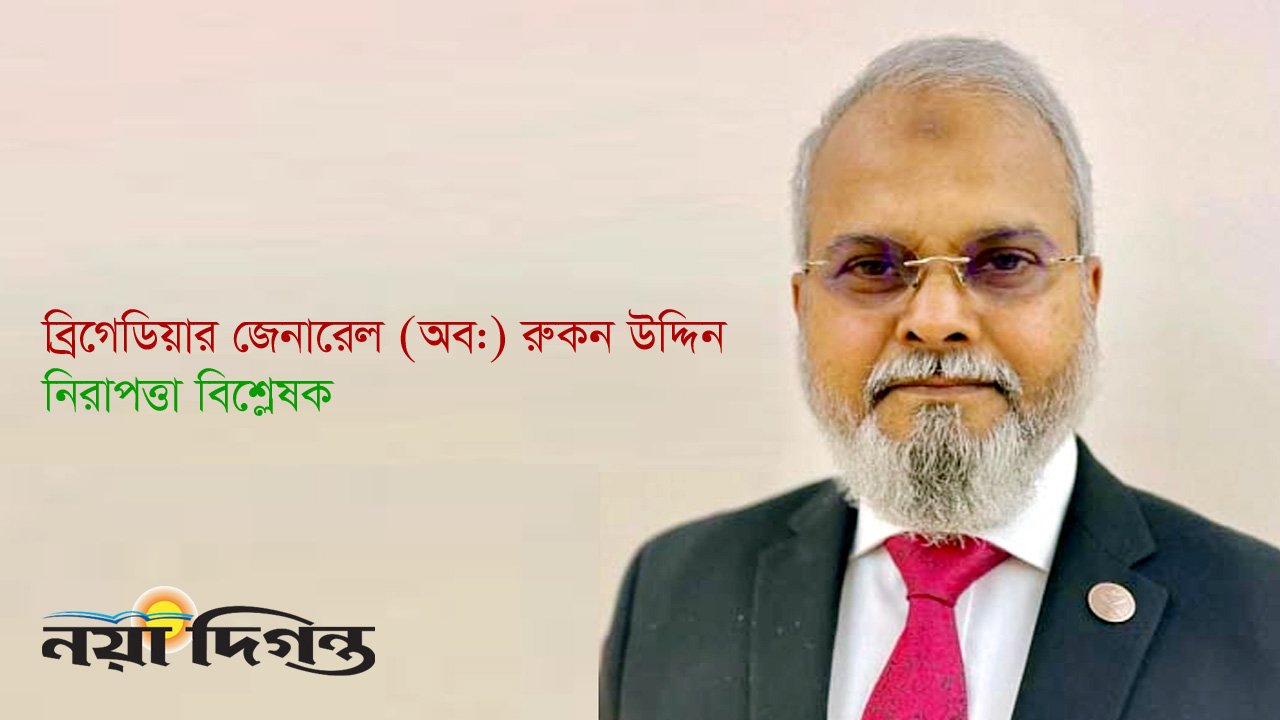সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম (ঈঐঞ) এলাকায় সংঘটিত সহিংসতা ও অস্থিরতার ঘটনাগুলো আকস্মিক বা নিছক স্থানীয় ঘটনা নয়; বরং এগুলো একটি বৃহত্তর ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এটি হলো ঢাকার সরকারগুলোকে চাপে রাখার কৌশল, যাতে প্রয়োজনে তাদের নিজস্ব স্বার্থে বাংলাদেশকে তাঁবে রাখা যায়। ১৯৭১ সালের পর থেকে বিগত ৫৪ বছরে ভারত ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদকে পুষ্ট করেছে এবং পরিকল্পিতভাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। স্বাধীনতার পরপরই পার্বত্য চট্টগ্রাম, যা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও কৌশলগতভাবে ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্তে অবস্থিত, ভারতের বিশেষ আগ্রহের এলাকা হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের নবীন রাষ্ট্রকাঠামো তখনো দুর্বল; এই সুযোগে ভারত বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীকে উসকে দিয়ে বিদ্রোহের বীজ বপন করে। তারা ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরামে শরণার্থীশিবিরের আড়ালে বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসহায়তাও দেয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সহজবোধ্য, বাংলাদেশ যাতে কখনোই ভারতের ইচ্ছার বাইরে স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণ করতে না পারে।
সময়ের পরিক্রমায় ভারত-নির্দেশিত বিভিন্ন বিদ্রোহী সংগঠন গঠিত হয়, যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) সন্তু লারমা নেতৃত্বাধীন অংশ, প্রীতি নেতৃত্বাধীন পিসিজেএসএস (পৃথক গোষ্ঠী), ইউপিডিএফ এবং সাম্প্রতিক কেএনএফ (কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট)। প্রতিটি সংগঠন ভারতের কৌশলগত তত্ত¡াবধানে একই লক্ষ্যে কাজ করেছে এবং করছে; সেটি হলো বাংলাদেশের ভেতরে অস্থিতিশীলতা ধরে রাখা। বাংলাদেশের সরকারকে চাপে রাখাই এর উদ্দেশ্য।
১৯৯৭ সালে নোবেল জয়ের স্বপ্নে শেখ হাসিনা সরকারের স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি (ঈঐঞ চবধপব অপপড়ৎফ) আন্তর্জাতিকভাবে এক ‘ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি’ হিসেবে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল একতরফা, অসম ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী একটি চুক্তি। এতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, যারা বাস্তবে এলাকাটির নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার প্রধান শক্তি, তাদের সম্পূর্ণভাবে প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয়া হয়। পাহাড়ে বসবাসরত বাঙালি অধিবাসীদের মতামতও গুরুত্ব পায়নি। ফলে চুক্তিটি হয়ে দাঁড়ায় একশ্রেণীর উপজাতীয় নেতার তুষ্টি অর্জনের উপকরণ, যা পার্বত্যবাসীর সামগ্রিক স্বার্থ ও নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করে। চুক্তির অন্যতম অংশ ছিল ভূমি কমিশন গঠন, যার মাধ্যমে জমি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করার কথা ছিল। কিন্তু সেই কমিশনে না ছিল সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি, না ছিল বাঙালি অধিবাসীদের কণ্ঠস্বর। ফলাফল, গত দুই দশকে এ কমিশন কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে। আগের সরকারগুলোও এই সমস্যা উপেক্ষা করেছে, যেন এটি কেবল সেনাবাহিনীর দায়িত্ব। অথচ এটি একটি জাতীয় নিরাপত্তা সমস্যা, যার সমাধান হওয়া উচিত ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।
শান্তিচুক্তির পর বিদ্রোহীদের অস্ত্রসমর্পণ কার্যক্রম ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি প্রতীকী নাটক। পিসিজেএসএস সামান্য কিছু পুরনো বা অকার্যকর অস্ত্র জমা দিলেও কার্যকর অস্ত্রভাণ্ডার অক্ষত রাখে। অপর দিকে সেনাবাহিনীর অনেক ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়া হয়, যার ফলে এলাকায় নিরাপত্তার শূন্যতা সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে বিদ্রোহীরা পুনর্গঠিত হয় এবং ইউপিডিএফ ও অন্যান্য গোষ্ঠী আবারো সক্রিয় হয়ে ওঠে। চুক্তির পর তারা ‘রাজনৈতিক দল’-এর ছদ্মবেশে নিজেদের পুনর্গঠন করে এবং একই সাথে চাঁদাবাজি, অবৈধ কর আদায়, অপহরণ ও সন্ত্রাস চালিয়ে যায়। এ দিকে সন্তু লারমা, চাকমা সার্কেলের প্রধান দেবাশীষ রায় এবং অন্যান্য উপজাতীয় নেতা সরকারি সুবিধা ও বিদেশী এনজিওগুলোর সহায়তা ভোগ করলেও, তারা দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এমন সব প্রচারণা চালাচ্ছেন যা পুরোপুরিই নেতিবাচক। তারা সেনাবাহিনী ও বাঙালি অধিবাসীদের ‘দমনকারী শক্তি’ হিসেবে চিত্রিত করেন, অথচ নিজেরাই পাহাড়ি জনগণকে ব্যবহার করছেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে।
সাম্প্রতিক সময়ে ইউপিডিএফ, কেএনএফ ও অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতা আবারো বেড়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, ভারতের মদদেই এই সংগঠনগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে নির্বাচনের আগে দেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে। তাদের কৌশল এখন আরো চাতুর্যপূর্ণ। এখন মহিলাদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে ‘অমানবিক আচরণের’ অভিযোগ আনা যায়। এটি কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়; এটি একটি সুচিন্তিত মনস্তাত্তি¡ক যুদ্ধ। তবুও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনী আইনের সীমারেখার ভেতরে থেকে, দায়িত্বশীলভাবে ও পেশাদারিত্বের সাথে এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখছে। কিন্তু কিছু বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। তারা ‘মানবাধিকার’ ও ‘আদিবাসী অধিকার’-এর নামে এমন এক প্রচারণা চালাচ্ছে, যা ভারতের কৌশলগত স্বার্থের সাথে সরাসরি মিলে যায়। এই বিদেশী অনুদাননির্ভর সংগঠনগুলো এবং কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি তুলছে, বাঙালি অধিবাসীদের উচ্ছেদের পক্ষে আওয়াজ তুলছে, যা ভারতের প্রচারণারই প্রতিফলন। বাস্তবে তারা শান্তি চায় না; তারা চায় পার্বত্য অঞ্চলে একটি ‘নিরাপত্তাহীন অঞ্চল’ তৈরি করতে, যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে এবং ভবিষ্যতে ‘স্বায়ত্তশাসনের’ দাবি তুলতে পারে।
স্পষ্টভাবে বলা দরকার, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তাকাঠামো কোনো দমনমূলক ব্যবস্থা নয়, এটি একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রয়োজন। স্থানীয় নিরাপত্তা কমান্ডাররাই বাস্তব পরিস্থিতি ও হুমকির মাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন; কোথায় নতুন ক্যাম্প স্থাপন হবে বা পুরনো ক্যাম্প বন্ধ করা হবে। এ বিষয়ে বাইরের কোনো চাপ বা রাজনৈতিক নির্দেশনা গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারের উচিত এখনই গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্যক্রম আরো জোরদার করা। বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত সন্দেহজনক এনজিওগুলোর তৎপরতা নজরদারিতে আনা, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ চক্রের অর্থের উৎস খুঁজে বের করা এবং ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমার মতো দুষ্কৃতকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা। পাহাড়ের সাধারণ মানুষের জন্য সেনাবাহিনীর উপস্থিতির অর্থ অবৈধ দমন-পীড়ন নয়; বরং তাদের নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণের বাস্তব গ্যারান্টি। যে এলাকাগুলো প্রায়ই সশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতা, সন্ত্রাসী ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও অনিশ্চয়তার শিকার, সেই পরিবেশে সাধারণ মানুষই প্রথমে ভুক্তভোগী হয়। সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তাবাহিনী থাকলে সীমান্ত থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী, সশস্ত্র তালিকাভুক্ত আইনবহিভর্ূত গোষ্ঠী এবং অপরাধী চক্রগুলোকে দমন করা যায়। ফলে গ্রামের মানুষ নিরাপদে বাজারে যেতে পারে, কৃষিকাজ ও ব্যবসায় নির্বিঘেœ চালাতে পারে এবং শিশু ও নারীরাই নিরাপদে শিক্ষা এবং চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে।
নিরাপত্তাবাহিনী কেবল সশস্ত্র অভিযানই চালায় না, তারা পাহাড়ে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি জরুরিকালে প্রভূত সহায়তা করে : প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে উদ্ধার, রোগবিধ্বস্ত এলাকায় চিকিৎসাশিবির, দূরবর্তী এলাকায় যোগাযোগব্যবস্থা পুনঃস্থাপন ইত্যাদি কাজও করে। নিরাপত্তা কেন্দ্রে সড়ক যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উদ্যোগগুলোর কাজ সুরক্ষিতভাবে এগোতে পারে- কেননা শান্তি না থাকলে কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্পই কার্যকর হবে না। সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রশাসন যখন নিয়মিত পাহারা দেয়, তখন বিনিয়োগকারীরা ও সরকারপ্রণোদিত নানান উন্নয়ন প্রকল্প তৎপর হতে পারে এবং তরুণরা শিক্ষার সুযোগ পেয়ে আত্মচর্চায় এগিয়ে আসতে পারে। অন্য দিকে কিছু বহিরাগত ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, যারা রাজনৈতিক লক্ষ্য বা বিদেশী এজেন্ডা নিয়ে চলেছে, সেনাবাহিনীকে অপমান করে সরকার ও জাতির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালায় তারা চেষ্টা করে সেনা উপস্থিতিকে ‘উৎপীড়ন’ বা ‘অধিকার হরণ’ হিসেবে উপস্থাপন করতে, যাতে পাহাড়ের নির্দোষ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। তবে বাস্তবতা হলো, যে কেউ শান্তি ও উন্নয়ন চায়, তাদের জন্য সশস্ত্রবাহিনীই প্রথম সহায়ক সঙ্গী। সত্যিকারের আদিবাসী কল্যাণ আসে তখনই, যখন কেউ নিরাপদে মাঠে মাটিতে কাজ করতে পারে, তার ফসল বাঁচতে পারে, সন্তান স্কুলে যেতে পারে- এগুলোই জীবনের প্রকৃত নিরাপত্তা।
তাই পাহাড়ি জনসমষ্টিকে মনে রাখতে হবে, নিরাপত্তাবাহিনীর উপস্থিতি তাদের অধিকার ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে। নেতিবাচক প্রচারণার মুখেও প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে নির্বিকারভাবে দায়িত্ব পালন করে। আমাদেরকে বাস্তব অবস্থা মেনে চোখ খোলা রেখে চলতে হবে। নিজেদের অভিজ্ঞতা, গৃহীত সুরক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে; কারণ যারা সেনা প্রত্যাহারের কথা বলে, তাদের উদ্দেশ্য প্রায়ই ভিন্ন। হয় অঞ্চলকে অনিরাপদ করে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে সুযোগ করে দেয়া অথবা ভিন্ন কোনো দূরগামী কূটনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করার সুযোগ যেন কেউ নিতে না পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শুধু একটি ভূগোল নয়; এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের দুর্গ। এই সীমান্ত অরক্ষিত রেখে দেয়া মানে রাষ্ট্রকে বিপদের মুখে ফেলে দেয়া। তাই এটি শুধু সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নয়, এটি জাতীয় ঐক্য টিকে থাকার প্রশ্ন। আমাদের অবশ্যই এই অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব, স্থিতিশীলতা ও জাতীয় ঐক্য রক্ষা করতে হবে, কারণ জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার স্বার্থের উপরে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক বা রাজনৈতিক সুবিধা নয়, দেশ ও তার সীমান্তই সর্বপ্রথম বিবেচ্য।
লেখক : নিরাপত্তা বিশ্লেষক