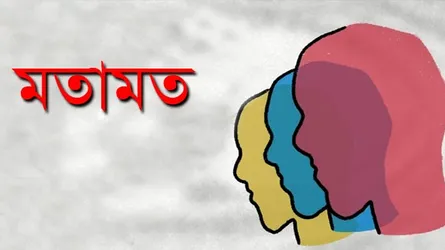মবতন্ত্র আজকাল জ্বলন্ত আলোচ্য বিষয়। শুধু বাংলাদেশে নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ায়। প্রায়ই জনতার হঠাৎ উত্তেজিত রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলার জায়গা দখল করে নিচ্ছে মব বা গোষ্ঠীভিত্তিক শক্তি। তারা এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে, যাতে আইন ও নীতি উপেক্ষিত হচ্ছে। আবেগ ও হিংস্রতা হয়ে উঠছে প্রধান নিয়ামক। এমন ধারা চলতে থাকলে অনেক সময় উত্তেজিত জনতার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা জিম্মি হয়ে পড়ে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে অবশ্য রাষ্ট্র-প্রযোজিত মবের ঘটনা বিস্তর। এর মাত্রা ও গভীরতাও বিপুল। এর শিকার সাধারণত মুসলিম ও দলিত শ্রেণী।
সাধারণত মব ঘটে রাষ্ট্রশক্তির নিষ্ক্রিয়তায় বা দায়শূন্য প্রতিক্রিয়ায়। বাংলাদেশে এমনতরো পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। মবতন্ত্র এখন আলোচিত বিষয়। এ নিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে মনে পড়ল, পুরনো ডায়েরির পাতায় এ বিষয়ে আমার কিছু বিশ্লেষণ রয়েছে। ২০০৩ সালের ডায়েরির পৃষ্ঠাগুলো ‘ডানা মেলার দিনলিপি’ নামে গ্রন্থভুক্ত হচ্ছে।
তখন মববাজির ঘটনা ছিল বিরল ও বিচ্ছিন্ন। এমন একটি ঘটনা উপজীব্য করে সদ্যতরুণ আমি মবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে, চলমান ঘটনাচক্র ও সময়ের বাস্তবতায় পৃষ্ঠাগুলোর পুনর্পাঠ গুরুত্বপূর্ণ।
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
সকালে হৈচৈ। খবর পেলাম, বাজারের মোড়ে এক চোর ধরা পড়েছে। ছুটে গেলাম। মাঠের মতো খোলা জায়গায় ভিড় জমেছে। লোকের চোখে উত্তেজনা। কারো হাতে লাঠি, কেউ পাথর হাতে মারমুখী। একজনকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।
আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। যেন বরফ হয়ে আছে আমার সময়। সামনে একজন মানুষের রক্তাক্ত, থেঁতলানো শরীর। বয়স খুব বেশি নয়, পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। কিছুক্ষণ আগেও লোকটি নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। এখন সে লাশ।
লোকজন বলছে, এদের এভাবেই শিক্ষা দিতে হয়! চুরি করতে এলে এমনই হবে! একজন বলল, আইন মাড়ানোর কী দরকার? বিচার আমরা করে দিয়েছি।
বাজারের সবজির গলিতে বেদনাভরা গোপনীয়তায় দুই লোকের আলাপ শুনলাম। তারা বলছে, ছেলেটার বাবা নেই। মা একা মানুষ। ছেলেটি দুই দিন ধরে খায়নি। একটি দোকানে চাল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। শুনে আমি স্তব্ধ। ভাবি, কে তাকে চোর বানাল? অভাব? অসাম্য? এই সমাজ? না আমরা সবাই?
পাবলিক বলছে, এভাবে সাইজ না করলে চোরেরা শিখবে না।
আমি ভাবলাম, কে শিখছে এখানে? আমরা কি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে শিখলাম? নাকি আরো নিষ্ঠুর হচ্ছি প্রতিদিন?
খুন করে নিষ্ঠুরগুলো খুশি। তারা কী তৃপ্তগলায় বলছে, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। চোরের এমনই পরিণতি হওয়া উচিত!
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
গতকাল নিহত ছেলেটার মুখ বারবার ভেসে উঠছে চোখে। তার রক্ত এখনো আমার চোখের পাতায় লেগে আছে। যখন ছেলেটার শরীর থেঁতলে দেওয়া হচ্ছিল, তখনো পুলিশ আসেনি। যখন এলো, সব শেষ। তারা একটি নিথর দেহ তুলে নিলো, নির্লিপ্তভাবে। কেন ঘটনার সময় পুলিশ ছিল না? নাগরিক সুরক্ষা ব্যর্থ হলো কেন? আমরা কি এমন এক সমাজ গড়ে তুলেছি, যেখানে পুলিশ কেবল লাশ তোলার গাড়ি? এ প্রশ্নের উত্তর নেই।
কারণ এখানে আইন নেই, শাসন নেই, আছে উত্তেজিত, অনিয়ন্ত্রিত জনগণ। এ এক আইনহীন রাষ্ট্রের বিকারের চিহ্ন। ঘটনার সময় ক্যামেরা তাক করেছিল একজন। লোকটি মরছে, তার ছবি তুলছিল বা ভিডিও করছিল। কেউ থামানোর চেষ্টা করেনি; বরং সম্ভবত উৎসাহ ছিল। টিভি পর্দায় উত্তেজক নিউজ বানানোর উচ্ছ্বাস।
মিডিয়ার কাজ ছিল এই হত্যার বিরুদ্ধে আর্তনাদ করা। তারা করল উল্টোটি। তারা রক্তাক্ত দৃশ্য বিক্রির প্রতিযোগিতায় নেমে গেল। যখন মিডিয়া বিবেক হারায়, ন্যায়পরায়ণতা মুছে ফেলে, তখন পুরো সমাজ নৃশংসতায় প্রশিক্ষিত হয়।
ভিড় কেন নির্মম? এ প্রশ্ন পীড়া দিচ্ছে সবচেয়ে বেশি। কেন তখন একজন সাধারণ মানুষের ভেতরের পশু গর্জে ওঠে? যে মানুষটি একা হলে হয়তো কাউকে আঘাত করতেন না, তিনি ভিড়ের মধ্যে পাথর ছুড়তে দ্বিধা করেন না কেন?
ভিড়ের যে লোকটি খুন করেছেন, আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি বলেন, আমার কিছু করার ছিল না, সবাই কাজটি করছিল।
এ এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক ফাঁদ। গ্রুপ সাইকোলজি বা গোষ্ঠী-মনস্তত্ত্ব এখানে মূল কাহিনী।
ভিড়ের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা বিলীন হয়ে যায়। দায়বোধ ব্যক্তিগত থাকে না, সবার পাতে ছড়িয়ে পড়ে।
ফলে আমি করিনি, সবাই করেছে- এমন আত্মপ্রতারণা জন্ম নেয়। উত্তেজনা, নিরাপত্তাহীনতা ও উন্মাদনা তখন একত্রে কাজ করে। যেন নৈতিকতার সব সীমা অদৃশ্য হয়ে যায়। আরেকটি কারণ অবদমিত রাগ, বেটাগিরি ও হতাশা। ব্যক্তি নিজের জীবনে যেখানে, সেখানে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। সেটা প্রকাশের নিরাপদ সুযোগ তালাশ করে। গণরোষের শিকার চোর ইত্যাদির মতো ‘নিরাপদ শত্রু’র ওপর লোকেরা অপ্রকাশিত বেটাগিরি উজাড় করে দেয়।
ভিড় তখন বিচারকে পরিণত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে বিচারকের জায়গায় থাকে না, শিকারির জায়গায় চলে যায়। মৃত্যু তখন উপভোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে, বিনোদন হয়ে ওঠে। এখানে ন্যায়ের ভ‚মিকা থাকে না। আমি যদি বিচারকের আসনে বসতাম, জিজ্ঞাসা করতাম, এই মৃত্যুতে কে দোষী?
১. সেই ছেলেটি?
২. বাজারের উত্তেজিত জনতা?
৩. পুলিশ প্রশাসন?
৪. মিডিয়া?
৫. নাকি পুরো সমাজ, যা একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে চোর বানাল?
আমি বলতাম, সব পক্ষ দোষী। তবে প্রধান আসামি রাষ্ট্র ও সমাজ, যারা মানুষের ক্ষুধা মেটাতে পারে না এবং যারা আইনের শাসন নিশ্চিত করে না।
সাধারণ মানুষ যখন ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই অশুভ কাজে লিপ্ত হয়, তখন অসাধারণ মাত্রার অশুভ ঘটে যায়। এই অশুভ তখন এলিটদের নয়। গণমানুষের নিজস্ব অশুভ, তাদের হাতেই তা বাস্তবায়িত হয়। এলিটদের অশুভ এই খেলার রেফারি। খেলার দু’পক্ষের নাম নাগরিক সন্ত্রাস বনাম রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা।
এই খেলা দেখিয়ে দেয়, আমাদের সভ্যতা খুব পাতলা পরতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য উত্তেজনা, নিরাপত্তাহীনতা বা গুজব এই স্তর গুঁড়িয়ে দেয়। নিচে বেরিয়ে পড়ে নগ্ন সহিংসতা।
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
গণপিটুনির ঘটনাটি ভাবাচ্ছে। ভাবছি আরেকটি দিক নিয়ে।
বাজার ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ হেঁটেছি। মাথার প্রশ্নটা ছিল সরল : কিভাবে এমন উন্মত্ততা জন্ম নেয় মানুষের মাঝে?
ভাবনা কখনো খালি হাতে ফেরায় না। একটি ধারণা জন্ম নিলো। মনে হলো, যদি কেউ নিজের ভেতরের শূন্যতার মুখোমুখি হতে ভয় পায়, তখন সে ভিড় তালাশ করে। ভিড় তাকে দেয় এক ধরনের অবলম্বন, ছদ্ম-পার্থক্যহীন নিরাপত্তা।
ভিড়ের মধ্যে সে আত্মপরিচয় ভুলে যায়। আগ্রহী হয়ে ওঠে কুৎসিত আনন্দে। ফলে ভিড়ের সহজ আনন্দ সম্মিলিত পাপাচার সহজ বা লঘু করে দেয়। কিছু পাপের জন্য মানুষ একা হতে চায়। আবার কিছু পাপ একা করতে পারে না। একা করতে ভয় পায়। ভিড়ের মধ্যে পাপের নৈতিক ভার বণ্টিত হয়, গুঁড়িয়ে যায়। তখন প্রত্যেকের অর্ধেক অর্ধেক দায়। ফলে মূলত দায়ী কেউই নয়, সবাই। এই অদৃশ্য দায়বণ্টনের মধ্য দিয়ে মানুষ পাপ করে আনন্দিত হয়। এই আনন্দ নিষ্ঠুরতার আনন্দ। এটি নিজেকে অতিক্রমের এক প্রকার নেশা এনে দেয়।
ভিড়ের মানুষ নির্মম হয়, কারণ সে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না। যখন সে হিংস্র হয়, কেবল তখন মনে করে- ‘আমি আছি। আমি শক্তিশালী।’ নিজের অস্তিত্ব ও জানান দেয়ার এই তাড়না তাকে খুনি বানায়। তখন দেখা যায়, রক্তাক্ত শরীরের পাশে দাঁড়িয়ে কেউ হাসছে। সে হাসে নিজের অস্তিত্বকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। সান্ত¡না হলো, ‘আমি জয়ী হয়েছি।’ এর মধ্য দিয়ে আসলে সে নিজের ভেতরের শূন্যতা ঢাকেমাত্র। এই জায়গা থেকে বারবার মনে হচ্ছে, ভিড়- সমাজের এক দেহহীন দেবতা।
ভিড়ের মধ্য দিয়ে এক নতুন সত্তা জন্ম নেয়, যাকে বলা যায় ‘ভিড়ের দেবতা’। এই দেবতা ন্যায়বোধ চায় না, চায় উন্মত্ত আত্মপ্রকাশ। সে জন্য দরকার উত্তেজনা। সে রক্তে তৃপ্ত হয়, মৃত্যুর উত্তেজনায় তুষ্ট হয়। ভিড়ের প্রত্যেক ব্যক্তি এই দেবতার অঙ্গ হয়ে ওঠে। নিজের বিবেক বিলুপ্ত করে দেয়। ফলে একজন শিক্ষিত, সংবেদনশীল মানুষও ভিড়ের মধ্যে নির্মম হতে পারে। কারণ তার ব্যক্তিসত্তা তখন নেই। তখন সে জনপ্রিয় আবেগের নামে রক্ত চায়, মৃত্যু চায়। এই চাওয়ার মাত্রায় যে যত তীব্র, সে জনতার তত বড় বীর!
মিডিয়ার ভ‚মিকা এখানে কেমন? আমার বিচারে মিডিয়া এখানে দৈত্যের আয়না। বাজারে দেখি কয়েকজন সংবাদকর্মী ছবি তুলছে, ভিডিও করছে। নিবিড়ভাবে দেখছে পরিস্থিতি। এই দেখার ধরনে আছে এক নির্মম নির্মাণ। সংবাদপত্র, টেলিভিশনের খবর নির্মাণ। ক্যামেরার পেছনের মানুষটি তখন আর মানবিক দর্শক নয়, বরং সে দৈত্যের আয়না। সে দেখতে চায়, রেকর্ড করতে চায়। কারণ সে নিজেও ভিড়ের নির্মম সুবিধার অংশীদার।
এখানে মিডিয়ার প্রযুক্তি নির্মমতা বাড়িয়ে দেয়। প্রত্যক্ষ দৃশ্যের পুনঃপ্রচার ভিড়ের দেবতাকে আরো পুষ্ট করে। প্রত্যেক ঘাতক বুঝতে পারে, আমি শুধু হত্যা করিনি, আমি এর স্মৃতিও তৈরি করেছি। গর্বের স্মৃতি। দৃষ্টান্তমূলক নজির।
এখানে পুলিশের ভ‚মিকা গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের বিলম্ব আমাকে ভাবায়নি; বরং ভেবেছি, পুলিশ এলে কী করতে পারত? তারা কি সমাজের এই গভীর অসুখ সারাতে চাইত? পারত?
উত্তর হচ্ছে এক বিরাট না। কারণ আইন তখন মৃত, ন্যায় তখন ছিন্নভিন্ন, ভিড় তখন দেবতাসুলভ। পুলিশ তখন দর্শক বা বাধাহীন সঙ্গীমাত্র। পুলিশ তো সমাজ থেকেই আসে। তাদের বিবেকও ভিড়ের দেবতার ছায়ায় আচ্ছন্ন।
শেষ পর্যন্ত মনে হলো, ভিড়ের নির্মমতা সমাজের অন্তর্লীন ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। এটি নগ্নভাবে উন্মোচন করে দেয় আমাদের শিক্ষার ব্যর্থতা, নৈতিকবোধের ব্যর্থতা, অর্থনীতির ব্যর্থতা ও ন্যায়বোধের ব্যর্থতা।
টিভি পর্দায় গণপিটুনির এ ঘটনার ভিডিও খুনিরাও দেখবে কাল? তাদের কাছে ব্যাপারটি হয়তো আরেকটি থ্রিল, আরেকটি বৈচিত্র্য, আরেকটি তুচ্ছ বিনোদন। এর পেছনে কোনো শোক নেই, অনুশোচনা নেই।
নিঃশ্বাস থেমে যাওয়া এক তরুণ দেহ, উত্তেজিত জনতার উল্লাস, আইনহীনতার নিষ্ঠুরতা এবং মিডিয়ার শীতল দর্শন আমার চার পাশে এক বেদনাময় বাস্তবতা হয়ে ঘুরছে।
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
সন্ধ্যা গড়াচ্ছে। হাঁটছিলাম বাজারের সড়কে। পেছনে মোড়ের সেই গলি, রক্ত শুকোতে বসেছে। পুরো একটি হত্যাকে মূল্য না দিয়ে হজম করে বসে আছে সমাজ। কী নির্মম!
কিন্তু কোন শক্তি আমাদের এত হিংস্র করে তোলে? আমি বিভিন্ন দিকে তালাশ শুরু করলাম। দেখি, এর পেছনে আছে বিচিত্র কারণ। কয়েকটি কারণ নোট করে রাখা দরকার :
১ . মানুষের প্রধান এক সঙ্কট হচ্ছে ‘অনুপস্থিত থাকার ভয়’। আমরা বাঁচি, যেন আমাদের অস্তিত্ব সজোরে ঘোষিত হয়। ভিড়ের মধ্যে সেই ঘোষণা সহজ হয়।
সে দিনের ভিড় একজোট হয়েছিল এক প্রয়োজনে; ‘আমি কেউ নই’ থেকে ‘আমি কেউ’ হয়ে ওঠার ছদ্মযাত্রায়। পিটিয়ে মেরে ফেলা এক অসহায় শরীরের সামনে দাঁড়িয়েছিল একদল অস্তিত্ব-উৎকণ্ঠিত মানুষ। কারণ অস্তিত্ব যখন অর্থহীন হয়ে পড়ে, মানুষ হিংস্রতার মধ্যে অর্থ খোঁজে।
২. স্বাধীনতা মানুষের মৌলিকত্ব। কিন্তু সেই স্বাধীনতার দায় বহন করতে হয়। গণপিটুনির মুহূর্তে এই দায় বহন না করে পরিহার করা যায়। ব্যাপারটি তখন ‘আমি নই, বরং আমরা’ হয়ে যায়। এই ‘আমরা’র ভেতরে ব্যক্তিগত বিবেক স্থগিত হয়। প্রত্যেকেই ভাবে, আমি তো শুধু অংশ, আমি সবার একজন ছিলাম।
সে স্বাধীনতার দায় থেকে পলায়ন করে দায়শূন্য হিংসায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পায়। সে দিন সেই দায়হীনতার উল্লাসই দেখলাম। চোখে উত্তেজনা, পায়ে লাথি, মুখে হাসি। এই হাসি অস্বস্তিকর। কারণ তাতে ছিল নিজের দায় অস্বীকারের উল্লাস।
৩. সবচেয়ে বড় মন্দ আসে তখন, যখন খুন করতে গিয়েও মানুষ ভাবে, আমি তো নিয়ম মেনে চলছি। যা সবাই করছে আমিও তাই করছি। সবাই যেহেতু করছে, ব্যাপারটি নিয়মে দাঁড়িয়ে।
বাজারের এই হত্যাকাণ্ড ঠিক এরকম। এটি সাধারণীকৃত মন্দ। এখানে কেউ মনে করেনি, আমি হত্যা করছি। ভেবেছে, আমি সমাজের প্রয়োজনে যা করার করছি, সমাজের সাথে অংশ নিচ্ছি। এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ তখন চরম নিষ্ঠুরতাও হয়ে ওঠে স্বাভাবিক সামাজিক আচরণ। এভাবে সমাজ নিজের বিবেককে লাঞ্ছিত করে হত্যাকে বৈধ করে তোলে।
৪. কিছু সাংবাদিক ছবি তুলেছে বা ভিডিও করেছে। কেউ ব্যক্তিগত ক্যামেরায় দৃশ্যটি ধারণ করেছে। তারা কাহিনী গড়ছে, সংরক্ষণ করছে। কিন্তু নৈতিকতা তাদের সাথে ছিল না। কারণ ব্যাপারটি তাদের কাছে শুধু খবর বা স্মৃতি। হয়তো কিছু উত্তেজনা, হয়তো কিছু কামাইও।
আধুনিক মিডিয়া অনুভ‚তির বদলে খবর তৈরি করে, ছবি প্রচার করে। সে ছবি বারবার দেখানো হবে নিউজ হিসেবে। একজনের করুণ মৃত্যু মিডিয়ার কাছে নিছকই নিউজ। এখানেই অপেক্ষা করছে আমাদের ভয়ঙ্কর বিপদ। আমরা সহিংসতাকে নৈতিকতা লঙ্ঘনের ঘটনা হিসেবে দেখাচ্ছি না। দর্শনীয় বিষয় হিসেবে দেখাচ্ছি।
৫. একটি সমাজ কীভাবে এত দ্রুত হিংসার দিকে যায়? যে সমাজ দ্রুতই হিংসার সিদ্ধান্ত নেয়, সেখানে গভীর এক অস্তিত্বগত ক্লান্তি কাজ করে। মানুষ জানে, তার জীবন অনির্দিষ্ট, অর্থহীন, গভীর অসমতায় আবৃত। এ অবস্থায় হিংসা তাদের এক আকস্মিক উত্তরণ দেয়। মুহূর্তের জন্য মনে হয়, আমি শক্তিশালী। আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি।
কিন্তু এই শক্তি আয়নার ভেতরের ছবিমাত্র। শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে আরো অর্থহীনতায় ছুড়ে ফেলে। নিজেকে আরো শূন্য, ক্লান্ত ও মলিন করে তোলে।
এসব উল্লাসের পরের মানুষগুলোর দিকে তাকান। দেখবেন তারা অস্বস্তিতে থাকে। ভিড় শেষ হয়ে গেলে চার পাশ ফাঁকা লাগে। কারণ প্রকৃতপক্ষে কেউ কিছু জেতেনি। শুধু হেরে গেছে সম্মিলিত বিবেক, মানবতা।
এসব ঘটনায় আছে নৈতিকতার পতন। আছে সমাজের অস্তিত্ব সঙ্কটের নগ্নতা। সমাজ যখন অর্থহীনতায় ডুবতে থাকা মানুষের জীবন অর্থবহ করতে পারে না, তখন অর্থহীন উল্লাসের পথ খোলা রাখে। বাজারের এই গণপিটুনি ছিল তেমনি অর্থহীন উল্লাস।
উন্মত্ত মানুষগুলো তখন খোদাকে অনুভব করছিল না। কারণ ভিড়ের উত্তেজনায় প্রত্যেকেই ছোটখাটো খোদা হবার দম্ভের কাছে ঝুঁকে পড়েছিল। যেখানে ন্যায়বোধ ক্লান্ত, নৈতিকতা ক্লিষ্ট, অস্তিত্ব অর্থহীন, সেখানে মানুষের মুখে নিষ্ঠুরতার হাসিই ফুটবে। এই হাসি জীবনের স্বাক্ষর নয়, বরং মরতে থাকার দলিল।
লেখক : কবি, সাহিত্যিক