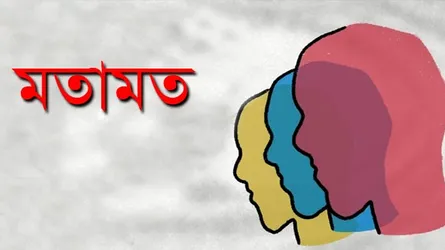সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এক অনন্য সৃষ্টিশীলতা উদযাপন করে। গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে মুসলমান কৃষক, জেলে, মাঝি-মাল্লা, মৃৎশিল্পী, তাঁতি, কামার-কুমার শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের মুখের ভাষায় গড়ে উঠতে থাকে একটি নতুন কথ্যভাষা- যাকে শনাক্ত করা হয় ‘যাবনী মিশাল’ নামে। এই ভাষা আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্তানি উপাদানে পরিপুষ্ট হলেও এর মূল আধার ছিল স্থানীয় বাংলা।
এই কথ্যভাষাকে কাব্যভাষার রূপ দিয়েছিলেন একদল প্রবল কবি, যারা ভাষায় যুক্ত করেছিলেন মানবিক ভাবধারা, সংস্কার ও আখ্যানশৈলী। এই সময়ে এখানে ‘সত্যপীর’ পাঁচালির ধারায় নানা পটভূমি থেকে উঠে আসা কবিরা ভিন্ন ভাষাশৈলীর সূচনা করেন, যা ছিল ভাষিক মিথস্ক্রিয়ার অসাধারণ উন্মোচন। এ সময় মুসলিম-হিন্দু সহাবস্থান এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের দৃষ্টান্ত ছিল বিস্তারণশীল। নানা অঞ্চলে এর নজির ছিল। ভুরশুট ও মান্দারন অঞ্চল এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারে। আজকের হুগলি জেলায় এ অঞ্চলের অবস্থান। এখানে বালিয়া, মণ্ডলঘাট ইত্যাদি পরগনায় অনেক কবি সত্যপীরের পাঁচালি রচনা করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- পেঁড়োর (পাণ্ডুয়া) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। হাফেজপুরের শাহ গরীবুল্লাহ, তাজপুরের আরিফ, ভুরশুটের সৈয়দ হামজা, চক-সাহাদাতের শের আলি, ধসা গ্রামের জনাব আলি প্রমুখ।
এসব রচনার মধ্যে ইসলামী ঐতিহ্যের অনুরণন ছিল, কুরআন, হাদিসের উল্লেখ ছিল, পীর, পাক পাঞ্জাতন, ফাতেমা বিবি ইত্যাদির মহিমাগান ছিল, আবার ছিল বাংলা লোকজ উপাদান, স্থানীয় চরিত্র, মিথ, জীবনাচার। ছিল ভাষাগত বৈচিত্র্যের লোকায়ত সম্মিলনী।
বাংলা কাব্যভাষায় যে ভাষাগত বৈচিত্র্য ঘটতে পারে, সেকালে তার ভালো উদাহরণ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার রচনায় সেকালের জবান ছিল হাজির। যে জবান আরবি-ফারসি-হিন্দুস্তানি শব্দসহযোগে বিকশিত হয়। তার মতে :
‘প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে।’
তিনি ‘অন্নদামঙ্গল’-এ লিখেছেন :
‘না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥’
এই উচ্চারণ কেবল একটি ভাষার নামকরণ নয়, বরং একটি সাহিত্যিক অবস্থান। এ ছিল এক বাস্তবতার ঘোষণা। বাংলা ভাষার সম্ভাব্য সব শব্দ, ছন্দ, সংস্কৃতি- সবকিছু আত্মস্থ করে একটি জনভাষাকে সাহিত্যভাষায় রূপান্তরের দাবি।
‘অন্নদামঙ্গল’-এর তৃতীয় খণ্ডে দিল্লি-আখ্যানে ভারতচন্দ্র যাবনী মিশাল বা মুসলমানি বাংলার অনুপম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। যেমন-
‘পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আজব কথায় ॥
‘সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরান।
ঝুটমুট পড়ি মরে আগম পুরাণ ॥
‘নাহোয় সুন্নত দেকে
কলমা পড়াঁও লেকে
জাতি লেঁউ খেলায়কে থুক ॥’
‘কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়,
ফাতেমা বিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড় ॥’
এমনতরো কাব্যে উচ্চারণ, কৌতুক, ব্যঙ্গ, পীর-ওঝা ও তাবিজ-কবচের নিখুঁত চিত্রায়ন এক অনন্য কাব্যিক নাটকীয়তা সৃষ্টি করে- যা তখনকার বাংলার সমাজজীবনের বর্ণময় প্রতিচ্ছবি। এই জীবনচিত্র বয়ান করার সামাজিক ভাষারূপ ছিল এটাই। মানে, কথিত যাবনী মিশালই ছিল হিন্দু-মুসলিমের সাহিত্যের ভাষা।
‘যাবনী মিশাল’ শব্দবন্ধে ‘যাবনী’ অর্থ বিদেশী। বিশেষত আরবি-ফারসি প্রভাবে, মিশেলে গঠিত ভাষারীতি। ভারতচন্দ্র এই নামকরণ করেই এর চরিত্র বিশ্লেষণ করেন- এ এক বহুভাষিক উদাহরণ, এক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা, যা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বাংলার দরবারি, কাব্যিক ও দৈনন্দিন জীবনের ‘যোগাযোগের ভাষা’ হয়ে উঠেছিল। যেভাবে মধ্যযুগে হিন্দুস্তানে ‘রেখতা’ বা ‘উর্দু’ ভাষার উদ্ভব হয়- তেমনই এই অঞ্চলে বাংলা ভাষার আত্মা থেকে এক বিশেষ রসসিঞ্চিত সংস্করণ জন্ম নেয়।
এই ‘যাবনী মিশাল’ ভাষায় লেখা কাব্য এক দিকে মুসলিম-হিন্দু ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম, অপর দিকে কবিদেরও কাব্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কৃষ্ণরাম দাস থেকে ভারতচন্দ্র হয়ে এক ধারাবাহিকতা তৈরি হয় যা উনিশ শতকে এসে ঔপনিবেশিক ভাষাশাসনের কবলে পড়ে।
যাবনী মিশালের মাধ্যমে ভাষা কেবল কাব্য-প্রকাশের মাধ্যম থাকেনি, বরং হয়ে ওঠে একটি সহাবস্থানভিত্তিক বহুস্বরিক সংস্কৃতির দলিল। ‘যাবনী মিশাল’ ভাষা সেই সমাজেরই প্রতিচ্ছবি, যেখানে ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন ভাষার মানুষ একসাথে জীবনযাপন করেছে। এই ভাষায় সত্যপীরের গানে যেমন মরমি প্রার্থনা, তেমনি ভারতচন্দ্রের শ্লেষে বিদ্ধ হচ্ছে রাজনীতি, ইতিহাস ও সমাজ।
এই ভাষার কাব্যিক ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কার করা মানে আমাদের সাহিত্যিক শিকড়ের গভীরে প্রবেশ করা- একটি সময়, একটি সমাজ, একটি ভাষাকে নতুন চোখে দেখা।
এই সাহিত্যধারার অন্যতম সূচনাকারী ছিলেন শাহ গরীবুল্লাহ, যিনি তার ‘ইউসুফ-জোলেখা’ কাব্যে তৎকালীন শাসনব্যবস্থার নৈতিক ছায়া কবিতায় ধারণ করেছেন। তার ব্যবহৃত ভাষা ‘মান্য বাংলা’ ছিল। তাতে আরবি-ফারসি শব্দের সুরঝংকারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি নতুন ভাষার অভিমুখ। কবি নিজেকে উপস্থাপন করেন এক দরবেশ, ফকির, প্রার্থনাকারী হিসেবে :
গরীব ফকির কহে কেতাবের বাত।
নায়েকের তরে আল্লা বাড়াও হায়াৎ ॥
এই প্রার্থনামূলক রীতি মুসলিম দরবেশ কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এমনতর বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভুরশুট-মান্দারন অঞ্চলে সাহিত্যিক চর্চার এক উজ্জ্বল কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। শাহ গরীবুল্লাহর সাথে ছিলেন তার শিষ্য সৈয়দ হামজা, যিনি ১৮০৪ সালে রচিত হাতেমতাঈ কাব্যের সময়কাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তিনি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান পেঁড়ো-বসন্তপুরে কিছু দিন কাটান, যা ভুরশুট অঞ্চলের সাথে তার প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক সংযোগ তৈরি করে।
ভাষাটি ছিল- বাংলা ব্যাকরণভিত্তিক, আরবি-ফারসি শব্দপ্রবণ, হিন্দুস্তানী ক্রিয়া-পদবিশিষ্ট, নিত্যদিনের কৌমজীবনের শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ। এই ভাষায় কেবল কাব্য নয়, ধর্মীয় উপদেশ, ঐতিহাসিক কাহিনী ও মানবিক অনুধ্যান একযোগে চলেছে।
এই ধারা হঠাৎ থেমে যায়নি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই ভাষায় কাব্যচর্চা চলে আসছিল। কলকাতার বিকাশের পাশে এবং উপনিবেশ-অনুমোদিত উচ্চশ্রেণীর নতুন ভাষাবিস্তারের জোয়ারেও শুধুমাত্র হুগলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই বহু কবিকে এই কৌমভাষার অনুশীলনে দেখা যাবে। অন্যত্র আরো অনেকেই এই ভাষার ধারক ও বাহক হিসেবে বিবেচিত হতেন। হুগলি অঞ্চলে তখন এই ভাষায় লিখছেন-
মালে মোহম্মদ, মুহম্মদ দানেশ, মুহম্মদ খাতের (বালিয়া), মুহম্মদ মুনশী, মুনশী আয়জাদ্দিন, বেলায়েত হোসেন, দায়েম উল্লাহ (বালিয়া)। তাদের রচনার ভাষা ও বিষয়বস্তু থেকে প্রতীয়মান হয় যে ‘যাবনী মিশাল’ কেবল ভারতচন্দ্র বা গরীবুল্লাহর কালে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি ছিল একটি চলমান সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি।
মানুষের মুখ থেকে উঠে আসা এই ভাষা ছিল বাংলা সাহিত্য ও সমাজের সংমিশ্রণের একটি চিহ্ন, যেখানে চাষি ও শ্রমজীবী মানুষের মুখের ভাষা কবিতা ও সাহিত্যভাষায় তুলে আনা হয়।
কেমন ছিল এর ব্যাকরণ : কাঠামো ও রীতি?
এখানে ক্রিয়ার রূপ বাংলার মূল ধাতুগুলো ঠিক রেখেছে এবং স্থানীয় কথ্যরীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- ‘কহে গরীব ফকির’, ‘চলে যায়’, ‘লইয়া আসে’, ‘রাখিবে’। এসব ক্রিয়াপদ আজও গ্রামীণ বাংলায় ব্যবহৃত হয়।
পদগঠন ও শব্দ-বিন্যাসে বাংলার মূল শব্দ-বিন্যাস ও পদক্রম (Subject–Object–Verb) অপরিবর্তিত। তবে শব্দ এসেছে বিচিত্র ভাষা থেকে। যেমন- ‘উজীর দিল হুকুম করিতে লড়াই’। ‘উজীর’ ফারসি, ‘হুকুম’ আরবি, লড়াই হিন্দি। কিন্তু বাক্য গঠনের ধাঁচ খাঁটি বাংলা। এই ভাষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষার শব্দভাণ্ডারের মিশ্র প্রকৃতি, শব্দ-সংকরতা।
‘আল্লা’, ‘নবী’, ‘কিয়ামত’, ‘দোয়া’, ‘ফজিলত’ ইত্যাদি ধর্মীয় শব্দ আরবি-ফারসি থেকে এলেও বাংলা বাক্যে বিগলিত। যেমন ‘আল্লা জানে কার কপাল কী’, ‘নবীর প্রেমে পাগল হইয়া গেল’।
দরবারি ও সামাজিক শব্দ স্থায়ী ও গভীর প্রভাব রেখেছে। যেমন ‘বাদশা’, ‘বিবি’, ‘নিকা’, ‘জাহাজ’, ‘দরবার’, ‘খাজাঞ্চি’, ‘ওজির’ ইত্যাদি। এগুলো ফারসি/উর্দু শব্দ। কিন্তু স্থানীয়তায় তারা আলো-বাতাসের মতো একাত্ম। যেমন- ‘বাদশার আজ্ঞা হইল’, ‘নিকা দিল বাদলের দিনে’ এখানেও গ্রাম্য শব্দের সহাবস্থান ছিল সহজ, সুগম। বিদেশী শব্দের পাশে একেবারে দেশজ, লোকভাষা বা আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আরামে, নিরুপদ্রবে। যেমন- বিবি গেল জলে/ওঝা ডাকে ভুতে কিংবা গতরে আতর মাখি দেখাবে তাকত/গাজী পীরের লাগি আগে করিল মানত।
এই যে সহাবস্থান, তা ভাষাকে করেছে লোকায়ত, বর্ণময়। এই ভাষার সাহিত্যরূপ মূলত পদ্যে বিকশিত হয়। বেশির ভাগ পুঁথি চৌপদী, সর্গীয়, কিংবা গীতিমালার ঢঙে রচিত হয়।
গরীবউল্লাহর ইউসুফ-জোলেখা থেকে উদাহরণ লক্ষ করা যাক :
ইউসুফ জোলেখার গীতপালা হৈল সায়,
লেহ ভাই আল্লার নাম দিন বহে যায়।
গরীব ফকির কহে কেতাবের বাত,
নায়েকের তরে আল্লা বাড়াও হায়াৎ।
এখানে ছন্দ, অনুপ্রাস, ধর্মীয় ভাষা ও লোকস্বর একসাথে কাজ করছে। এই ভাষায় অর্থপ্রবণতা : ধর্ম, প্রেম ও সামাজিক বাস্তবতা ছিল বিশেষ চরিত্রসম্পন্ন। এই ভাষার সেরা নমুনাগুলোর মধ্যে ‘হাতেমতাই’, ‘আমির হামজা’, ‘গুলে বকৌলি’- সবই লোকরসের রঙে লেখা।
ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; ভাষা এক মানবিক আত্মপ্রকাশের জায়গা, এক ‘বৌদ্ধিক বাসস্থান’। হাইডেগারের বিচারে ভাষাই মানুষের অস্তিত্বের পরিসর নির্মাণ করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যাবনী মিশাল ভাষা কোনো কাব্যিক কৌতুক নয়, বরং তা ছিল এক বহুস্বরিক ও সাংস্কৃতিক চৈতন্যের দার্শনিক অবয়ব। এই নামটির মধ্যেই নিহিত একটি দার্শনিক গতি-একটি ভাষা, যা নিজের সীমারেখা অতিক্রম করে।
এই ভাষা বহু উৎসভিত্তিক (বাংলা, ফারসি, আরবি, হিন্দুস্তানি), বহু ধর্মের ছায়ায় বিকশিত (হিন্দু পৌরাণিকতা, ইসলামী আখ্যান), বহু শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ছায়াপথে চলে (রাজদরবার, দরবেশী সমাজ, কৃষিজীবী জনতা)।
তাই ‘যাবনী মিশাল’ ভাষা দার্শনিকভাবে দাঁড়ায় ‘হাইব্রিডিটির’ (hybridity) এক উচ্চতর রূপ- যেখানে ভাষা একক সংস্কৃতি বা পরিচয়ের মালিকানা দাবি করে না, বরং বহু সংস্কৃতির মধ্যে গীত হয় একসাথে। এই অন্তর্ভুক্তি দেরিদার différance তত্ত্বের মতো- যেখানে ভাষার অর্থ নির্ধারিত হয় অনবরত ভিন্নতা ও বিলম্বের প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ, যাবনী মিশাল ভাষা কোনো স্থির ‘সত্তা’ নয়; বরং তা চলমান ও সম্পর্কনির্ভর। যাবনী মিশাল ভাষা শরীরী, মুখনির্ভর, শ্রুতিধর্মী। এর শব্দ প্রয়োগের মধ্যে উচ্চারণের সজীবতা আছে।
এই ভাষা তাই দেরিদার Logocentric ধারণার বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়- এখানে লেখা নয়, মুখের ভাষাই প্রাথমিক। এটি ‘লোকের ভাষা’, ‘প্রান্তের ভাষা’, ‘শ্রমজীবী চৈতন্যের ভাষা’। এই দেহজ উচ্চারণই এক বিশেষ দর্শনের ভিত্তি গড়ে তোলে- যেখানে ভাষা কোনও দেবভাষা নয়, বরং মানুষের মুখ ও মাটি থেকে উঠে আসা এক জীবন্ত প্রবাহ।
ভারতচন্দ্রের বক্তব্যই এই ভাষার দার্শনিক আত্মবিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ দলিল :
‘যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে।’
‘অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥’
এখানে ‘যে হৌক সে হৌক ভাষা’ কথাটি ভাষার শ্রেণিবিন্যাস, ধর্মবিভাজন, আভিজাত্যবোধ- সবকিছুর বিরুদ্ধ ঘোষণা। ভাষাকে তিনি তার নন্দনশক্তি দিয়ে বিচার করেন, উৎস বা উৎসারিত শ্রেণী দিয়ে নয়। এটি এক নিঃশর্ত ভাষাগত মুক্তির দর্শন।
দার্শনিকভাবে যাবনী মিশাল কোনো নিরীহ কাব্যিক প্রয়োগ নয়; এটি ছিল অস্তিত্ববাদী ভাষা-রাজনীতির প্রকাশ। এটি এমন একটি ভাষা যা- ক. জাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষার সীমা অতিক্রম করে, খ. জনতার মুখ থেকে উঠে আসে, গ. ‘অপর’-কে অন্তর্ভুক্ত করে নিজের পরিধি বিস্তৃত করে, ঘ. সাহিত্যে ‘ভাষার নিরঙ্কুশতা’ নয়, বরং ‘সংলাপের বহুত্ব’ রক্ষা করে। এটি দেখায়, কিভাবে সাহিত্য কেবল শিল্প নয়, বরং এক দার্শনিক সংলাপ- সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সত্তাকে একত্র করে নতুনতর চৈতন্য নির্মাণের উপায়। যাবনী মিশাল ভাষা এক সাম্যের দর্শন। এটি প্রান্তের ভাষাকে কেন্দ্র করে তোলার এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব।
সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার কৌম-সমাজে যে কথ্যভাষা প্রচলিত ছিল, পুঁথিসাহিত্য তার সাহিত্যিক রূপ। এই ভাষা ছিল বাংলা ভাষার শরীরে হিন্দুস্তানি, ফারসি, আরবি শব্দের চর্চা-ভিত্তিক এক জীবন্ত লোকভাষা।
একাধিক সংস্কৃতি, পরিচয় বা ভাষার মিলনস্থলে যে নতুন কিছু তৈরি হয়-তাকে বলা হয় হাইব্রিডিটি। এটি শুধু দু’টি জিনিসের যোগফল নয়, বরং এক নতুন রূপ, এক নতুন পরিচয়, এক নতুন মানে। যেখানে পুরনো ও নতুন, উপনিবেশ ও উত্তর-উপনিবেশ, সবকিছুর সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে নতুন সত্তা।
উপনিবেশ অনুমোদিত কলকাতার ভাষাকুশলী ব্যাকরণ বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে যাবনী মিশেলের ধারা থেকে। উপনিবেশিত মানুষের ভাষাকে করেছে বেমানান। এখনো তাকে বেমানান করে রাখা হয়েছে ক্ষমতার ভাষা দিয়ে। কিন্তু যখন উপনিবেশকারী ও উপনিবেশিত ভাষা-সংস্কৃতি মুখোমুখি হয়, তখন তাদের মধ্যকার দ্বৈততা ভেঙে গিয়ে এক তৃতীয় স্থান তৈরি হয়। এই তৃতীয় স্থান হলো এমন এক জায়গা, যেখানে নতুন অর্থ তৈরি হয়, নতুন পরিচয় গঠিত হয় এবং বিদ্যমান ক্ষমতার ভাষা চ্যালেঞ্জ করা হয়।
যাবনী মিশাল ভাষা হলো এই ‘তৃতীয় পরিসর’- যেখানে সে ব্যাকরণ নয়, কর্তৃপক্ষ নয়, অনুমোদন নয়, নিয়মের রক্তচক্ষু নয়, কিন্তু চলমান। সে চলমান জনতার জবানের নিয়মে। এটাই তার চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। জনতার জবান যত ভাষার যত শব্দ অধিগ্রহণ করছে, তত ভাষার তত শব্দ এই ভাষার অধিগত। এ এক মধ্যবর্তী ভাষা, যা ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক ‘বর্ডার’-এর চরম পুনর্বিবেচনা ঘটায়। এটি কেবল জাগতিক ‘সার্বজনীনতার’ (universality) নয়, বরং পারস্পরিকতার ভাষা (relational language)। এর পুনরুজ্জীবন কেন নয়?
বাংলাদেশ যখন নিজের সাহিত্যিক ও ভাষিক আত্মতার তালাশ করছে, তখন পুঁথির পাতায় লুকিয়ে থাকা আমাদের লোকভাষার পুনরুজ্জীবন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি কেবল জবানের জীবনের জন্য নয়, আমাদের তাহজিব-তমদ্দুনের জীবনের জন্যও জরুরি।
লেখক : কবি, সাহিত্যিক
[email protected]