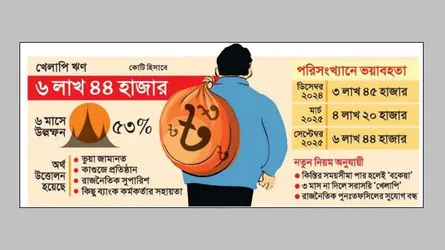অর্থনৈতিক বৈষম্য শুধু সম্পদ বা আয়ের সংখ্যাগত ব্যবধান নয়, বরং তা এক বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার বহুমাত্রিক প্রতিফলন। এই ব্যবধান সমাজে ক্ষমতা, সুযোগ ও মর্যাদার অসাম্যের চিত্র হাজির করে। ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের আলোচনা কেবল অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা ন্যায্যতা, অধিকার ও রাষ্ট্রনৈতিক নৈতিকতার প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে।
ন্যায্যতা হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রথম গুণ। সেটা হারালে প্রতিষ্ঠানগুলোর চরিত্রে যুক্ত হয় বৈষম্য। অর্থনৈতিক বৈষম্য তখনই ভয়াবহ হয় যখন তা মানুষের বিকাশের মৌলিক সামর্থ্য সীমিত করে ফেলে। আমাদের প্রেক্ষাপটে এই সীমাবদ্ধতা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে। একই সাথে বিচার, মর্যাদা, প্রতিনিধি ক্ষমতা ও সামাজিক অংশগ্রহণ থেকেও বঞ্চিত রাখে।
এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ও কাঠামো একটি নৈতিক প্রশ্নের মুখে থমকে দাঁড়ায়। প্রশ্নটি হলো, কার অবস্থান কোথায় থাকবে? কে কোন সুবিধায় প্রবেশ করতে পারবে? কে কিসের ওপর, কতটুকু অধিকার পাবে? এসব প্রশ্নের জবাব নির্ধারণের কাজ শুধু বাজারের উপর ছেড়ে দিলে চলে না। এখানে প্রয়োজন ইনসাফভিত্তিক এক তাকাদ্দুমি (অগ্রগামী) সমাজচিন্তা- যা সম্পদের বণ্টন ও প্রবেশাধিকারে সুবিচার নিশ্চিত করে।
বৈষম্যের বিপরীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জোরালো প্রয়াস এদেশে অভ্যুত্থানে রূপায়িত হয়েছে। জুলাই ২০২৪ এ জেন-জি’র লাল সংগ্রাম শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন স্বৈরতন্ত্রকে পরাজিত করে। হাসিনা পালাতে বাধ্য হন। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিদের বৈষম্যমূলক কোটাদানের ফলে তরুণদের মধ্যে বঞ্চনার যে বোধ সঞ্চারিত হয়, সেটা প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ হয়। শেষ অবধি বৈষম্যপ্রধান আদত কাঠামোকেই সে চ্যালেঞ্জ করে। বৈষম্যের বদলে সে অন্তর্ভুক্তির প্রতিষ্ঠা কামনা করে।
জুলাই অভ্যুত্থান যদি কেবল রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে সীমিত না থাকতে চায়, তাহলে তাকে এই দীর্ঘস্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ন্যায্যতার স্পষ্ট দাবি উচ্চারণ করতে হবে। এটি হবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নৈতিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে নাগরিক চেতনার এক ঐতিহাসিক জবাব।
এই অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বিশ্লেষণ করা জরুরি। একই সাথে জরুরি হলো সম্পদের ন্যায্য বণ্টন ও প্রবেশাধিকারের সুবিচারের ধারণা তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা।
কোনো একক অর্থনৈতিক ডাটার ভিত্তিতে এখানে বিশ্লেষণ করছি না। বরং রাষ্ট্রের নৈতিক চুক্তি, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক ন্যায়বোধের আলোকে বৈষম্য ও সম্পদনীতিকে পুনঃচিন্তার চেষ্টা করছি। আমরা বিশ্বাস করি, বৈষম্য শুধু উন্নয়নের অন্তরায় নয়, বরং তা রাষ্ট্রীয় সত্তা ও নাগরিকত্বের মধ্যে এক মৌলিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্বকে নিরসন করতে গেলে রাষ্ট্রকে শুধু উন্নয়নে সক্ষম হলেই চলে না, বরং তাকে হতে হবে ন্যায্যতাকেন্দ্রিক ও মানবিক।
অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত উন্নয়নশীল একটি দেশ হিসেবে পরিচিতি অর্জন করলেও বাংলাদেশের ভেতরে লুকিয়ে আছে ব্যাপক ও বহুমাত্রিক বৈষম্য। বৈষম্যের ডালপালা বিস্তৃত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ভূগোলভিত্তিক এবং নৈতিক স্তরে। বৈষম্যের প্রধান প্রকাশ আয় ও সম্পদে, কিন্তু তার পরিধি শিক্ষা, মর্যাদা, প্রতিনিধিত্ব, বিচার ও পরিবেশের মতো মৌলিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও প্রসারিত। গ্রাম ও শহর অঞ্চলের পার্থক্য, নারীদের সাথে জুলুম ও বঞ্চনা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকারহীনতা প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বিভক্ত করছে।
একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটছে, অন্যদিকে প্রকট হচ্ছে ন্যায়ভিত্তিক বিকাশের অভাব। যা রাষ্ট্রকে এক নৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যেখানে উন্নয়ন কেবল শক্তিমানদের জন্য, দুর্বলদের জন্য নয়। রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় নৈতিকতা ও সামাজিক জবাবদিহির অভাবে বৈষম্য আরো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিচ্ছে।
১. অর্থনৈতিক বৈষম্য :
বাংলাদেশের বৈষম্যের সবচেয়ে দৃশ্যমান, পরিমাপযোগ্য ও রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল স্তর হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য। এটি শুধু আয়ের ফারাক নয়, বরং তা এক বহুব্যাপ্ত কাঠামো। যার মধ্যে আছে সম্পদে প্রবেশ, চাকরির সুযোগ, কর-নীতি, জীবনের নিরাপত্তা ও উৎপাদনে অংশগ্রহণের মতো বিষয়।
এই স্তরটি বিশ্লেষণ করতে আমরা তিনটি পরিসরের দিকে নজর দেবো। যথা -
১.১. আয় ও সম্পদের বৈষম্য :
২০২২ সালের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের Gini coefficient হলো 0.499, যা বৈষম্যের একটি উচ্চস্তরের সতর্কসূচক।
বিগত দশকগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বটে। কিন্তু মূল সম্পদের অধিকাংশ উচ্চ আয়ের গোষ্ঠীর দখলে। যেমন :
ক. শীর্ষ ৫ শতাংশ মানুষের হাতে মোট জাতীয় আয়ের ২৭ শতাংশ, যেখানে নিচের ৫০ শতাংশ পায় মাত্র ১৪ শতাংশ।
খ. শহর-গ্রাম বৈষম্য প্রবল : একদিকে গ্রামীণ কৃষকের মাথাপিছু জমি হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে নগর-মালিক শ্রেণি জমি ও ফ্ল্যাটের মালিক হচ্ছে।
১.২. শ্রমবাজার ও পেশাগত বণ্টন :
বাংলাদেশের শ্রমবাজার একটি অনিরাপদ, অনানুষ্ঠানিক ও বৈষম্যপূর্ণ কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। প্রায় ৮৫ শতাংশ কর্মসংস্থান এখনো অনানুষ্ঠানিক, যেখানে নেই শ্রম-সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা বা নিয়োগনীতির স্বচ্ছতা। নারী শ্রমিকরা একই কাজে পুরুষের চেয়ে ২০-৩০ শতাংশ কম পারিশ্রমিক পান। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কার্যত শ্রমবাজারের বাইরে। অর্থনীতি কেবল ধনীদের জন্য কাজ করছে। দীর্ঘমেয়াদে তা সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করবে।
১.৩. উৎপাদনে অংশগ্রহণ ও মূলধনে প্রবেশাধিকারের বৈষম্য :
অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কেবল আয় নয়, উৎপাদন সম্পদে প্রবেশাধিকার গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু
ক. ক্ষুদ্র কৃষক ব্যাংকঋণে প্রবেশ করতে পারেন না। পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় এবং পরিচয় না থাকায়।
খ. সরকারি সহায়তা মূলত শহুরে ও সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
এই কাঠামোগত বৈষম্য অর্থনীতিকে সাংবিধানিক সাম্যনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। বৈষম্যের এই বাস্তবতায় আমরা প্রস্তাব করছি সম্পদের ন্যায্য বণ্টন ও প্রবেশাধিকারের ধারণা।
২. সম্পদের ন্যায্য বণ্টন ও প্রবেশাধিকার : তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত
অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু হলো সম্পদের ন্যায্য বণ্টন ও তার প্রবেশাধিকারের সুবিচার। এটা নিশ্চিত হওয়ার মানে হলো সমাজে ক্ষমতা, সুযোগ ও মর্যাদার সুষম বণ্টন নিশ্চিত হওয়া।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সম্পদের এই ন্যায্যতা শুধু আয়বণ্টনে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে জমি, পুঁজি, প্রযুক্তি ও সামাজিক সম্পদে প্রবেশাধিকারের ব্যাপারটি গুরুত্ব। এখানে সমতা নিশ্চিত করতে হবে।
২.১. এখানে খোলাসা করার প্রথম বিষয় হলো সম্পদের ন্যায্য বণ্টন বলতে আমরা কী বুঝাচ্ছি? এর তাত্ত্বিক ভিত্তি কী? আমরা মনে করি, সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের মূলনীতির কেন্দ্রে থাকবে সমাজের সব সদস্যকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধায় সমান অধিকার প্রদান। সর্বনিম্ন অবস্থার মানুষের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এর মানে, সম্পদের বণ্টনের মধ্য দিয়ে সামর্থ্যরে প্রসার ঘটবে। তা কেবল কেন্দ্রীভূত হবে না। বণ্টন ব্যবস্থা ব্যক্তির বিকাশের বাস্তব সুযোগ নির্ধারণ করে দেবে।
আমাদের বিচারে সম্পদের বণ্টন নিছক সম্পদের বণ্টন নয়। এর সাথে সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি ও অংশগ্রহণের সংযোগের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ সম্পদ বিতরণকে একক মাত্রায় সীমাবদ্ধ না করে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে ।
২.৩. খোলাসা করার দ্বিতীয় বিষয় হলো প্রবেশাধিকারের সুবিচার। এর গুরুত্ব কোথায়?
আমাদের মতে, সম্পদের ন্যায্য বণ্টন তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন জাতীয় সম্পদে সব নাগরিকের সমান প্রবেশাধিকার থাকে। কিন্তু এখানে বাধা হিসেবে দাঁড়াবার জন্য তৈরি থাকে অনেকেই।
যেমন আর্থিক বাধা, সামাজিক, নৈতিক বা সাংস্কৃতিক বাধা। এসব প্রতিবন্ধকতা সম্পদের সুযোগকে অপ্রতুল করে তোলে এবং বৈষম্যকে প্রকট করে।
বাংলাদেশে জমি ও পুঁজি ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারের বৈষম্য দরিদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য সবচেয়ে সঙ্কটময়। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে জমির মালিকানার একচেটিয়া প্রবণতা, যেখানে মোট জমির প্রায় ২০ শতাংশ মালিকানায় ৫ শতাংশ পরিবার অংশীদার।
ভূমি মালিকানায় অসাম্য বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির একটি দীর্ঘস্থায়ী বৈশিষ্ট্য। এখানে ভূমি সংস্কারকার্যক্রম থাকলেও তার বাস্তবায়ন কম। রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতির ফলে বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে ভূমিহীন কৃষকরা উৎপাদনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় কম। দারিদ্র্যের চক্র থেকে তারা মুক্তি পায় না।
২.৩. পুঁজিসম্পদ ও প্রোডাকশন অ্যাসেটের প্রবেশাধিকারেও বাধা তীব্র।
এখানে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদনমূলক পুঁজিতে প্রবেশাধিকার দরিদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণীর জন্য সীমিত। আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার অনেক সময়ই বড় মালিক ও করপোরেটের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সাধারণত ছোট উৎপাদক ও উদ্যোক্তারা প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পেতে ব্যর্থ হন। আর্থিক নিরাপত্তার অভাবে দরিদ্র পরিবারগুলো অনিশ্চিত জীবনযাপনে বাধ্য হয়।
পুঁজি, ঋণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থায় প্রবেশের সুযোগও গরিব শ্রেণীর জন্য ভীষণ সঙ্কুচিত। অপর দিকে সরকারি সম্পদ বণ্টনে স্বচ্ছতার অভাব এবং রাজনৈতিক দখলদারিত্ব ভয়াবহ, যা সম্পদে গরিবের প্রবেশাধিকারে বাধা সৃষ্টি করে।
৩. বৈষম্যরোধ ও ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করতে জুলাই কী করবে?
এই বহুমাত্রিক বৈষম্য থেকে উত্তরণের জন্য একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রচিন্তার প্রয়োজন। জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিরিট ও দাবি এখানে কী কামনা করবে? কোন কোন পরিবর্তন ও সংস্কার নিশ্চিত করবে? মোটাদাগে কিছু দিক হাজির করছি।
৩.১. আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাসে কর ও সম্পদনীতির সংস্কার :
ক. প্রগতিশীল করনীতি চালু করা
উচ্চ আয়ের গোষ্ঠীর ওপর প্রগতিশীল আয়কর হার কার্যকর করতে হবে।
সম্পদ, জমি ও উত্তরাধিকার করকে কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক করতে হবে।
খ. সম্পদ কর ও পুনর্বিনিয়োগ নীতি
বহুজমি, অচল সম্পদ ও বহু ফ্ল্যাট মালিকদের জন্য সম্পদ কর আরোপ করে তা প্রান্তিকদের আবাসন-নিরাপত্তায় ব্যয় করতে হবে।
কৃষিজমির পুনর্বিন্যাস ও ভূমি কার্যকর করতে হবে।
গ. গ্রাম-শহর ভারসাম্য রক্ষা
অবকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিনিয়োগ গ্রামে বাড়িয়ে শহরকেন্দ্রিক সম্পদ প্রবাহ কমাতে হবে।
কৃষিভিত্তিক শিল্প ও নগর-গ্রামীণ সংযুক্তি উন্নয়নে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।
৩.২. শ্রমবাজার ও পেশাগত বৈষম্য কমাতে সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায্য পারিশ্রমিক আইন :
ক. শ্রমিকের ন্যূনতম অধিকার ও সুরক্ষা :
অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য ইউনিফর্ম ন্যূনতম মজুরি ও কাজের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।
শ্রমিক রেজিস্ট্রেশন ও মোবাইল ভিত্তিক ডিজিটাল শ্রম-পরিচয়পত্র চালু করতে হবে।
খ. নারী শ্রমিকদের সম-মজুরি
একই পেশায় সমান পারিশ্রমিক বাধ্যতামূলক করার জন্য ন্যাশনাল ওয়ার্কফোর্স অডিট চালু করতে হবে।
মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা, ডে-কেয়ার সেবা ও নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করতে হবে।
গ. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ
ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও হিজড়াদের জন্য পেশাগত কোটা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে হবে।
৩.৩. উৎপাদন ও মূলধনে অংশগ্রহণে অর্থনৈতিক ইনসাফ :
ক. সুলভ সহায়তা ও ক্ষুদ্র উৎপাদক বান্ধব ব্যাংকিং
জামানতবিহীন ঋণ, ইসলামী সামাজিক তহবিল (ওয়াক্ফ, জাকাত, সাদাকা) ইসলামের সাপেক্ষে পুনর্গঠন করতে হবে এবং গ্রামীণ অর্থায়ন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।
কৃষিজাত ও কারুশিল্প উৎপাদকদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ও বাজার সংযোগ দিতে হবে।
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য পুঁজিসম্পদ ও প্রযুক্তিতে সহজ প্রবেশ, টেকসই কৃষি ও শিল্পায়নে সহায়তা। প্রান্তিকদের জন্য করজে হাসানাহ ও উদ্ভাবনী আর্থিক পরিষেবা।
খ. সরকারি সহায়তা ও নীতিতে গ্রামীণ অংশগ্রহণ
উপজেলা পর্যায়ে উৎপাদনভিত্তিক সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।
সহযোগিতা বণ্টনের নীতিতে ‘নির্দিষ্ট বরাদ্দ’ ও ‘সমবায়ভিত্তিক বণ্টন’ মডেল আনতে হবে।
৩.৪. সামগ্রিকভাবে জুলাইকে দাবি করতে হবে :
১. ‘অর্থনৈতিক ন্যায়ের কমিশন’ গঠন করে বৈষম্য বিশ্লেষণ, মনিটরিং ও সুপারিশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
২. সংবিধানের ১৯(১) ধারার আলোকে, অবিচারের বিলুপ্তি ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রীয় নীতিতে।
৩. রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণে প্রান্তিক জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ।
৪. ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের জন্য কার্যকর ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা এবং সম্পদ বণ্টনে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রবর্তন।
৫. প্রবেশাধিকারে বাধা দূরীকরণে আইনগত ও সামাজিক সংস্কার।
৬. ভূমি সংস্কারের পুনর্বিবেচনা, তথা জমির ন্যায্য বণ্টন ও ব্যবহারে কাঠামোগত পরিবর্তন।
বৈষম্য যখন প্রাতিষ্ঠানিক হয়, তখন তাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? তা কি অর্থনৈতিক ব্যর্থতায় সীমাবদ্ধ? মোটেও নয়। বরং তা এক রাষ্ট্রনৈতিক ও নৈতিক ব্যর্থতার নামান্তর। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ভাষা যতই জাঁকালো হোক, প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন যদি সমাজের প্রান্তিক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত না করে, তবে সেই উন্নয়ন আত্মঘাতী। কারণ, উন্নয়ন তখন এক বিশেষ গোষ্ঠীর সুবিধা সরবরাহ করে, সম্মিলিত জনগণের হক হরণ করে।
জুলাই অভ্যুত্থান এই বৈষম্যপ্রবণ কাঠামোর বিরুদ্ধে এক সামাজিক চেতনার জাগরণ। জুলাই কেবল ক্ষমতা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের একটি নৈতিক দাবি। জুলাই মনে করিয়ে দেয়, রাষ্ট্র কেবল আইন প্রয়োগকারী একটি সংগঠন নয়; বরং তা একটি নৈতিক প্রতিশ্রুতি। রাষ্ট্র সমান মর্যাদা, সুযোগ এবং অধিকার দেয়ার একটি চুক্তি।
শাসন নয়, সঙ্গতি; নিয়ন্ত্রণ নয়, ন্যায্যতা; ক্ষমতা নয়, ইনসাফ-এই তিন নীতির বুনিয়াদে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন জরুরি। একটি প্রকৃত জনকল্যাণী রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো অন্তর্ভুক্তি, সমতা ও সম্পদের সুবিচার, যার মাধ্যমে নাগরিক কেবল শাসিত নয়, বরং রাষ্ট্রচরিত্রের সক্রিয় অংশীদার হয়ে ওঠে।
এই রচনা এক রাজনৈতিক নৈতিকতার আহ্বান। সে বলছে, কেবল সম্পদের মালিকানার প্রশ্নে নয়, বরং সুযোগের ন্যায্যতা দিচ্ছে কিনা, তা দিয়ে আমরা রাষ্ট্রকে বিচার করব। রাষ্ট্রকে তার দুর্বল নাগরিকের সাথে চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। তাদের শুধু টিকে থাকলে চলবে না, বিকশিত হতে হবে।
জুলাই অভ্যুত্থানের তাৎপর্য এখানেই। সে আমাদের প্রশ্ন করছে- রাষ্ট্র কার? উন্নয়ন কার জন্য? ইনসাফ কাদের অধিকার? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে উন্নয়ন হবে কেবল মুষ্টিমেয় মানুষের বিলাসিতা, বাকিদের জন্য তা নিপীড়নের দীর্ঘশ্বাস।
এই প্রেক্ষাপটে, ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এটি শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়- এ হচ্ছে মানবিকতার এক অবিচ্ছেদ্য দায়িত্ব।
লেখক : কবি, সাহিত্যিক
[email protected]