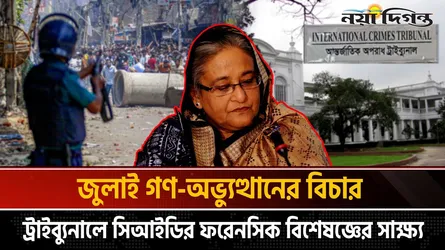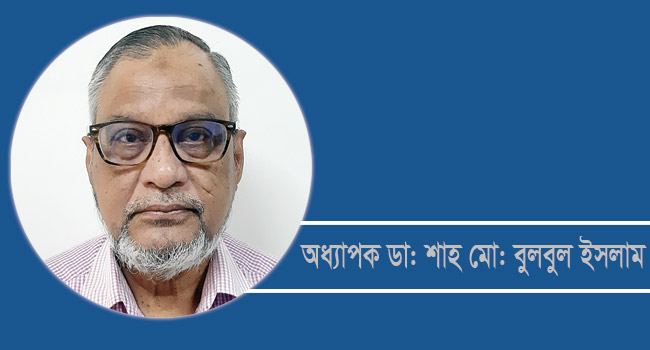শৈশবের কথা। চৈত্রসংক্রান্তি বা পয়লা বৈশাখ বোঝার বয়স তখনো আমার হয়নি। তবে কিছু ঘটনা, কিছু আচারের কথা স্পষ্টতই মনে আছে। চৈত্রের শেষ দিনে গ্রামের পাড়ায়, পাড়ায়, বাড়িতে, বাড়িতে উৎসবের আমেজ বিরাজ করত। গ্রামে তখন কদাচিৎ পাকা বাড়ি দেখা যেত। অধিকাংশ বাড়িই ছিল মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরি। কিছু ছিল মাটির উঁচু ভিটার ওপর চারচালার বাড়ি। দেয়ালের জায়গায় ছিল কয়েক স্তরের তৈরি বাঁশের বাহারি নকশা ও রঙের বেড়া, যা নিশ্চিতভাবেই টিকত বছরের পর বছর।
চৈত্রের শেষ দিনে বাড়ির বউ-ঝিরা দলবেঁধে ঘরদুয়ার পরিষ্কার করতেন। মাটির দেয়াল ও ভিটে নিকেয়ে দিতেন। দেখলে মনে হতো একেবারে নতুন। বাড়ির সব কাপড়চোপড় কাচার ধুম পড়ে যেত। সাবান ছিল না। কলাগাছের গোড়া ও মূল কেটে শুকিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে রাখা হতো প্রতিটি বাড়িতেই। এটিকে বলা হতো খার। কাপড় পরিষ্কার করে ধোয়ার এর চেয়ে উৎকৃষ্ট তখন আর কিছু ছিল না। কচিৎ কদাচিৎ কাউকে দেখা যেত রিঠার ফেনা দিয়ে কাপড় কাচতে। বিশেষ করে পাঞ্জাবি আর পাজামা। কাপড় ধোয়ার পালা শেষ হলে শুরু হতো নিজেদের মাথা ধোয়ার পালা। সাবান ছিল দু®প্রাপ্য। একধরনের সাদা মাটি দিয়ে মহিলারা চুল ধোয়ার কাজ করতেন। বিত্তশালীরা ব্যবহার করতেন সরষের খৈল।
এ দিকে সকালে বাড়িতে বাড়িতে আয়োজন হতো তিতা-খাওয়ার আয়োজন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই কচি নিমপাতা কাঁচা হলুদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল ঘরে ঘরে। আরো ছিল ছোলা ভাজা, চাল ভাজা খাওয়ার রেওয়াজ। দুপুরে পাড়া বা গ্রামের অধিকাংশ মানুষ পোলো জাল ঠোলা নিয়ে ছুটতেন পাশের নদীর খালে অথবা বিলে। মাছ ধরা হলে সব মাছ একত্র করে পাড়ার সব বাড়িতে পাঠানোর রেওয়াজ ছিল। যেন সবাই একই আনন্দ উৎসবের অংশী হতে পারে। স্থানীয় উপজাতি; বিশেষ করে সাঁওতালরা দলবেঁধে শিকারের জন্য তীর-ধনুক নিয়ে বের হয়ে যেত।
তখন জনবসতির চেয়ে জঙ্গলের পরিমাণ ছিল বেশি। এসব জঙ্গলে বাঘ, শূকর, খরগোশ ও কাঠবিড়ালির কোনো কমতি ছিল না। সাঁওতালরা দিন শেষে যখন সারাদিনের শিকার নিয়ে বাড়ি ফিরত তখন তাদের কাঁধে দেখা যেত মৃত শূকর, খরগোশ কাঠবিড়ালি, বেজি, গুইসাপ এবং বিভিন্ন ধরনের পাখি ঝুলছে।
বিকেলে গ্রামের স্কুল, মাদরাসা বা বাজারের পাশে খোলা মাঠে আয়োজন করা হতো লাঠিখেলা, হাডুডু খেলার প্রতিযোগিতা। আশপাশের গ্রাম থেকে যোগ দিত বিভিন্ন দল। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়াটা ছিল অনেকটাই অলিখিত নিয়ম।
স্থানীয় ছোট-বড় দোকানদার দোকানের পাশে বা পেছনে রঙিন শামিয়ানা টানিয়ে নববর্ষের হালখাতার আয়োজন করত। সারাদিন মাইকে বিভিন্ন ধরনের গান বাজত। বন্ধুবান্ধব পাড়া প্রতিবেশী এবং খদ্দেররা এসে মিষ্টিমুখ করতেন। যাওয়ার সময় আগের বকেয়া পরিশোধ করে যেতেন। যারা খদ্দের নন তারাও যাওয়ার সময় আধুলিটা বা টাকাটা শুভেচ্ছাস্বরূপ দিয়ে যেতেন। দোকানদাররা পুরনো খাতার সাথে সাথে রাখতেন নতুন খাতা লাল রঙের মলাটযুক্ত।
পরদিন পয়লা বৈশাখ। নতুন বছরের শুরু। এ দিন আমরা ছোটরা থাকতাম বাবা-মা অথবা বাড়ির অন্য বড়দের নজরদারিতে। কারণ অন্য কারোর বাড়িতে গিয়ে যেন আমরা কিছু না খাই। এ জন্য এত সতর্কতা। সবার ভেতর একটি অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল যে, এ দিন প্রথম খাবারটা অন্যের ঘরে খেলে সারা বছর অপরের অনুগ্রহী হয়ে থাকতে হবে। তাই এই সতর্কতা। আরো একটি ব্যাপার ছিল লক্ষ করার মতো। আগের দিনের পরিষ্কার করা জামাকাপড় পরা। এ দিন কোনো বাসি খাবার খাওয়ার প্রচলন ছিল না, ছিল না পান্তাভাত, ইলিশভাজি বা শুঁটকি ভর্তা খাওয়ার রেওয়াজ। এ দিন সবাই গরম ভাত-তরকারি ছাড়া অন্য কিছু খাবারের কথা ভাবতেন না। বাড়ির ছোট-বড় সবাই মিলে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে বসে খেতেন। মা-দাদী-চাচীরা পরিবেশন করতেন গরম খাবার। বাসি পান্তা-শুঁটকি ভর্তা ও ইলিশ খাওয়ার রেওয়াজ আমদানি করা নতুন সংস্কৃতি। বিকেলে গ্রামের বাজারে বসত মেলা। কমবেশি সবাই দলবেঁধে মেলায় যেত। মেলার আকর্ষণ ছিল নাগরদোলা এবং বিভিন্ন ধরনের ও রঙের কাগজের ফুল ও বাঁশি।
বাড়তি আকর্ষণ ছিল মাটির পুতুল। মেলায় মিষ্টি বলতে ছিল মোয়া (খইয়ের লাড়ু) মুড়কি (খইয়ের সাথে চিনি বা গুড় দিয়ে প্রস্তুত করা হয়) মুড়ি ও বাতাসা। বাঘ, সিংহ, সাপ, পেঁচার মুখোশ পরে মঙ্গল শোভাযাত্রার অপসংস্কৃতির গ্রামীণ জনপদে তখনো ছিল না এখনো নেই। এটি আমদানি করা চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃতি। গ্রামীণ জনপদে শুধু নয়, বেশির ভাগ জেলা শহরে তখন ছিল না বিদ্যুৎ, ছিল না খাবার সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা। তখন নতুন বছরে ইলিশ খাওয়ার কথা ভাবাটাই ছিল অবান্তর। এটা নববর্ষকে বাণিজ্যিকীকরণ ছাড়া কিছুই নয়। নববর্ষের হাজারো বছরের ঐতিহ্যকে, এ দেশের পালিত, সামাজিক সংস্কৃতিকে অপসংস্কৃতিতে রূপান্তরের এই চেষ্টার ব্যাপারে সবার সচেতন ও সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন।
লেখক : চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ