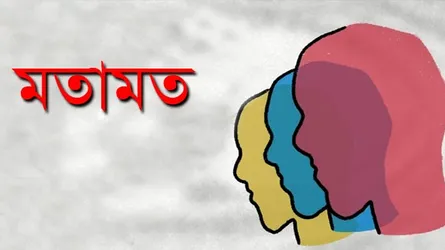সিলেট ভৌগোলিকভাবে একটি অববাহিকা অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় পাহাড় ও আসাম সমভূমি থেকে আসা বহু নদী ও উপ-নদীর মিলনস্থল। এখানে বন্যা নতুন নয়। ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৭, ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালে বড় বন্যা হয়। তবে ২০২২ ও ২০২৪-এর বন্যা ছিল ব্যতিক্রম; ১২২ বছরের ইতিহাসে সিলেট ও সুনামগঞ্জে এমন ভয়াবহ বন্যা হয়নি। সিলেটে বন্যার আশঙ্কা ও ভয়াবহতা এক ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা।
১. বন্যার কারণ
ক. পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টি : এ অঞ্চলে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিশ্বে সর্বোচ্চস্তরের। (চেরাপুঞ্জিতে বার্ষিক গড়ে ১১ হাজার মিলিমিটারের বেশি)। প্রাকৃতিক বন একসময় পাহাড়ি ঢলের গতি রোধ করত, সবুজ বাঁধ হিসেবে কাজ করত। বন উজাড় হয়েছে, মাটির পানি ধারণক্ষমতা কমেছে। ফলে ঢল হচ্ছে তীব্র ও ঘন ঘন। এছাড়া প্রাকৃতিক বাস্তবতাও এখানে সক্রিয়। পাহাড়ি ঢালের ঢাল-কোণ বেশি হলে বৃষ্টির পানি মধ্যাকর্ষণে দ্রুত নেমে আসে। শিলা-গঠনের কারণে পানি মাটিতে শোষিত না হয়ে সরাসরি প্রবাহে পরিণত হয়।
খ. নদী ও খাল ভরাট : সুরমা-কুশিয়ারা, মনু, খোয়াইসহ প্রধান নদী ও উপ-নদীগুলো প্রাকৃতিকভাবে পলি বহন করলেও শিল্পবর্জ্য ও প্লাস্টিকের কারণে এর স্বল্পরিশোধন ক্ষমতা ভেঙে পড়েছে। উজানের মাটি ক্ষয় নদীতে অতিরিক্ত পলি জমা করে। ফলে নদীর গভীরতা কমে যায়। এতে নদীর অঙ্গসংস্থানের (চ্যানেল মরফোলজি) পরিবর্তন ঘটে। পানি অনিয়ন্ত্রিতভাবে নতুন পথে প্রবাহিত হয়। অন্য দিকে নদী-খাল দখলের মাত্রা ভয়ানক। দখলের কারণে নদী ও খাল অপ্রশস্ত হয়ে গেছে। নদী ও খালের পানি ধারণক্ষমতা কমেছে। অতিরিক্ত পানি বহন করতে পারছে না। আর ঢলের জন্য তো প্রস্তুত নয় মোটেও। এই প্রভাব কেবল বর্ষা মৌসুমে সীমিত নয়। শুষ্ক মৌসুমে নৌ-পরিবহন ব্যাহত হয়ে অচল হওয়ার উপক্রম। মাছের প্রজননভূমি ধ্বংস হয়ে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে। কৃষিতেও পড়েছে বিরূপ প্রভাব।
গ. হাওর এলাকার ভৌগোলিক ঝুঁকি : হাওর হলো প্রাকৃতিক নিম্ন অববাহিকা। হাওর বর্ষায় প্লাবিত হয়, মাছ ও কৃষির চক্র পুনর্নবীকরণ করে। কিন্তু হাওরে অবকাঠামো নির্মাণে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাঁধ, রাস্তা ও স্থায়ী কাঠামো হাওরের চরিত্র পাল্টে দিয়েছে। প্রাকৃতিক বন্যাপ্রবাহ ব্যাহত করছে। হাওরের পানিধারণ ক্ষমতা কমছে। অতিবৃষ্টিতে দ্রুত ভরে যাচ্ছে, ঢলে হচ্ছে বন্যা।
ঘ. সীমান্তপারের জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণহীন : সিলেট অঞ্চলের অধিকাংশ নদীর উৎস ভারতে। উজানে বাঁধ ও জলাধার থেকে হঠাৎ পানি ছাড়া হলে ভাটি অঞ্চল মারাত্মকভাবে প্লাবিত হয়। বাঁধে পলি আটকে যাওয়ায় ডেল্টা ক্ষয় হয়। বর্ষায় পানি একত্র হয়ে হঠাৎ নেমে আসছে। বন্যা ও ভাঙন দেখা দিচ্ছে। উজানের দেশ পানিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করায় পানিসংক্রান্ত নিরাপত্তা-সঙ্কট ক্রমবর্ধমান।
ঙ. জলবায়ু পরিবর্তন : গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে গেছে। সিলেটে অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় ও অস্বাভাবিক বর্ষণ বেড়েছে। উষ্ণায়ন বাড়ছে। বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের আধিক্য ঘটছে। স্বল্প সময়ে হচ্ছে অতিবৃষ্টি। সিলেট অধিক বৃষ্টিপ্রবণ স্পর্শকাতর সীমানার শিকার হচ্ছে। মেঘালয়ের উচ্চভূমির পানির ঢল প্রবল তোড়ে প্রবেশ করছে সুনামগঞ্জে, সিলেটে।
২. বহুমুখী প্রভাব
২.১. নদী ও জলপ্রবাহের ওপর প্রভাব
ক. প্রবাহের অস্বাভাবিকতা তৈরি হয়েছে। শুকনো মৌসুমে প্রবাহ হ্রাস হয়।
উজানে বাঁধ থাকায় ফেব্রুয়ারি-মে সময়ে নদীগুলোতে ন্যূনতম প্রবাহ কমে যায়। এতে পানির স্তর কমে, নৌচলাচল ও কৃষি সেচ ব্যাহত হয়। নদীর প্রাকৃতিক পলিপ্রবাহ (sediment load) কমে গিয়ে তলদেশে পরিবর্তন ঘটে। মাছ ও জলজ জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল ধ্বংস হয়।
খ. বর্ষায় হঠাৎ অতিপ্রবাহ (surge flow) ঘটে। তখন হঠাৎ গেট খুলে পানি ছাড়লে একসাথে বিশাল জলধারা নদী ছাপিয়ে জনপদ সয়লাব করে। আকস্মিকভাবে সিলেট শহর তলিয়ে যায়।
গ. নদীর স্বাস্থ্যে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি : পানির ধারা অনিয়মিত হওয়ায় নদীর হাইড্রোলজিক্যাল রিদম ভেঙে পড়ে। প্রাকৃতিক মনসুন-ড্রাই সিজন সাইকেল ভঙ্গ হওয়ায় নদী সিজনাল পালসের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড ভালনারেবিলিটি বা হঠাৎ বন্যা-ঝুঁকিপ্রবণতা এই অঞ্চলের নিয়তিতে পরিণত হয়।
২.২. নিরাপত্তা ও কৌশলগত প্রভাব
ক. পানিকে ভূ-রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার : উজানে পানি আটকে রাখা ও বর্ষা মৌসুমে হঠাৎ ছেড়ে দেয়াকে আমরা বলতে পারি পানির অস্ত্রায়ণ। এতে ভাটির দেশের জীবনযাত্রায় সঙ্কট তৈরি হয়, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক চাপ বাড়ে।
খ. সীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় প্রভাব : বন্যার সময় সীমান্তবর্তী গ্রাম ও চৌকি পানিতে ডুবে গেলে নজরদারি দুর্বল হয়। অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের বাড়তি সুযোগ তৈরি হয়। অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ঘটে এবং সামাজিক চাপ তৈরি হয়। জননিরাপত্তা ও খাদ্যনিরাপত্তা হুমকিতে পড়ে।
গ. দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি : উজান দেশের একতরফা পানি নিয়ন্ত্রণ নিম্নধারার ওপর ক্রমাগত অনিশ্চয়তা চাপিয়ে দেয়। মৌসুমি চরমতার সাথে উজানের কৃত্রিম পানি ব্যবস্থাপনা একত্র হয়ে ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। সর্বোপরি নদীর ভবিষ্যৎ ধ্বংস করা হয়। তলদেশ ভরাট ও প্রবাহ-প্যাটার্নের ভাঙন ভবিষ্যতে স্থায়ী নাব্য সঙ্কট তৈরি করে।
২.৩. কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা সঙ্কট
ক. হাওরাঞ্চল মূলত বোরো ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। বন্যায় অল্প সময়ের মধ্যেই ফসল তলিয়ে যায়। বছরের প্রধান খাদ্য ও আয়ের উৎস ধ্বংস করে দেয়।
খ. স্থানীয় বাজারে ধান ও শাকসবজির সরবরাহ কমে যায়, ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। মৌসুমি বেকারত্ব বাড়ে।
গ. ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বীজ, সার ও শ্রম খরচ মেটাতে ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদে ঋণফাঁদের দিকে ঠেলে দেয়।
২.৪. অবকাঠামো ক্ষয়ক্ষতি
ক. বন্যা ও ঢলে কাঁচা ও আধাপাকা ঘর ভেঙে পড়ে বা অচল হয়ে যায়, যার ফলে হাজারো পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে।
খ. গ্রামীণ সড়ক ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থায় সঙ্কট বাড়ে। জনগণকে দীর্ঘমেয়াদি ধকল সইতে হয়। বন্যাকালে ত্রাণ ও জরুরি সহায়তা পৌঁছানো কঠিন হয়, দুর্যোগ মোকাবেলায় বিলম্ব ঘটে।
গ. স্কুল-মাদরাসা ডুবে যায়, পাঠদান বন্ধ হয়। প্রায়ই এগুলোই আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যাহত হয়।
২.৫. কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়
ক. কৃষি ও নির্মাণ শ্রমিকরা তাৎক্ষণিক আয়ের উৎস হারান। দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকরা বিপদে পড়েন।
খ. দোকান, হাটবাজার ডুবে গেলে ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যায়; পুঁজি হারিয়ে অনেকে আর ব্যবসায় শুরু করতে পারেন না। ছোট ছোট বাণিজ্যিক ও কৃষি উদ্যোগ স্থগিত হয়।
গ. আয়হীনতা ও সম্পদের ক্ষতি নতুন দারিদ্র্য সৃষ্টি করে এবং পুরোনো দারিদ্র্য আরো গভীর করে।
২.৬. স্বাস্থ্যঝুঁকি ও সামাজিক প্রভাব
ক. পানিবাহিত রোগের বিস্তার ঘটে। ডায়রিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, চর্মরোগসহ নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ে; সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের অভাবে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে।
খ. মানসিক স্বাস্থ্যে এর প্রভাব পড়ে। ঘরবাড়ি ও জীবিকা হারানোর ধাক্কা হতাশা, উদ্বেগ ও ট্রমার জন্ম দেয়। যা দিনশেষে জীবন-জীবিকার সঙ্কট বাড়ায়, সামাজিক স্থিতিশীলতায় প্রভাব ফেলে।
গ. সামাজিক অসমতা বাড়ে। ত্রাণ ও সহায়তা তাদের ক্ষতি পোষাতে পারে না। ধনী-দরিদের ব্যবধান সামাজিক অসন্তোষের সৃষ্টি করে।
৪. প্রতিকারের রূপকল্প
৪.১. স্বল্পমেয়াদি (এক থেকে তিন বছর)
ক. দ্রুত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন : কাজের ধরন- শহর ও গ্রামীণ এলাকায় খাল, ড্রেন, ছোট নদী ও জলধারাগুলো পুনর্খনন ও পলিমাটি, আবর্জনা, আগাছা ইত্যাদি অপসারণ। কারণ, পানি দ্রুত বেরিয়ে যেতে না পারলে শহর ও গ্রামে জলাবদ্ধতা বাড়ে, যা বন্যার ক্ষতির মাত্রা বাড়ায়।
খ. অস্থায়ী বাঁধ ও বালুর বস্তা প্রতিরক্ষা : বন্যা মৌসুমের আগেই বালুর বস্তা, বাঁশ ও মাটি দিয়ে অস্থায়ী বাঁধ প্রস্তুত রাখা এবং প্রয়োজনে তা দ্রুত স্থাপন করা। কারণ, পাহাড়ি ঢল বা নদীর পানি হঠাৎ বেড়ে গেলে এই অস্থায়ী বাঁধ প্রাথমিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।
গ. আধুনিক আবহাওয়া সতর্কীকরণ ব্যবস্থা : আধুনিক রেডার, স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করে বৃষ্টিপাত ও পানির স্তর পূর্বাভাস তৈরি, তারপর তা মোবাইল এসএমএস, অ্যাপ, কমিউনিটি রেডিও ও লাউডস্পিকারের মাধ্যমে দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া। সময়মতো সতর্কবার্তা পেলে মানুষ আগাম প্রস্তুতি নিতে পারে, প্রাণহানি ও ক্ষতি কমে।
ঘ. জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র বৃদ্ধি : প্রয়োজনীয় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এবং স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদিকে এমনভাবে প্রস্তুত করা, যাতে বন্যা বা যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সেগুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
৪.২. মধ্যমেয়াদি (চার থেকে সাত বছর)
ক. নদী-খাল পুনর্খনন ও প্রস্থ বৃদ্ধি : সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা- নদী ও খাল খনন (ড্রেজিং), নদীর প্রস্থ বাড়ানো, আবর্জনা ও আগাছা পরিষ্কার করা। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে এই কাজের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিও থাকতে হবে।
খ. সীমানা-পারের পানি ব্যবস্থাপনা চুক্তি : ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কার্যকর ভূমিকা- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নদীর পানি-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যার সময় পানি ছাড়ার নিয়মাবলি নিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন্ন রেখে চুক্তি ও কার্যকর কমিটি গঠন। সহযোগিতা না পেলে আন্তর্জাতিক ফোরামে যেতে হবে। সিলেট অঞ্চলের নদীগুলো ভারত থেকে প্রবাহিত হওয়ায় ভারতের পানি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের বন্যার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। সীমান্ত পারাপার পানি নিয়ন্ত্রণে দ্বিপক্ষীয় সহায়তা ও আন্তর্জাতিক আইনের অনুসরণ না করা হলে বন্যার ধ্বংসযজ্ঞ অনিবার্য।
গ. টেকসই কৃষি ব্যবস্থা : স্বল্পমেয়াদি ফসল, ভাসমান চাষ এবং বন্যা-সহনশীল ধান : দ্রুত ফলনশীল ও স্বল্পমেয়াদি ফসল চাষের প্রচারণা, পানিতে ভাসমান চাষের প্রযুক্তি প্রয়োগ, বন্যা-সহনশীল ধানের উন্নয়ন ও বীজ বিতরণ। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দান।
ঘ. উন্নত বাঁধ ও স্লুইসগেট নির্মাণ : হাওর ও জনবসতি সুরক্ষায় মজবুত কংক্রিট বাঁধ ও নিয়ন্ত্রণ গেট (স্লুইসগেট) নির্মাণ যা পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবে। বাঁধের ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত পরীক্ষা ও মেরামত। হাওর এবং নিম্নাঞ্চলগুলো বন্যার পানি ধরে রাখা বা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে বাঁধ ও স্লুইসগেটের ওপর নির্ভরশীল।
৪.১. দীর্ঘমেয়াদি প্রতিকার ( আট থেকে ২০ বছর)
ক. বন্যা সহনশীল নগর পরিকল্পনা : উঁচু রাস্তা, ভবন ও ড্রেনেজ মাস্টারপ্ল্যান। অবকাঠামো এমনভাবে পরিকল্পনা ও নির্মাণ করা, যাতে বন্যার পানি প্রবাহে বাধা না দেয়। রাস্তা, ভবন ও ড্রেনেজ সিস্টেম উঁচু ও শক্তপোক্ত করা হবে। একটি সামগ্রিক মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হবে, যেখানে পানি নিষ্কাশন হবে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত।
খ. বৈজ্ঞানিক জলাধার ও রিজার্ভার নির্মাণ : বর্ষায় পানি ধরে রেখে শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহার। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য জলাধার ও রিজার্ভার নির্মাণ, যেখানে পানি সঞ্চিত থাকবে। শুষ্ক মৌসুমে সেই পানি কৃষিকাজে ও জনসাধারণের পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হবে।
গ. প্রাকৃতিক জলধারা পুনরুদ্ধার : হাওর-নদী সংযোগ পুনঃস্থাপন ও জলাভূমি সংরক্ষণ। পুরোনো ও প্রাকৃতিক নদী ও জলাধার পুনরুদ্ধার, অবরুদ্ধ জলধারা উন্মুক্তকরণ ও জলাভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া পুনঃস্থাপন।
ঘ. জলবায়ু অভিযোজন নীতি : গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা। পাহাড়ি অঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন ও ভূমি সংরক্ষণ, যা পানি ধারণের ক্ষমতা বাড়ায় এবং ঢলের তীব্রতা কমায়। পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো (গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার) যেমন- বৃষ্টির পানি শোষণযোগ্য পার্ক, জলাধার, বনায়ন ও টেকসই জমি ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ। কারণ, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি ও পরিবেশকে শক্তিশালী করে বন্যার প্রভাব কমানো যায়।
সিলেট অঞ্চলের বন্যাপ্রবণতা প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট কারণেও গুরুতর রূপ নিয়েছে। উজানের দেশ থেকে পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণহীনতা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অবকাঠামো নির্মাণের অনিয়ম এবং দূষণের কারণে বন্যার তীব্রতা ও প্রভাব বাড়ছে। বন্যা শুধু ক্ষণস্থায়ী দুর্যোগ নয়, এটি সিলেটের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি বাধা সৃষ্টি করছে।
ফলে বন্যা মোকাবেলায় কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়; বরং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, আন্তঃদেশীয় সমন্বয়, টেকসই কৃষি, প্রাকৃতিক জলধারা সংরক্ষণ এবং সামাজিক সচেতনতার বিকল্প নেই। একত্রিত উদ্যোগ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সিলেটকে বন্যা-সতর্ক ও টেকসই অঞ্চলে পরিণত করার বিকল্প নেই।
লেখক : কবি, গবেষক
[email protected]