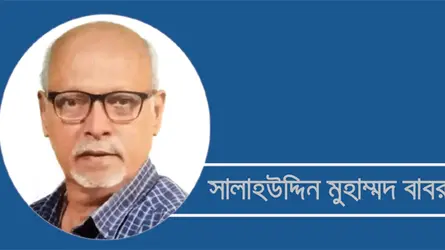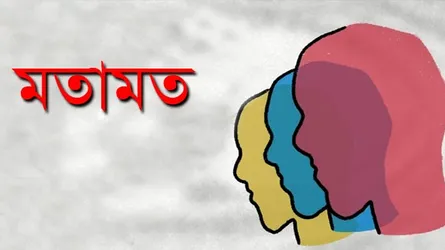বাংলাদেশের মুক্তি তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী সরকার পরিচালিত হলেও মুক্তি তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সব শ্রেণিপেশার মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপ্তিকাল ছিল ৯ মাস। চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বক্ষণে ভারত-পাকিস্তান প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের রণকৌশল ছিল গেরিলাযুদ্ধ। গেরিলাযুদ্ধে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, জনতাসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ মুক্তি সংগ্রামীকে এ দেশের সাধারণ মানুষ আশ্রয়, খাদ্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে হারে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং এর প্রতি সমর্থন জুগিয়েছিল তাতে নির্দ্বিধায় বলা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামটি ছিল সর্বজনীন।
বাংলাদেশের মুক্তি তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে সংগঠিত হলেও তার নামে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন যে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে তার রাষ্ট্রপতি পদে ভূষিত করা হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ থাকাকালীন উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রবাসী সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
বাংলাদেশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের শাসনভার থেকে মুক্ত হলেও ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় প্রত্যাবর্তন অবধি অস্থায়ী সরকার দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তনের পরদিন তিনি রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তার দল আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ হতে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। উভয় পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। এই গণপরিষদকে সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। গণপরিষদ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর হতে সংবিধানটি কার্যকর হয়। অতঃপর উভয় পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত গণপরিষদ ভেঙে দিয়ে জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।
শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে তাকে প্রধানমন্ত্রী করে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ থেকে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এমন সব দলের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এটি আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার ছিল। একটি নবগঠিত রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে দেশ ও সমাজের দলমত নির্বিশেষে সব শ্রেণিপেশার মানুষের সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন। সে মানসে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল এমন সব দলের পক্ষ হতে দাবি উঠেছিল সব দলের সমন্বয়ে জাতীয় সরকার গঠনের। যদিও আওয়ামী লীগ সে সময় জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। কিন্তু ১৯৭৫ সালে যখন বামধারার দু-তিনটি দলকে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে অন্যদের বাকশালে যোগদানের সুযোগ উন্মুক্ত রেখে এটিকে সর্বদলীয় রূপ দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়; তখন ওই সময়কার প্রধান বিরোধী দল জাসদসহ অপরাপর ক্ষুদ্র দল বাকশালে যোগদান না করায় এটিকে কোনোভাবে সর্বদলীয় জাতীয় সরকার বলার অবকাশ নেই।
স্বাধীন বাংলাদেশে গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নকালে দল ও দেশের ওপর শেখ মুজিবুর রহমানের একক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই একক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে শেখ মুজিবুর রহমান সেসময় কিংবদন্তিসম বিরল ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। সে সময় শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা গগণচুম্বী হওয়ায় আওয়ামী লীগের বা অন্যান্য দলের অপর কাউকে তার সমকক্ষ ভাবা দূরের কথা; তার সাথে তুলনার কোনো অবকাশ ছিল না। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে ’৭২ এর সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার যে রূপরেখা দেয়া হয়; তাতে সরকারের শীর্ষ নির্বাহী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে যে ক্ষমতা দেয়া হয় তা বলতে গেলে নিরঙ্কুশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য যেসব গণতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু রয়েছে সেসব দেশের প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় অত্যধিক।
শেখ মুজিবের শাসনামলে বাকশাল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় তাতে সরকারব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতি হতে রাষ্ট্রপতি শাসিত করা হয়। সেই সাথে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ ক্ষমতা দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতা-পরবর্তী অবশিষ্ট সময়সহ বর্তমানে দেশ সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার অধীন পরিচালিত হচ্ছে। ’৭২-এর সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল বর্তমানেও প্রধানমন্ত্রী অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করেন।
আমাদের মন্ত্রিসভার অপরাপর সব সদস্য প্রধানমন্ত্রীর একক সিদ্ধান্তে নিয়োগ লাভ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তারা পদে বহাল থাকেন। আমাদের অন্যান্য বিভাগের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদধারী যেমন রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি বিদেশ সফর বা সাময়িক অসুস্থতাজনিত কারণে স্বীয় কার্য পালনে অপারগ হলে কে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন তা সংবিধানে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বিদেশ সফর বা অসুস্থতাজনিত কারণে প্রধানমন্ত্রী তার কার্য পালনে অপারগ হলে কে তার দায়িত্ব পালন করবেন সে বিষয়ে সংবিধান নিশ্চুপ। এ নিশ্চুপতায় দেখা যায়, বিদেশ অবস্থানের কারণে প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতি দীর্ঘায়িত হলেও কার্যত তার অনুপস্থিতির সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে কেউ না থাকায় একটি শূন্যতা বিরাজ করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এ ধরনের শূন্যতা অনুমোদন করে না। সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু আছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এ ধরনের শূন্যতার স্থান নেই।
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অনুসৃত হয় এমন সব দেশে জনগণ স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করে। একজন সংসদ সদস্যের মূল কাজ সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন প্রণয়ন। কিন্তু আমাদের দেশে আইন প্রণয়নসহ সংসদে যেকোনো বিষয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগে দলীয় সংসদ সদস্যরা স্বাধীন নন। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী, একজন দলীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন পরবর্তী দল হতে পদত্যাগ করলে অথবা সংসদে দলের বিপক্ষে ভোটদান করলে সংসদে তার আসন শূন্য হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী বা একটি দলের দলীয় প্রধানের সাথে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে দলের যেকোনো সংসদ সদস্যের মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ মতভেদে তিনি পদত্যাগ করলে তার আসন শূন্য হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক প্রতীয়মাণ হয়। কথাটি অনস্বীকার্য যে, সংসদ সদস্য হিসেবে একজন ব্যক্তির নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় দলের ভাবমর্যাদা এবং নিজের জনপ্রিয়তা দুইয়ের অবদান থাকে; তবে কোনোটির অবদান বেশি ক্ষেত্রবিশেষে এর ভিন্নতা রয়েছে। একজন সংসদ সদস্যকে সংসদে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোটদানে সংসদে তার আসন শূন্য হওয়া কোনোভাবে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত আছে গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি। একজন সংসদ সদস্যকে সংসদে স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ায় কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাতের শামিল।
সংবিধানের উপরিউক্ত বিধানদ্বয় সংসদ সদস্যদের যে বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাতে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর একক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আরো সুসংহত করেছে।
বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি অভ্যুদ্বয়ের পর আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি এই তিন দল ক্ষমতাসীন ছিল। তিনটি দলের যখন যেটি ক্ষমতাসীন ছিল তখন দেখা গেছে দলীয়প্রধান ও সরকারপ্রধান একই ব্যক্তি। পৃথিবীর অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশে একই ব্যক্তি কখনো দলীয় ও সরকারপ্রধান হয় না। একই ব্যক্তি দলীয় ও সরকারপ্রধান হলে দল ও সরকারবিষয়ক সর্বময় ক্ষমতা এক ব্যক্তির কাছে কেন্দ্রীভূত থাকে। এ কারণে আমাদের দেশে দেখা যায়, দলে পদ, দলের মনোনয়ন লাভ এবং মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তিসহ সব বিষয়ে দলীয় ও সরকারপ্রধানের একক সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। উল্লেখিত তিনটি দলের দলীয় প্রধান দীর্ঘদিন যাবৎ দলের নেতৃত্বে আসীন থাকায় এগুলোর কোনোটিতে এখনো পর্যন্ত পরিবারবহির্ভূত বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। দলে বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর করতে পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এ দু’টি পদের মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই মেয়াদে নির্ধারিত আছে। আমাদের সংবিধানে বিষয়টি অনুপস্থিত থাকায় বড় তিনটি দলে পরিবারবহির্ভূত যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা যথাযথভাবে মূল্যায়িত হতে পারছেন না।
বাংলাদেশে এ যাবৎকাল পর্যন্ত যে কয়টি দল সরকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেছে তাদের একটি অপরটির প্রতি আস্থাশীল নয়। দেশে এ যাবৎকাল ১২টি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আটটি দলীয় সরকারের অধীনে এবং চারটি অন্তর্বর্তী, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক ও সেনাসমর্থিত সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল বিজয়ী হয়েছে। অন্য দিকে অন্তর্বর্তী, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক ও সেনাসমর্থিত সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে নির্বাচনের অব্যবহিত আগের ক্ষমতাসীন সরকার পরাভূত হয়েছে।
আমাদের দেশে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না; বিরোধী দলে থাকাকালীন এই দাবির বিষয়ে অনড় থাকলেও অন্তর্বর্তী, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক ও সেনাসমর্থিত সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতেও বিজিত দল সুষ্ঠুভাবে মেনে তো নেয়নি বরং নির্বাচনে অস্বচ্ছতা ও কারচুপির অভিযোগ তুলেছে। তা ছাড়া ক্ষমতাসীন বিজয়ী দল কখনো বিজিত দল হিসেবে পরাজয় স্বীকার করে বিজয়ী দলের প্রধানকে অভিনন্দন জানায়নি। বিজিত দলের প্রধান পরাজয় স্বীকার করে বিজয়ী দলের প্রধানকে অভিনন্দন জানানো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অংশ। আমাদের বিজিত দলের প্রধানরা তুলনামূলক বিচারে যেসব নির্বাচন নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ হয়েছে সেসব নির্বাচনের ফল মেনে না নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে অভিনন্দন জানানো থেকে বিরত থাকেন। তাতে গণতন্ত্রের প্রতি তাদের আস্থাহীনতা প্রকাশ পায়।
পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের ছায়া মন্ত্রিসভা থাকে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে ছায়া মন্ত্রিসভার দায়িত্বপ্রাপ্তরা নীতিনির্ধারণী বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা ও সমালোচনাপূর্বক গণতন্ত্র বিকশিত করে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সহায়তা করেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা নিজেদের সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবিদার বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও এ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এখনো গঠনমূলক সমালোচনা নির্ধারিত স্থান পায়নি।
আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকায় সরকারের মন্ত্রী পদবহির্ভূত অন্যান্য সাংবিধানিক পদ যেমন সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, চিফ হুইপ, হুইপ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রধান ও সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনার, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারের সচিবসহ বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ ও ঊর্ধ্বতন পদসমূহ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রভৃতিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর আকাক্সক্ষাই মুখ্য। এ কারণে এসব নিয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য প্রাধান্য দেয়ায় জ্যেষ্ঠতা, দক্ষতা, সততা, মেধা, যোগ্যতা উপেক্ষিত হয়।
আমাদের সংবিধান প্রণয়ন পরবর্তী এ যাবৎকাল পর্যন্ত ১৭টি সংশোধনী আনা হয়েছে। এসব সংশোধনী দ্বারা ’৭২-এর সংবিধানের যে মৌলিকত্ব ছিল তা একদিকে বিঘ্নিত হয়েছে আবার ওই সংবিধানের যেসব সীমাবদ্ধতা ছিল তা অতিক্রমের চেষ্টা করা হয়নি।
জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো বিষয়ে গণভোটের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। বাহাত্তরের সংবিধানে গণভোটের বিধান ছিল না। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা গণভোটের বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়। দ্বাদশ সংশোধানী দ্বারা এটিকে সীমিত করা হয়। বিধানটি সন্নিবেশনের কারণে সংবিধানের প্রস্তাবনাসহ আরো কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধন বিষয়ে গণভোটের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। আমাদের দেশে ইতঃপূর্বে তিনবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও তিনটি গণভোটের কোনোটি সংবিধান সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। প্রথম ও দ্বিতীয় গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ওপর জনগণের আস্থা আছে কি-নেই তা জানতে চাওয়া হয়। তৃতীয় গণভোটের মাধ্যমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কর্মরত প্রধান বিচারপতি নির্বাচনকালীন সরকারের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি জনগণের আস্থা আছে কি-নেই তা জানতে চাওয়া হয়। তা ছাড়া ভারতবর্ষ বিভাগের সময় আসামের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেট জেলা পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে কি-হবে না তা গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। সম্প্রতি বিশ্ববাসী অবলোকন করেছে যে, স্কটল্যান্ড যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি-থাকবে না সে বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। যদিও গণভোটে যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না থেকে স্কটল্যান্ডের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল সে সম্ভাবনার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করে সফলতা পায়।
আমাদের সংবিধানে গণভোটবিষয়ক যে বিধান ছিল তা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা রহিত করা হয়। এ রহিতকরণে বর্তমানে সংবিধানের যেসব অনুচ্ছেদ সংশোধন অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো গণভোটের মাধ্যমে সংশোধনের দ্বারও রুদ্ধ হলো। আমাদের সংবিধানে উল্লিখিত গণভোট সংবিধান সংশোধনসংক্রান্ত। জাতীয় প্রয়োজনে যেকোনো বিষয়ে দেশবাসীর সিদ্ধান্ত চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা যদি গণভোটের মাধ্যমে চাওয়া হয় সেক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষয়টি সংবিধান সংশোধনবিষয়ক নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত গণভোটের আয়োজনে সংবিধান কোনো ধরনের অন্তরায় নয়।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি নির্বাচনী এলাকার সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত ঘোষণার ভোটগ্রহণ পদ্ধতিতে জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটে না এমন যুক্তিতে অধুনা পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচনীব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। যেকোনো দেশের সাধারণ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টনের পদ্ধতিকে বলা হয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচনীব্যবস্থা। এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ব্যবস্থা। এর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি থাকতে পারে। তবে পক্ষের যুক্তির কাছে বিপক্ষের যুক্তি খুব দুর্বল।
স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও দেখা যায়, মেয়াদ অবসান বা মেয়াদ অবসান ব্যতীত জাতীয় সংসদ নির্বাচন কোন ধরনের সরকারের অধীনে এবং কি নির্বাচনীব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হবে এ বিষয়ে দেশের রাজনৈতিক দল ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারায় প্রতিটি নির্বাচনের আগমুহূর্তে সমগ্র দেশ অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। নির্বাচনের আগমুহূর্তে এই ধরনের অস্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকলে আমাদের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি ব্যাহত হবে, যা কোনোভাবে কাক্সিক্ষত হতে পারে না। আমাদের নির্বাচনকালীন সরকার, নির্বাচনীব্যবস্থা, প্রধানমন্ত্রীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রোধে কিছু বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দিয়ে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোট আয়োজন, একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই মেয়াদ নির্ধারণ, দলীয় ও সরকারপ্রধান একই ব্যক্তি না হওয়া, দল থেকে পদত্যাগ ও সংসদে দলের বিপক্ষে ভোটদান করলে সংসদে আসন শূন্য না হওয়া, ঊর্ধ্বতন পদগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর একক আকাঙ্ক্ষায় নিয়োগ না হওয়া, প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মন্ত্রিসভার পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তির দায়িত্ব পালন প্রভৃতি বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে হলে দলীয় সরকার দ্বারা তা কখনো সম্ভব নয়। এ কারণে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর যে জাতীয় সরকার গঠন অত্যাবশ্যক ছিল তখন তা না হওয়ায় আমরা দেশ ও জাতি হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলীয় সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দ্বিধাবিভক্ত। এ দ্বিধাবিভক্তি হতে উত্তরণে সংলাপের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক দলসহ ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এ সরকারের কাজ হবে সংবিধানের সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করে একটি যুগোপযোগী সংবিধান প্রণয়ন, যা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষাসহ প্রধানমন্ত্রী নামক প্রতিষ্ঠানটির নিরঙ্কুশ ক্ষমতার হ্রাস ঘটিয়ে নির্বাচনকালীন সরকার ও নির্বাচনীব্যবস্থা বিষয়ে স্থায়ী পদ্ধতি সুনিশ্চিত করবে।
লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক
E-mail: [email protected]