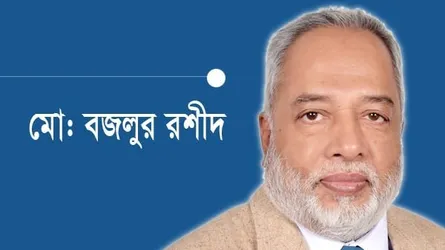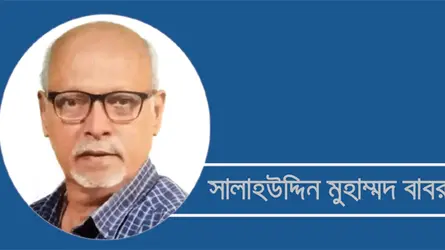দুর্বৃত্তায়নের গোলকধাঁধায় পড়ে গেছে আমাদের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি। ছেলেবেলায় আমরা জাদু দেখতাম। ধারালো ছুরি দিয়ে আস্ত একজনকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো, আবার জোড়া লাগানো হতো। আরো দেখতাম, কত সহজে একজনকে শূন্যে ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব ছিল জাদুবিদ্যা। আমরা শুধু ধাঁধায় পড়ে যেতাম। আমাদের বর্তমান রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি দুর্বৃত্তায়নের এমন এক গোলকধাঁধায় পড়ে গেছে যে, কেউ বুঝতে পারছি না, কোথা থেকে কী হচ্ছে।
দেশ ও দশের চিন্তায় যেসব ব্যক্তির পেরেশান হওয়ার কথা ছিল; তারা আজ স্থূলকায়। অর্থবিত্তে, গায়ে গতরে স্ফীত। এক বছর আগেও যারা রিকশাভাড়া দিতে পারতেন না, আজ তাদের বাহন পাজেরো কিংবা হেলিকপ্টার। কৈফিয়ত কি আছে! এখানে কী ধরনের দুর্বৃত্তায়ন কাজ করছে? যুগে যুগে সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তনের যে আশা নিয়ে আন্দোলন, বিপ্লব হয়েছে তার পরিবর্তন কি আদৌ হয়েছে? সামগ্রিক অর্থে পরিবর্তন এখনো দৃশ্যমান নয়। মাঝখানে শ্রেণিবৈষম্য বাড়ছে বৈ কমছে না। একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অর্থ-বিত্তে আরো স্ফীতি হয়ে রীতিমতো দৈত্যকায় হয়ে উঠছে।
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর গণমানুষের মনে বিপুল আশার সঞ্চার হয়েছিল। মানুষ ভাবতে শুরু করেছিলেন একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে; কিন্তু দিন শেষে দেখা যাচ্ছে সবাই ক্ষমতা পেতে মরিয়া। দুর্নীতি, দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি আর আমলাকেন্দ্রিক জটিলতা আগের মতো রয়ে গেছে। কোনো পরিবর্তন বা হেরফের হয়নি।
বিশ্বের যেসব দেশে স্বৈরশাসক দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকেন সেসব দেশ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়ে। ওই সব দেশে স্বৈরশাসকের পতনের পর রাষ্ট্র বিনির্মাণে সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া বেশ জটিল হয়ে পড়ে। এখানে বহু মত-পথ সামনে এসে দাঁড়ায়। যারা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তারা, যারা রাজনৈতিকভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করেন তারা এবং সমাজের সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর মতামত সামনে আসে নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী। কেবল অবহেলিত থেকে যায় বৃহৎ জনগোষ্ঠী।
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে বাংলাদেশ থেকে ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের পতনের পর এ দেশের জনগণের জন্য যে স্বপ্নের দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছিল, তা ফের রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে, বাংলার মানুষ আন্দোলন করে সাধারণত ব্যর্থ হয়, কখনো কখনো সফল হয় এবং সফল হওয়ার পর মনে থাকে না কেন তারা আন্দোলন করেছিল।
আমাদের জাতীয় পর্যায়ে এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে দুর্বৃত্তায়ন বাসা বাঁধেনি। যে যত বড় মাপের দুর্বৃত্ত, সে তত বড় ক্ষমতাধর। এই শ্রেণীই সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ভালো মানুষের কদর দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারের কাজে তাদের খুব কম সুযোগ দেয়া হয়। বিপরীতে যারা সমাজে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, ভয় দেখিয়ে নিজস্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে; তারা সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারের হর্তাকর্তা বনে যায়। যার কারণে এ সমাজ দুর্বৃত্তায়নের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। কিন্তু এ থেকে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার বড় প্রয়োজন। যারা স্বচ্ছ ও আদর্শিক রাজনীতি করেন, দেশ-দশের কথা চিন্তা করে রাজনৈতিক অঙ্গীকার করেন, তাদের পক্ষে রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কার অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হতে পারে। তবে সে পথ খুব কঠিন, জটিল ও বন্ধুর। কারণ যে দুর্বৃত্তায়ন সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে তা সংস্কারের পথ রোধ করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।
গত শতকের শেষভাগ থেকে এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিশেষ করে শেষ হাসিনার ফ্যাসিবাদী জমানায় দুর্বৃত্তায়নের গোলকধাঁধায় হোঁচট খাচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক-ব্যবস্থাপনা। ব্যক্তিজীবন থেকে জনজীবন- সব জায়গা স্বার্থবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। তাদের ভয়ঙ্কর ছোবলে সব খাত তছনছ। তাই পরিবর্তনে প্রয়োজন স্বচ্ছ রাজনীতি ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের দুঃশাসনে তা ছিল জনমানুষের জন্য দুঃস্বপ্ন। এমন একটি ভীতিকর পরিস্থিতি থেকে রাষ্ট্রকে যখন বের করে আনা হয়েছে তারপর আজকে ঐক্যের জায়গায় পৌঁছাতে বেগ পেতে হচ্ছে। সংস্কারের জটিল সমীকরণ যেন ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য ডেকে আনছে। গোলকধাঁধায় পড়ে গেছে নির্বাচনের তারিখ। নির্বাচন প্রচলিত নিয়মে নাকি পিআর (প্রোপশনাল রিপ্রেজেনটেশন) পদ্ধতিতে হবে, তা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একধরনের বিভেদ তৈরি করে দিচ্ছে।
আজকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, গণতন্ত্রের নামে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চা বিসর্জন দিয়ে জনগণকে অহসায় করে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়; বরং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন দেশের উন্নয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে তৈরি হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। এতে করে রাজনীতির মাঠে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দুর্নীতিবাজরা।
সঙ্কটের কেন্দ্রবিন্দুতে নির্বাচন; কিন্তু শুধু নির্বাচন সঙ্কটের সমাধান দিতে পারবে না। এ জন্য রাজনৈতিক অঙ্গনে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারে কিছু মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য অর্জন অপরিহার্য। আমাদের নতুন বাস্তবতায় এখনো নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত নিয়মে হওয়া উচিত বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রয়েছে। কারণ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে বিপুল রক্তের বিনিময়ে যে ফ্যাসিবাদ বিদায় নিয়েছে তা আবার ফিরে আসার শঙ্কা আছে। পিআর পদ্ধতিতে ছোট ছোট দলের হয়তো সুবিধা হবে; কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে তা নির্বাচনী সঙ্কট দূর করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে এ কথাও সত্যি যে, দেশে এখন যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা নির্ধারিত রয়েছে, তা কমিয়ে আনা একান্তভাবে দরকার। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারণ করতে হবে। দুই মেয়াদের বেশি এক ব্যক্তি সরকারপ্রধান হতে পারবেন না, এটি সত্যিকার অর্থে কার্যকর করতে হবে।
গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পার্লামেন্টের ভূমিকা শক্তিশালী করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা কার্যকর করতে হবে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধনীসহ রাজনৈতিক দলে গণতান্ত্রিক চর্চা বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে হবে। সংসদের বাইরেও বিরোধী দলগুলো যেন সঠিক অর্থে গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখতে পারে, তার জন্য রাজনৈতিক পথ প্রশস্ত রাখতে হবে। তবে অযৌক্তি হরতাল-অবরোধের নামে জনগণের জান-মালের যেন ক্ষতি না হয় তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। সর্বোপরি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ব্যাহত করে এমন কোনো কর্মসূচি যেন আমাদের রাজনীতিকে কলুষিত করতে না পারে, সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য থাকতে হবে।
আজকে যে কারণে এ দেশের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষমতার দুর্বৃত্তায়নের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে, তার মূলে রয়েছে, ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু দুর্নীতি-অপব্যবহারে অবৈধ সম্পদ উপার্জনের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি, যা রীতিমতো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। এখন রাষ্ট্রকে মেরামত করতে হলে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের চাইতে বরং বেশি প্রয়োজন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দুর্নীতি নির্মূল করা। শুধু তাই নয়- প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচারব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান দলীয় প্রভাব মুক্ত রাখা। রাষ্ট্র মেরামতের মূলে রাখতে হবে গণতন্ত্র ও জনস্বার্থ।
ফ্যাসিবাদ-পরবর্তী দেশের মানুষের মন থেকে কর্তৃত্ববাদের আতঙ্ক দূর করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সদিচ্ছা থাকলে তা অসম্ভব নয়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার দৃঢ় সঙ্কল্প এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধারণ করে জাতীয় স্বার্থ ও জনপ্রত্যাশা সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারার মানসিকতা হতে পারে সব সমস্যার বড় সমাধান এবং সব সংস্কারের বড় সংস্কার।
লেখক : কলামিস্ট ও রাজনীতিক