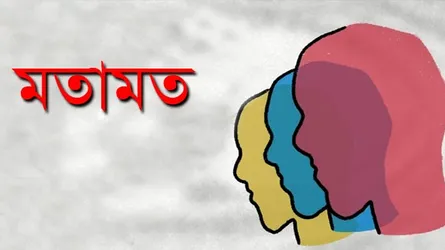ফিরোজ আলম
সারা বিশ্বে শিক্ষকতাকে সম্মান দেয়া হলেও আমাদের দেশে এ পেশার যথাযথ মূল্যায়ন অনুপস্থিত। ফলে চাকরিতে যুক্ত হয়ে তারা সীমাহীন অপ্রাপ্তি আর অবহেলা দেখে যৌক্তিক দাবি নিয়ে বছরের বেশির ভাগ সময় অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে রাজপথে ব্যস্ত থাকেন। এতে করে আগের চেয়ে দ্বিগুণ শিক্ষক নিয়োগ হওয়ার পরও শিক্ষার গুণগত মান এখন তলানিতে। শিক্ষকরা বাড়িভাড়া, চিকিৎসাভাতা বাড়ানো ও জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন করেছেন বিশ বছরের বেশি সময় ধরে। আর কত দিন তারা যৌক্তিক দাবি চাওয়া থেকে নীরব থাকবেন। সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্তাব্যক্তিদের সাথে সাথে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। শতাংশ হারে বাড়িভাড়ার দাবি উপেক্ষা করে বিশ্ব শিক্ষক দিবসে ৫০০ টাকার বাড়িভাড়া ঘোষণা করে শিক্ষকতা পেশাকে আরো মর্যাদাহীন করার চেষ্টা করা হয়।
সরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিংবা স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষকরা ৪৫ শতাংশ বাড়িভাড়া পাওয়ার পরও দাবি-দাওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ২০২২ সালের সর্বশেষ প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫১ শতাংশ বাংলায় ও ৩৯ শতাংশ গণিতে শ্রেণী বিবেচনায় প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করেছে। বাকিরা ব্যর্থ হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর বেলায় বাংলায় এ হার ৫০ ও গণিতে ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাতৃভাষা বাংলায় অর্ধেক শিক্ষার্থী দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। তাই এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, শিক্ষকরা যদি ৪৫ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া পেতে পারেন, তাহলে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা তা না পেয়ে কিভাবে ক্লাসে মনোযোগী হবেন।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা অন্তত দুই হাজার বা তিন হাজার টাকা কিংবা শতাংশ হারে করার প্রস্তাব অর্থ বিভাগে পাঠানো হয়েছে। হয়তো আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রজ্ঞাপন হতে পারে। শিক্ষকরা চান শতাংশে, মোড়লেরা চান এককালীন। তারা শিক্ষা-শিক্ষকদের বুঝতে চান না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলন অনুযায়ী, বাড়িভাড়া ২০ শতাংশ বা ন্যূনতম তিন হাজার টাকা করা হলে সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (মাউশি, মাদরাসা বিভাগ ও কারিগরি বিভাগ আওতাধীন) মিলে বছরে ব্যয় হবে ২২৬৭ কোটি ২৪ লাখ টাকা, কোন অঙ্গে এটি রাষ্ট্রের জন্য বোঝা; তা বোঝা সত্যি মুশকিল। দেশে দারিদ্র্যের হার ২০২৩-২৪-তে বেড়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দারিদ্র্যের হার অধিক হারে বেড়েছে। শিক্ষকদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ৬০ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে যাবে।
সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের তথ্যমতে, শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মানের দিক থেকে বাংলাদেশ অন্তত ৪ দশমিক ৫ বছর পিছিয়ে। দেশের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মান আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সপ্তম শ্রেণীর সমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) একজন স্নাতকের সনদ সিঙ্গাপুরে ফাউন্ডেশন কোর্সের সমমান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত স্নাতক সনদকে ‘ডিপ্লোমা’ ও বাংলাদেশের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে স্নাতক মানের ধরা হচ্ছে সিঙ্গাপুরে। একই সংস্থার তথ্যমতে, শিক্ষা মান হারিয়ে শিক্ষিত বেকার তৈরি করছে।
পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে যত বেকার, এর ১৩ শতাংশ স্নাতক। ৭ দশমিক ১৩ শতাংশ বেকার উচ্চমাধ্যমিক পাস। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জনে পাঁচজন বেকার। শিক্ষক সুবিধা নিশ্চিত না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা তৈরি হচ্ছে না। ২০২২ সালের বৈশ্বিক সৃজনশীল ইনডেক্সে ১৩৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সূচকেও পিছিয়ে আমরা। ২০২২ সালে ইউএনডিপি এবং মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম নলেজ ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বৈশ্বিক জ্ঞান সূচকে ১৫৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২০তম। জাতিসঙ্ঘের সংস্থা ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অরগানাইজেশনের ২০২১ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে ১৩২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৬ নম্বরে। উদ্ভাবন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় সবার নিচে আছে বাংলাদেশ। মেডিক্যাল শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিক্যাল এডুকেশনের (ওয়ার্ল্ডের তথ্যমতে, বাংলাদেশে এমবিবিএস ডাক্তারের বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা অনেক কমেছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডস (কিউএস) প্রকাশিত ২০২৫ সালের বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংকিং অনুযায়ী, বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান স্থান পায়নি।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন ‘ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাংকিং ২০২৫’-এ সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। যা শিক্ষার গুণগত দুর্বলতার বড় প্রমাণ। ২০২২ সালের বিবিএসের হিসাবে, দেশে অতিদারিদ্র্য ছিল ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, তা ২০২৫ সালে বেড়ে হয়েছে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ। মানে, এমপিওভুক্ত নতুন যোগদানকারী শিক্ষকরা অতিদারিদ্র্য শ্রেণীর বেতন নিয়ে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দিচ্ছেন। এছাড়া সাধারণ দারিদ্র্য হার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশে। মানে প্রভাষক- সহকারী অধ্যাপকরা সাধারণ দারিদ্র্য শ্রেণীর বেতন কাঠামোয় অবস্থান করছেন।
নি¤œবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের মাসিক আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় তাদের ধারদেনা করে সংসার চালাতে হয়। একটি পরিবারের খাবার কিনতে ব্যয় হয় মোট আয়ের ৫৫ শতাংশ। পরিবারে আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে সবচেয়ে বেশি চিকিৎসাব্যয় ৬৭ দশমিক ৪ শতাংশ। ঋণ পরিশোধে যায় ২৭ শতাংশ। ২০২৫ সালের স¤প্রতি দলমত নির্বিশেষে হাজারো শিক্ষক ন্যূনতম দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে দাঁড়িয়েছেন রাস্তায়। রাস্তা না আটকে কেউ যদি অন্য কোনো উপায়ে ন্যায্য দাবি জানান, তাহলে সরকার গুরুত্ব দিতে চায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাস্তা আটকালে ফল আসে, সরকার গুরুত্ব দেয়। গত এক বছরের পরিসংখ্যান তাই বলছে। গত এক বছর বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৫৪ বার সড়ক আটকানো হয়েছে। এর মধ্যে ২৬ বার ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ছিল ১৩টি।
চাকরিসংক্রান্ত দাবিতে রাস্তা আটকানো হয়েছে ৬ বার। বাকি ৯ বার অন্যান্য কারণে রাস্তা আটকানো হয়েছে। প্রতিবারে আন্দোলনকারীরা সফল। তাহলে শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান কোথায়? রাস্তার আন্দোলনে, সচিবালয়ের টেবিলে নাকি রাজনৈতিক সমাধানে, তা এখন ভাবনার বিষয়।
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি থেকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করলেও এখনো সাড়ে ৮ শতাংশের উপরে, যা অতি উচ্চ বলা যায়। দিশেহারা শিক্ষকরা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো- শিক্ষাসংশ্লিষ্ট দফতরে যারা দায়িত্বে আছেন, তাদের কাছে সমস্যা সমাধানের জ্ঞান নেই, শিক্ষকদের সম্মান করার কর্মী নেই এবং শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সেই সাহসও নেই। এদের দিয়ে রাষ্ট্র চলতে পারে না, পারবে না। বিশ্বব্যাংক ও এআরআই গবেষণা ইনস্টিটিউটের হিসাবে, রাস্তা অবরোধ ও যানজটে ঢাকায় দৈনিক ৮২ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়, যার আর্থিক মূল্য তখন (২০২২) ছিল ১৩৯ কোটি টাকা। সেই হিসেবে, শিক্ষকরা তিন দিন পথ আটকালে দেশের ক্ষতি ৪০০ কোটি টাকারও বেশি। অথচ শিক্ষকদের বাসাভাড়া সমস্যা সমাধানে এ টাকা হলে ৪০ শতাংশ হাউজ রেন্ট দেয়া সম্ভব।
বাংলাদেশের সংবিধানের কোনো সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে সরকারি, আধা-সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩ অনুযায়ী, এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র মালিকানার তিনটি রূপের তৃতীয় ধাপ, মানে- ব্যক্তিগত মালিকানা (ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মালিকানা)। অথচ জাতীয়করণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া; যেখানে একটি রাষ্ট্র বা সরকার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোনো সংস্থা, শিল্প বা সম্পদকে রাষ্ট্রের পাবলিক মালিকানার অধীনে নিয়ে আসে। সংবিধানের ৯৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি জাতীয় স্বার্থে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করার ক্ষমতা রাখেন। সংবিধানের মৌলিক চাহিদা পূরণ (অনুচ্ছেদ ১৫), সামাজিক ন্যায়বিচার (অনুচ্ছেদ ১৯) এবং শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব (অনুচ্ছেদ ১৮) জাতীয়করণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি।
বাংলাদেশের সংবিধান সরাসরি ‘জাতীয়করণ’ শব্দটির উল্লেখ না করলেও, সংবিধানের কিছু মূলনীতি ও ধারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয়করণ প্রক্রিয়া সমর্থন করে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা (অনুচ্ছেদ ১৩, ১৭, ১৯) অর্জনের জন্য। সরকার যখন কোনো শিল্প বা প্রতিষ্ঠানকে ‘জনস্বার্থে’ জাতীয়করণ করে, তখন তা সংবিধানের এ নীতিগুলো বাস্তবায়নের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। অনুচ্ছেদ ১৭ (শিক্ষার জাতীয়করণ) ধারায় শিক্ষার জাতীয়করণ ও বৈষম্যহীন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে সরকার চাইলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণের মাধ্যমে একটি সুশিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে পারে। অনুচ্ছেদ ১৯ (সুযোগের সমতা) অনুযায়ী, সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব। জাতীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা যায়।
তাই বলি, শিক্ষার দুর্বলতা কাটাতে, হারিয়ে যাওয়া মান ফেরাতে, সৃজনশীলতা বাড়াতে শিক্ষকদের যৌক্তিক বাড়িভাড়ার দাবি, সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণসহ অন্যান্য দাবি পূরণ করে শিক্ষকদের ক্লাসরুম থেকে রাস্তায় সংগ্রাম করার রীতিকে চিরতরে বিদায় করুন। তা না হলে মেধাবী শিক্ষকদের পাশাপাশি মেধাবী ছাত্র ও আগামীর দেশ গঠনপ্রক্রিয়া কালের গর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
লেখক : মহাসচিব, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ মাদরাসা জেনারেল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমজিটিএ)