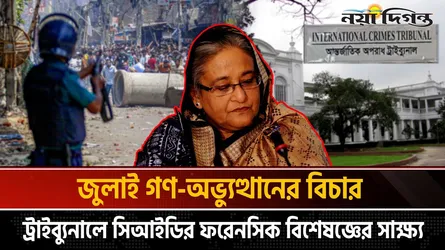স্বাধীন সুলতানি আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে ইতিহাসচর্চার বিকাশ এবং জোয়ার তৈরি হয়। এতে পথ দেখান কিছু বলীয়ান ঐতিহাসিক। তাদের অন্যতম জিয়াউদ্দিন বারানি (১২৮৫-১৩৫৭)। ভারতীয় মুসলিম প্রাথমিক ইতিহাসচর্চায় তিনি আলাদা। কারণ তিনি তখনকার ইতিহাসচর্চার ধারা থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন আঙ্গিকের প্রচলন করেন। গোটা উপমহাদেশে শাস্ত্রীয় ইতিহাসচর্চার পথ নির্মাণে জিয়াউদ্দিন বারানির অবদান অনস্বীকার্য। তার ইতিহাসকর্মে তৎকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।
তিনি শুধু ঘটনার বিবরণ দিয়ে থেমে যাননি; বরং রাষ্ট্রচিন্তা, নৈতিকতা এবং ধর্মীয় আদর্শের সমন্বয়ে একটি দার্শনিক ইতিহাসচর্চার ভিত্তি স্থাপন করেন। ইতিহাসশাস্ত্রে তার প্রধান গ্রন্থÑ তারিখে ফিরোজশাহী। যা ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসচর্চার নতুন পথ নির্মাণ করে। এতে তিনি ইতিহাসতত্ত্বে নিজস্ব বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গির বয়ান করেন এবং প্রতিফলন ঘটান। প্রফেসর আবদুল করিমের (১৯২৮-২০০৭) ভাষায় ‘এ গ্রন্থে আমরা সামাজিক অগ্রগতি ও ভূ-সম্পত্তিগত বিষয়াবলির বিবরণ পাই। আধুনিক পণ্ডিতবর্গ বারানির ইতিহাসকে একটা নিশ্চিত বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন। এটি হলো সামাজিক রীতি-নীতির বিজ্ঞান যার ভিত্তি হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা।’
১. বাস্তবমুখী ইতিহাসচর্চা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা
জিয়াউদ্দিন বারানির ইতিহাসতত্ত্ব তার রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও সামাজিক অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্মিত এক বাস্তবভিত্তিক বয়ান। তত্ত্ব নয়, বাস্তবতা তার ইতিহাসের মূল উপাদান। ১২৮৫ সালের একটি রাজনৈতিক মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। তার বাবা, চাচা ও দাদা; সবাই দিল্লির সালতানাতের বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তার নানা হুসামউদ্দিন ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা এবং তারা বাবা মুয়াউয়িদ উল মুলক ছিলেন জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজির ছেলে আরকালি খানের নায়েব। আলাউদ্দিন খিলজির শাসনামলে তার চাচা কাজি আলাউল মুলক ছিলেন দিল্লির কোতোয়াল বা পুলিশ প্রধান। বারানি নিজে ছিলেন দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজসভায় বিশেষ উলামার একজন। এখানে তার দীর্ঘ ১৭ বছরের উপস্থিতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে তিনি একজন পর্যবেক্ষক ও চিন্তক হিসেবে ছিলেন সজাগ ও নিবিড় দৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি যেসব ঘটনা, নীতি বা বিপর্যয়ের বিবরণ দেন, তার অধিকাংশই নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন বা প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে যাচাই করে লিপিবদ্ধ করেছেন।
বারানির ইতিহাসচর্চা তৎকালীন রোমান্টিক ও অলৌকিক প্রবণতাসম্পন্ন মুসলিম ইতিহাসবিদদের ধারার বিপরীতে অবস্থান করে। বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা কাহিনী চিত্র ও অলৌকিকতার আতিশয্য দেখতে পাই, যেখানে রাজাদের প্রশংসা অনেক সময় অতিরঞ্জিত। বারানি এই প্রবণতা থেকে সরে এসে ক্ষমতার রাজনীতি, সামাজিক বিভাজন, উলামা ও অমাত্যের দ্বন্দ্ব এবং কৃষক ও সৈন্যদের দুঃখ-কষ্টের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেন। এভাবে তিনি ইতিহাসকে গৌরবগাথা থেকে টেনে এনে এক প্রজ্ঞাবান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নীতিবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।
তিনি ইতিহাসকে কেবল ‘সঙ্ঘটনের বিবরণ’ হিসেবে দেখেননি; বরং তার দৃষ্টিতে ইতিহাস ছিল একটি নীতিনির্দেশক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক শাস্ত্র, যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ শাসক ও প্রজারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। তার রচনার মধ্যে বারবার একটি সতর্ক বোধ কাজ করে ‘রাজনীতি কেবল ন্যায়ের ওপর দাঁড়ানো উচিত নয়, তাকে বাস্তবতার কাঁটাতারেও হাঁটতে হয়।’ ফলে আমরা দেখি, তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, ধর্মের অপব্যবহার ও দরবারি চাটুকারিতার বিপদগুলো উল্লেখ করেন।
এভাবে বারানি আমাদের ইতিহাসের এক ব্যতিক্রমধর্মী ধারা উপস্থাপন করেন, যেখানে ক. ইতিহাস কেবল অতীতকে নয়, বর্তমানকে ব্যাখ্যা করে। খ. ভবিষ্যতের জন্য রাজনৈতিক ও নৈতিক দিকনির্দেশ প্রদান করে। গ. বাস্তবতা তার কাছে কেবল উপাদান নয়; বরং তা-ই তার ইতিহাসচর্চার নৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি।
২. ইতিহাসের উপযোগিতা : বারানির দৃষ্টিতে ইতিহাস হলো নৈতিক রাজনীতি ও আদর্শ রাষ্ট্রচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তিনি মনে করতেন, ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য হলো : ক. শাসকদের জন্য শিক্ষা : পূর্ববর্তী রাজাদের ন্যায়-অন্যায়, সাফল্য-ব্যর্থতা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের শাসকরা শিক্ষা গ্রহণ করবে। খ. রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ : ইতিহাস রাষ্ট্রনীতি গঠনের জন্য নৈতিক ও ব্যবহারিক উপকরণ সরবরাহ করে। যেমন কোন নীতি সমাজে স্থিতি আনে আর কোনটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তা ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণযোগ্য। গ. জনসাধারণের চেতনার জাগরণ : ইতিহাস সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সচেতনতা তৈরি করে। ঘ. নীতিশিক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক নির্মাণ : তিনি ইতিহাসকে আত্মশুদ্ধির একটি মাধ্যম মনে করতেন, যেখানে রাজা, উলামা, দরবারি, সৈন্য সবার জন্য রয়েছে শিক্ষা ও সতর্কবার্তা।
বারানির ইতিহাসচর্চা তাই কেবল ‘কি ঘটেছিল’ তা বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ‘কেন ঘটেছিল’ এবং ‘এর থেকে আমাদের কী শেখা উচিত’-এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে।
৩. ধর্মীয় চেতনার উপস্থাপন : বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর ইতিহাস লিখলেও বারানির ইতিহাসতত্ত্ব ইসলামী দর্শন ও সমাজ বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতিপালিত। তার মধ্যে ছিল প্রগাঢ় ধর্মীয় নৈতিকতা, যার ভিত্তিতে তিনি ইতিহাসকে অবলোকন করেন। এতে কয়েকটি ধাপ প্রতিফলিত হয় : ক. ইতিহাসের ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ : তিনি মনে করতেন, ইতিহাস আল্লøাহর কুদরত ও হিকমতের প্রকাশ। মানুষ যখন ধর্মীয় পথচ্যুতি ঘটায়, তখন তা রাজনৈতিক পতনের রূপে প্রকাশ পায়। ইতিহাস তাই ঈমান ও আমলের ফলাফলের বাস্তব দলিল। খ. হেদায়েত বা খোদার নির্দেশনার শ্রেষ্ঠত্ব : তার দৃষ্টিতে শাসক ও রাষ্ট্র উভয়ের উচিত হেদায়েতের অনুসরণ। হেদায়েতের একটি ক্ষেত্র ফিতরাত বা সহজাত ন্যাচার আর প্রধান ক্ষেত্র ধর্মীয় নীতিমালা। রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে তা দুর্নীতির দিকে ধাবিত হয়। তিনি এই বিশ্বাস থেকেই ‘ফতওয়া-ই-জাহানদারি’ গ্রন্থে রাজনীতিতে শরিয়াহর প্রাধান্য দাবি করেন। গ. উলামার ভূমিকা : ইতিহাসে উলামার অবনতি এবং চাটুকার আলেমদের উপস্থিতি তাকে বিচলিত করে। তিনি চান একটি ন্যায়ভিত্তিক ধর্মীয় নেতৃত্ব, যা শাসকদের আল্লাহভীতির পথে পরিচালিত করবে।
৩. ধর্ম ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক : বারানির দৃষ্টিতে ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পরের পরিপূরক, দ্বান্দ্বিক নয়। তিনি রাজনীতিকে এমন একটি ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছেন, যেখানে ধর্মীয় নীতিমালা কার্যকরভাবে প্রয়োগ পায়। তার মতে, রাজনীতি যদি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তবে তা নৈতিক পতনের পথে নিয়ে যায়। বারানির মূল উদ্বেগ হলো, ধর্মহীন রাষ্ট্র কখনো ন্যায়ভিত্তিক হতে পারে না। রাষ্ট্র বা রাজনীতি যদি হেদায়েত ও ইনসাফের অনুসরণ না করে, তবে সেখানে অন্যায়, দমন-পীড়ন ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।
বারানির ইতিহাসচর্চার একটি বিশেষ দিক হলো বার্তা প্রদান। তিনি যেসব বার্তা দিতেন, তার অন্যতম হলো : রাজনীতি নীতিবোধের দ্বারা চালিত না হলে তা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।
এখানে ইতিহাসচর্চা হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আমরা ধর্মীয় নীতিমালার আলোকে রাষ্ট্রশাসনের শিক্ষা গ্রহণ করি। বারানির দৃষ্টিতে ইতিহাস কেবল অতীত নয়; বরং নৈতিক পথনির্দেশ।
বারানির চিন্তা ভারতের মুসলিম ইতিহাসচর্চায় একটি নতুন ধারা সুস্পষ্ট করে। এই ধারা মূলত মাসলাহা বা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কল্যাণের বোধে রাজনীতির আদর্শ নির্মাণ। তিনি অতীত ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করেন। বিশ্লেষণে তিনি কিছু প্রশ্নের জবাব তালাশ করেন। যেমন ক. কোন রাজা হেদায়েতের পথে ছিলেন? খ. কার রাজনীতি বিদয়াতি বা খেয়াল-খুশির উদ্ভাবন দ্বারা পরিচালিত ছিল? গ. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের কল্যাণে কাকে অনুসরণ করা উচিত?
বারানি দেখান, ধর্ম ইতিহাসের ব্যাখ্যা দেয় এবং ইতিহাস ধর্মের কর্মফল প্রকাশ করে। ইতিহাস তাই আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক উভয় বিবেচনার ধারক।
৪. রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি : বারানির দৃষ্টিতে রাজা হচ্ছেন একাধারে রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তিনি শুধু আইন প্রয়োগকারী নন; বরং জনগণের ওপর আল্লাহর খলিফা-স্বরূপ। তাই তার দায়িত্ব ধর্মীয় নীতিমালা অনুসারে রাষ্ট্র চালানো।
‘রাজনীতি যদি নীতিবোধ দ্বারা চালিত না করা হয়, তবে তা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।’ এই বাক্যটি বারানির রাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রে হেদায়েত ও নৈতিকতা থাকা উচিত এই মতের প্রতিফলন। তার দৃষ্টিতে, রাষ্ট্রনীতি মানে হচ্ছে ক. হেদায়েতের ভিত্তিতে শাসন; খ. আদল (ন্যায় ও যথার্থতা) প্রতিষ্ঠা; গ. নৈতিক সংযম এবং ঘ. আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সমাজ গঠন।
অতএব, রাষ্ট্রনীতি হলো আল্লাহর প্রদত্ত ফিতরাত (সহজাত প্রকৃতি) ও হেদায়েতের প্রয়োগের রাজনৈতিক কৌশল।
বারানির দৃষ্টিতে রাজতন্ত্র একটি উপযোগী কাঠামো কিন্তু তা তখনই কার্যকর, যখন রাজা ন্যায়পরায়ণ, কল্যাণী ও দ্বীনদার হন।
বারানির ইতিহাসচর্চা ভবিষ্যৎ শাসকদের জন্য ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতির পথনির্দেশ করে। তার মতে, ইতিহাস কেবল অতীত নয়; বরং রাজনৈতিক আদর্শ গঠনের পাথেয়। ফলে তিনি ইতিহাস রচনা করেন যেসব দৃষ্টিকোণ থেকে, তার অন্যতম হলো ক. কোন রাজা ইনসাফ ও হেদায়েতের অনুগামী ছিলেন? খ. কার রাজনীতি মাসলাহা বা সামগ্রিক কল্যাণবর্জিত ছিল? গ. কেমন রাষ্ট্রনীতি মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়?
শরিয়াহর দাবিকে প্রাধান্য দিয়েও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসের সাথেও তিনি চলমান থাকেন। আল ফারাবিবাহিত প্লেটো ও এরিস্টটলের চিন্তার প্রভাব মানেন বারানি। তিনি মনে করেন, রাজনীতি হচ্ছে ন্যায়বিচারের প্রকাশ ও অপরাধ দমন।
৫. ঐতিহাসিকের দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতা : বারানি ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন ন্যায়ের চেতনা বিস্তারের জন্য। তার বিচারে ঐতিহাসিকের প্রথম দায়িত্ব হলো নৈতিক বিচারবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সত্যবাদের অনুশীলন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঐতিহাসিক কেবল ঘটনাপঞ্জি লেখেন না; বরং তিনি জনগণ ও শাসকের জন্য এক নৈতিক আয়না নির্মাণ করেন, যার মাধ্যমে সমাজ নিজের ভুল ও সঠিক পথ শনাক্ত করতে পারে। এখানে ইতিহাসচর্চা একদিকে ইবাদত, আবার রাজনৈতিক ও নৈতিক দায়িত্ব।
ভবিষ্যৎ রাজনীতির নৈতিক পথনির্দেশনার প্রশ্ন
বারানির ইতিহাসচর্চা ভবিষ্যৎ শাসকদের জন্য ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতির পথনির্দেশ করে। আদল (ন্যায়) ও নৈতিকতাই ছিল তার ইতিহাস লেখার মূল মানদণ্ড। বারানির ইতিহাসতত্ত্বে ঐতিহাসিক কেবল অতীত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না; বরং তিনি ভবিষ্যতের রাজনীতির জন্য নৈতিক ও ইনসাফপূর্ণ গাইডলাইন তৈরি করেন।
ঐতিহাসিকের সীমাবদ্ধতা ক্ষমতার চাপ ও সত্য রক্ষার সংগ্রাম : তৎকালীন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতা অনেক সময় ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। তবে বারানি সত্যের প্রতি যতটা সম্ভব নিষ্ঠাবান ছিলেন।
আমরা দেখি, বারানি দরবারের ঘনিষ্ঠ, সুলতানদের আশপাশে অবস্থান করেন, কখনো প্রশস্তি লিখতে বাধ্য হন কিন্তু তাতেও তিনি ইতিহাস বিকৃত করেননি।
বারানি বুঝেছিলেন ঐতিহাসিক কখনোই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারেন না কিন্তু নৈতিক সত্য থেকে দূরে থাকা অনুচিত।
সত্য ও আদর্শের দ্বন্দ্ব : ঐতিহাসিকের চরম বাস্তবতা
ইতিহাস যেমন নীতিকথা নয়, তেমনি কেবল তথ্যসংগ্রহও নয়। বারানি এই দুয়ের মাঝে একটি ভারসাম্য খুঁজেছেন। তিনি ঐতিহাসিকের অবস্থানকে দেখেন দুই বিপরীত শক্তির মাঝে দাঁড়ানো একজন চিন্তক হিসেবে, যার একদিকে আদর্শ ও ন্যায়ের দাবি, অন্যদিকে দরবার, রাজা ও ক্ষমতার চাপ। এই দ্বৈত বাস্তবতা ঐতিহাসিককে করে তোলে সঙ্কীর্ণ, সাবধানী, কিন্তু সাহসী এক নৈতিক কর্মী।
বারানির মতে, ঐতিহাসিকের দায়িত্ব বিশাল, কিন্তু সীমাবদ্ধতাও বাস্তব। ইতিহাসবিদ সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক বিবেক। তিনি অতীত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের ন্যায়নীতি নির্দেশক, আবার তিনি ক্ষমতার বলয়ে থাকা এক বিপন্ন সত্যপ্রেমীও।
তার বাস্তবতার একপাশে বা সব পাশে সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা, অপর পাশে বা সব পাশে ক্ষমতার লালচোখ ও অক্টোপাসি বাস্তবতা। এই বিপরীতমুখী দ্বৈত চাপে থাকতে হয় ইতিহাসবিদকে। ফলে তার চলার পথটি কঠিন। তবুও ন্যায়ের পক্ষে অটল থাকা তার প্রধান দায়িত্ব।
মোদ্দা কথা, জিয়াউদ্দিন বারানির ইতিহাসচর্চা ছিল ধর্ম, রাজনীতি ও নৈতিকতার সমন্বয়ে গঠিত এক বিশেষ দর্শনচিন্তামূলক প্রবাহ। তার রচনা শুধু ইতিহাসের ধারাবিবরণ নয়, একটি মূল্যবোধভিত্তিক রাজতন্ত্রের খসড়া। বারানি ইতিহাসকে সমাজের দর্পণ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বারানি কেবল গুরুত্বপূর্ণই নন, ইতিহাসসম্পর্কিত বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির গঠনে তিনি অনন্য মাইলফলক।
লেখক : কবি, গবেষক