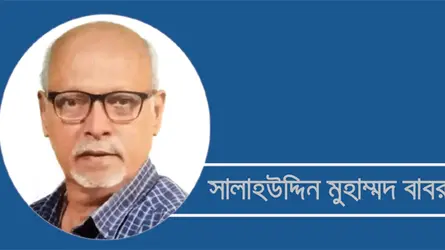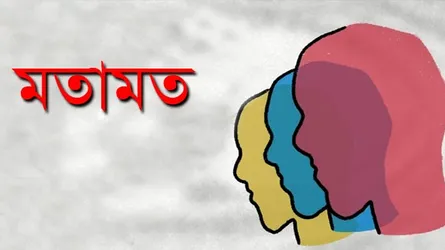তিন স্টেকহোল্ডার তথা সরকার, রাজনৈতিক দলগুলো এবং রাষ্ট্রযন্ত্র। এই তিন পক্ষ নির্বাচন নিয়ে এখন একই সমান্তরালে হাঁটছে। বিস্ময়ের হলেও এটাও সত্য, এর ধ্বনি- প্রতিধ্বনি কিন্তু লোকসমাজে তেমন একটা লক্ষ করা যাচ্ছে না। অনেকে জানেন, এ অঞ্চলের মানুষের ভোট নিয়ে আগ্রহ-উৎসাহ-উদ্দীপনার কখনো কমতি ছিল না। তবে এখন সেই ভোট নিয়ে লোকসমাজ এতটা নির্লিপ্ত নির্বিকার, যা অভূতপূর্ব। বিজ্ঞজনদের ধারণা, বিগত তিন তিনটি নির্বাচন নিয়ে জনমনে যে দুঃসহ স্মৃতি, তা এখনো কারো মন থেকে মুছে যায়নি। আগামী নির্বাচন কেমন হবে, ওই প্রশ্নেও সবাই দ্বিধাদ্ব›েদ্ব আছেন। আগামী নির্বাচনের রূপ-স্বরূপ নিয়ে এখনো আতঙ্কে আছে মানুষ। সব স্টেকহোল্ডার নির্বাচন নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছালেও আগামীতে দেশবাসীর কাক্সিক্ষত মানের একটা নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব কি না- তা নিয়ে সর্বত্র দোদুল্যমানতা বিরাজ করছে। যারা ভোট দেবেন, তাদের মধ্যে এখনো সংশয়, শঙ্কা, দ্বিধা-দ্ব›েদ্বর অবসান হয়নি। এ সম্পর্কিত তাদের নানা প্রশ্নের সুরাহা হয়নি- সরকার ও বাকি দুই অংশীজন নির্বাচনের জন্য প্রকৃত অর্থে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হবে। এখনো সাধারণের মধ্যে সে বিশ্বাস জন্ম নেয়নি আর নতুন ভোটার হতাশ হওয়ার পথে। এমন পরিবেশ পরিস্থিতিতে নির্বাচন করা হলে, সেটা একটি অর্থহীন ভোটাভুটিতে পর্যবসিত হতে পারে। সে কারণে জনগণের মনোজগতে ঝড়ো হাওয়া বইছে। অথচ মানুষ গভীর আকুতি নিয়ে একটি অর্থপূর্ণ নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন। যে অপেক্ষা কোনোভাবে স্বার্থক হবে না- যদি ‘যেনতেন’ একটা নির্বাচন করা হয়। লোকসমাজে নির্বাচন নিয়ে যে কল্পনা, তাতে কোনো তৃপ্তির পরশ থাকবে না। বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা কোনোভাবে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিষয়টি নিয়ে স্টেকহোল্ডারদের অবশ্যই ভাবতে হবে, বুঝতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে শঙ্কাটা কোথায়। সে সম্পর্কে কারো অভিমত, উপদেষ্টা পরিষদের আন্তরিকতা নিয়ে কারো প্রশ্ন না থাকলেও; তাদের মধ্যে সবাই কি সমান দক্ষতার সাথে খেলতে পারবেন নির্বাচন নিয়ে। এ ক্ষেত্রে কিছুটা আস্থার সঙ্কট বিরাজমান। যেকোনো খেলায় বিজয়ী হতে হলে দলের ১১ জনকে সমানতালে খেলতে হয়। না পারলে ব্যত্যয়ের আশঙ্কা থেকে যায়। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাকি দুই স্টেকহোল্ডারের ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে তাদের ভূমিকার মূল্য কতটা; সবাইকে তা বুঝতে হবে। অন্যতম স্টেকহোল্ডার রাজনৈতিক দলের কারো কারো সহযোগীদের ভূমিকা নিয়ে সীমাহীন শঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে নানা স্থানে ওই সহযোগীদের ভূমিকা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কেউ বলছেন, জাতিকে কি এখন সেই প্রস্তর যুগে টেনে নেয়া হচ্ছে!
তাদের আচরণে পতিত যুগের প্রতিচ্ছবি বৃত্তাকারে মানুষের মনমগজে ঘুরছে। তবে এ কথা সত্য, তাদের ভূমিকার পেছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছেন কি না তা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে। খোদা না করুন, এমন কিছু যদি নির্বাচন পর্যন্ত বহাল থাকে, তবে নির্বাচনের পরিবেশ শুধু অক্ষুণ্ণ হবে না; গোটা নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ ও কালিমাযুক্ত হয়ে পড়বে। যদি তেমন কিছু ঘটে যায়, তখন গোটা জাতির পরিতাপের আর কোনো বিকল্প থাকবে না। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারের রাজনীতিতেও বড় ধরনের ধস নামতে পারে, যা কারোরই কাম্য নয়। তাদের ভালো একটি অতীত ছিল এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আছে। তাদের মধ্যে এখন যেন আত্মহননের একটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। অথচ সময় হাতছাড়া হলে কোনো ‘সলিউশন’ কাজে আসবে না।
এবার আসা যাক, তৃতীয় প্রশ্নে; অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্র। নির্বাচন নিয়ে তাদের ভূমিকা গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ১৯৯১ সালে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রযন্ত্র ইতোবাচক ভূমিকা পালন করে। ফলে দেশে একটা প্রশ্নমুক্ত ইতিহাস খ্যাত নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিল। জাতির দুর্ভাগ্য, সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের উত্তরসূরিরা গৌরবের ওই অতীতকে জলাঞ্জলি দিয়ে বহু প্রহসনের নির্বাচনে সহায়তা দিয়েছে। বিশেষ করে গত ১৬ বছরে তিনটি তথাকথিত নির্বাচনে তারা ‘উদম’ হয়ে কাজ করেছে। ইলেকশনকে সিলেকশনে রূপান্তরিত করতে সহায়তা দিয়েছিল। ওই রাষ্ট্রযন্ত্র তখন পতিতজনের সেবাদাসে পরিণত হয়, অতীতে যারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি! রাষ্ট্রযন্ত্রের ওই কর্মকর্তাদের প্রেতাত্মা এখন চারপাশে বিরাজ করছে। তাহলে হবেটা কি! একটি শ্রেষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তাদের বিশ্বাসযোগ্যটা কোথায়। তারপরও যদি উপরিউক্ত তিন সত্তার এক সাথে এক লয়ে এক তালে মিলতে পারেন; তবেই জনতা আকাক্সক্ষার আশাবাদ অটুট থাকার সম্ভাবনা হয়তো কিছুটা থাকবে।
দ্বিরোক্তির কোনো অবকাশ নেই, একটি ভালো নির্বাচনের ফল সুদূরপ্রসারী এক প্রভাব ফেলবে। বিগত ১৫-১৬ বছর জাতির বুকে দুর্যোগ দুর্ভোগের এক জগদ্দল পাথর চেপে বসেছিল। তা থেকে মানুষের পরিত্রাণের সম্ভাবনা থাকবে। বাংলাদেশ তখন আপন মহিমায় জেগে উঠতে পারবে। নতুন এক দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হবে। সবার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটবে। প্রতিটি জনপদ কর্মমুখর হয়ে উঠবে। প্রতিটি দিন নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে পারবে। তবে পোকায় খাওয়া কোনো নির্বাচন হলে, ১৮ কোটি মানুষ সে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করবে। মানুষের মন থেকে সব আশার আলো একসাথে দপ করে নিভে যাবে। দেশকে পুনর্গঠন পুনর্নির্মাণের যে প্রত্যয়-প্রত্যাশা- সেটা নিমিষে চোরাবালিতে তলিয়ে যাবে। জাতি তখন বিমর্ষ হলেও পতিত সত্তা খিলখিলিয়ে হাসবে। পতিতদের পৃষ্ঠপোষকরা এ দেশের মানুষের ঘাড়ে আবারো জোয়াল তুলে দেবে। তাদের শোষণ প্রক্রিয়া দ্বিগুণ তিন গুণ করবে। এমন নেতিবাচক প্রভাব-প্রক্রিয়া শুরু হবে যা কি না কল্পনার অতীত। উপরিউক্ত তিন পক্ষকে এখন বেছে নিতে হবে। তারা কোন পথে হাঁটে। সম্মুখে মাত্র দু’টি বিকল্প রয়েছে- একটি মুক্তির, অন্যটি আত্মবিলুপ্তি। অতীতে জাতি তিনবার বিপুল রক্তের বিনিময়ে নিজেদের শৃঙ্খলমুক্ত করেছিল। আবারো যদি প্রয়োজন পড়ে, তবে প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তুত একজনকে শহীদী কাফেলায় যোগ দেয়ার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করবে।
ধরে নেয়া যাক, নির্বাচন ভালোয় ভালোয় উৎরে গেল। কিন্তু তারপর কি! নির্বাচন-উত্তর কী হতে হবে- একটা নতুন সংবিধান প্রণয়ন, নতুন সরকার এবং নতুন দিনের একটা সংসদ। তারপরও জনপ্রত্যাশা শেষ হবে না। সমাজে যার বা যাদের গ্রহণযোগ্যতা যত বেশি, স্বাভাবিকভাবে তাদের কাছে জনপ্রত্যাশা আকাশচুম্বী। জানি, দেশে সম্পদের সীমবদ্ধতা আছে। পতিত সরকারের বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগের একটি ছিল মানুষ মানুষে ভেদ-বৈষম্য সৃষ্টি করা। নতুন প্রশাসন যদি নতুন দিনের একটা ভালো পরিকল্পনা ও সঠিক পথনকশা তৈরি করতে পারে; তবে সম্পদের স্বল্পতা সত্তে¡ও সর্বত্র তার একটা স্পর্শ পড়বে। তেমন একটা যোগ্য সরকার গড়তে কালবিলম্ব হলে সবার জন্য সহ্যের সীমা অতিক্রম করবে। ভালো সরকার বলতে এ মুহূর্তে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দিকে তাকানো সম্ভব নয়। আর দেশেও কেমন একটা দক্ষ যোগ্য সরকারের উদাহরণ বিরল। তার পরও যদি ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ সালের ২৯ মে পর্যন্ত যে সরকার ছিল, সেটি শাসন নয় দেশের জন্য দায়িত্ব পালন করেছিল। সেই ধরনের একটা সরকার হলেও পথহারা জাতি আপাতত একটা ভিশন খুঁজে পেতে পারে। দেশে যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল; তা শুধু কাগজে কলমে ছিল। তথাকথিত সেই সব সংসদের জন্য হাজারো কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।
বিশ্বব্যাপী সংসদীয় সরকারব্যবস্থা জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সে ব্যবস্থা কেবল নামকাওয়াস্তে ছিল। কার্যত গত ১৫ বছর প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশে অদ্ভুত স্বৈরতান্ত্রিক একটি ব্যবস্থা পোক্তভাবে কায়েম ছিল। সংসদীয় ব্যবস্থার কোনো কিছু অনুশীলন অনুসরণ করা হয়নি। নিশ্চয় এখনই বাংলাদেশের ইংল্যান্ডের ‘মাদার’ পার্লামেন্টের সমকক্ষ হওয়ার মতো সংসদের কোনো স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়। তবে অন্তত দেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের অনুরূপ একটা সংসদ তৈরি করা অনিবার্য। সেই সংসদে সংসদীয় প্রায় অনুরূপ শৈলী অনুশীলন করা হতো। জবাবদিহিমূলক তেমন একটা সংসদ প্রতিষ্ঠার বিকল্প কিছু নেই। ওই দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার-ব্যবস্থার অধীন একটি পার্লামেন্ট ছিল। অথচ তার ভূমিকা ছিল সংসদীয় ব্যবস্থার প্রায় অনুরূপ। এর পরবর্তীতে আর কোনো সংসদে তেমন কিছুর অনুশীলন ছিল না। সংসদ পরিচালনায় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির গুরুত্ব সর্বাধিক। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ছাড়া আর কোনো সংসদের সংসদ কার্যপ্রণালী বিধির কোনো চর্চা ছিল না।
’৭২ সালে গৃহীত সংবিধান কার্যত এখন অচল। এ ছাড়া আওয়ামী আমলে বারবার ইচ্ছামতো ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে এতে। একে জাতীয় নয় দল ও দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ‘পকেট বুক’ হিসেবে পরিণত করা হয়েছিল। সেই পকেট বুক তাকে স্বৈরশাসকে পরিণত করেছিল। সেই তথাকথিত সংবিধানকে পুনর্লিখন বা আমূল পরিবর্তন করা না হলে আবারো যে কারো স্বৈরাচারে পরিণত হওয়ার শতপথ খোলা থাকবে। জাতি এ মুহূর্তে এর পরিবর্তন চায়। সংবিধান জাতির প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্য। তা নিয়ে যে কাজ চলছে- তাকে সবাই সাধুবাদ জানাচ্ছে।
শেষ করব আরো দু-একটি কথা বলে। যেসব ব্যবস্থা পোকায় কেটেছিল সেগুলোর আমূল পরিবর্তন পরিমার্জন ছাড়া একচুল সামনে এগোনো কোনোভাবে সম্ভব নয়। এ সংশোধন পরিমার্জনে যত বাধাবিপত্তি আসুক না কেন, তার মোকাবেলা করতে হবে; তা না হলে চব্বিশের বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।