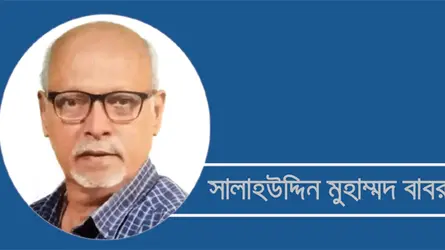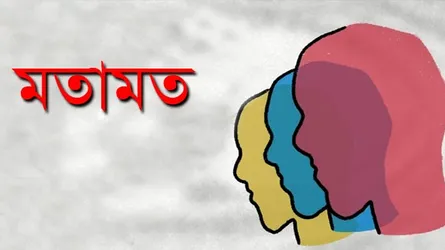ঢাকার গায়ে লেগে থাকা ধুলোর মতোই যেন নাগরিক ক্লান্তি। যানজট, অব্যবস্থা, সময়ের অপচয় সবকিছুর মাঝে হঠাৎই যেন এক টুকরো নিশ্বাস ফেলার জায়গা হয়ে উঠেছে মেট্রোরেল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বগির ভেতরে প্রবেশ করলেই বাইরের নাকাল ঢাকা যেন আরেক গ্রহের গল্প মনে হয়।
অথচ এই স্বস্তি এবং শৃঙ্খলার মধ্যেও রয়েছে কিছু হালকা আঁচ, কিছু অসঙ্গতির চাকা ঘোরে উল্টো দিকে। মেট্রোরেল তার নির্মাণে যেমন ব্যয়সাধ্য, তেমনি যাতায়াতে তুলনামূলক বেশি ভাড়াও চায়। কিন্তু শহরের সময়-সঙ্কটগ্রস্ত নাগরিকের কাছে তা যেন স্বস্তির বিনিময়ে গ্রহণযোগ্যই হয়েছে। টিকিট কাটার লাইনে, এস্কেলেটরের পাটায় কিংবা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের সারিতে মেট্রো যেন এক নতুন ধরনের শৃঙ্খলার বার্তা দেয়।
কিন্তু এই শৃঙ্খলা যেন কিছু জায়গায় এসে গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। সেসব জায়গা মানে অগ্রাধিকার আসন কিংবা লিফটের অগ্রাধিকার ব্যবহার।
মেট্রোর প্রতিটি বগিতে দুই পাশে থাকে ছয়টি করে। অর্থাৎ মোট বারোটি ‘অগ্রাধিকার আসন’। স্পষ্টভাবে লেখা থাকে বাংলা-ইংরেজিতে, ‘বয়স্ক, শারীরিকভাবে অক্ষম, গর্ভবতী নারী ও শিশু কোলে থাকা নারীদের জন্য সংরক্ষিত।’ এমনকি বোঝাতে ছবিও দেয়া হয়েছে, যেন ভাষা না জানলেও হৃদয়টা যেন বোঝে!
কিন্তু বাস্তবে কী ঘটে? এক দল কিশোর, তরুণ কিংবা মাঝবয়সী যাত্রী চোখ বুজে বসে পড়েন ওই আসনে, ঠিক যেন নিজের অধিকার! পাশেই এক বৃদ্ধা কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে আছেন, আর ছেলেটি হয় মোবাইল স্ক্রলে ডুবে, নয়তো চাহনির এক প্রাচীন কৌশল- ‘আমি তো কিছু দেখিনি!’
একই চিত্র লিফটেও। ‘অগ্রাধিকার ব্যবহারকারী’ বোঝাতে লিফটের গায়ে লেখা আছে, ছবি টানানো আছে। কিন্তু একহাতে ব্যাগ, অন্য হাতে কফির কাপ নিয়ে তরুণটি স্বচ্ছন্দে ভেতরে ঢুকে যায়। আর পিছনে থাকা হুইলচেয়ারে বসা মানুষটি কিংবা হাঁটুর ব্যথায় ধুঁকতে থাকা প্রৌঢ়টি চোখের ভাষায় অনুরোধ করলেও তাদের সেই অনুরোধ হয় বাতাসে উবে যাওয়া এক আওয়াজের মতো।
কখনো কেউ সাহস করে কিছু বললে তার প্রতিদান মেলে ‘টিটকারি’। ‘আরে দাদা, আইন বানালে তো সবাই মানে না!’ অথবা, ‘এইটা কি আপনার বাবার লিফট?’
এই অভিজ্ঞতা শুধু বিরক্তিকর নয়, এটি একধরনের নাগরিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। আর এই ব্যর্থতা শুধু ব্যবস্থাপনার নয়, আমাদের মানসিকতার, আমাদের শিষ্টাচারের।
তাহলে উপায়?
আমরা যদি আসলেই পরিবর্তন চাই, তবে চাই একটি সামাজিক ‘আয়না’; যেখানে মানুষ নিজের আচরণ দেখে লজ্জিত হবে। মেট্রোর স্টেশন ও বগির ভিতরে থাকা মনিটরগুলো হতে পারে সেই আয়না।
প্রতিটি স্টেশনে ও প্রতিটি বগিতে নিয়মিতভাবে দেখানো হোক
– কারা অগ্রাধিকার আসনে বসে আছেন এবং তারা সেই আসনের উপযুক্ত কিনা
– কারা মধ্যভাগ দিয়ে হুড়োহুড়ি করে উঠে পড়ছেন, যেখানে ওঠার রাস্তা নির্ধারিত দু’পাশ
– লিফটের সামনে কে কার ‘অগ্রাধিকার’ ছিনিয়ে নিচ্ছেন
এমন ভিডিও যখন ঘনঘন চলবে, হয়তো লজ্জাহীন মানুষগুলো একবার হলেও লজ্জিত হবেন। যখন কেউ নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখবেন বড় পর্দায়—এক বৃদ্ধকে ঠেলে ঢুকে পড়ছেন লিফটে কিংবা মোবাইলে মগ্ন থেকে গর্ভবতী নারীকে দাঁড় করিয়ে রাখছেন, তখন হয়তো অন্তত চোখ নামিয়ে ফেলবেন।
এই কাজ অবশ্য রাতারাতি করা উচিত নয়। আগেভাগে ঘোষণা দিতে হবে, ‘আগামী মাস থেকে মেট্রো ও স্টেশনের মনিটরে যাত্রী-আচরণ দেখানো হবে।’ বারবার ঘোষণা হোক, যেন কেউ পরে ‘আমি জানতাম না’ বলে চিৎকার করার সুযোগ না পায়। কারণ, সম্মান চেয়ে নিতে হয় না। সেটা দিয়ে দিতে হয়। অগ্রাধিকার আসন অনুগ্রহ নয়, সেটি সম্মানের দাবিদার মানুষের জন্য।
মেট্রো আমাদের সময় বাঁচাচ্ছে, আর আমরা কি পারি না একটু মানবতা দেখাতে? ঢাকা শহরের মানুষ যদি নিজেদের পরিচয় দিতে চায় নতুন নগর-সভ্যতার অংশ হিসেবে, তবে শুরু হোক সেই সভ্যতা একজন মানুষকে তার ন্যায্য আসন ফিরিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে।
আশা করি মেট্রো কর্তৃপক্ষ এই আহ্বান বুঝবে, শুনবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এই নগরটা বদলাতে শুরু করেছে মেট্রোর হাত ধরে। এবার সময় এসেছে মনটা বদলানোর।