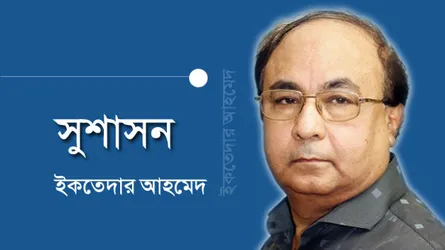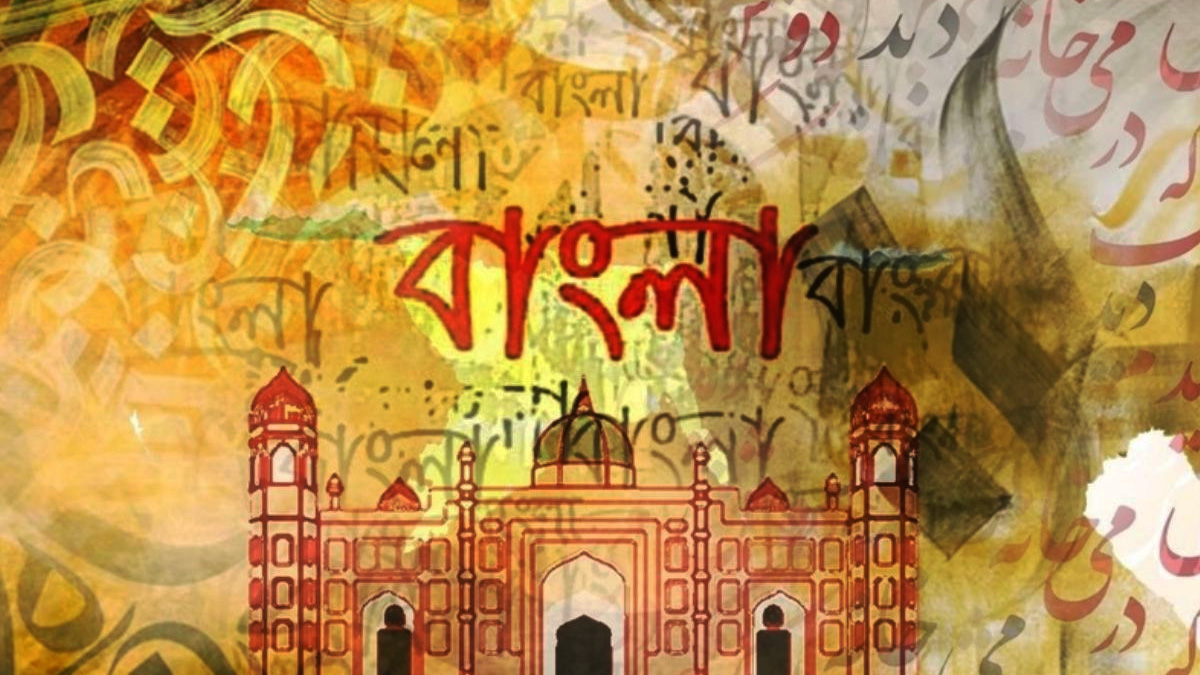আলেক্স জোভেন
বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতে পারস্য বা আধুনিক ইরানের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাণিজ্য, আধ্যাত্মিকতা ও নান্দনিক বিনিময়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই ছাপ আজও আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও সাহিত্য, উৎসব ও সঙ্গীতে শোনা যায়। বাংলার সাথে ফরাসি মিশ্রণ একটি অনন্য সাংস্কৃতিক পরিচয় তৈরি করেছে, যা এখনও বাঙালির আবেগ ও অভিব্যক্তিকে রূপায়ণ করে।
প্রখ্যাত জার্মান কবি, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক ইয়োহান ভোলফগাং ফন গ্যোটে একবার লিখেছিলেন, “অন্য সাহিত্যের প্রভাব ছাড়া কোনো জাতির সাহিত্য পূর্ণ হতে পারে না।” বাংলা ভাষা এই সত্যের জীবন্ত প্রমাণ। যদিও বাংলা প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃত থেকে জন্ম নিয়েছে, এটি আরবি, তুর্কি এবং সবচেয়ে গভীরভাবে পারস্যের প্রভাবের সংস্পর্শে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে।
বাংলায় পারস্যের ভাষা প্রবেশের সূচনা ঘটে মধ্যযুগের ত্রয়োদশ শতকে, বখতিয়ার খিলজির অভিযানের সময়। চতুর্দশ শতক থেকেই ফারসি বাংলার রাজদরবার, আইন, শিক্ষা ও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। ষোড়শ শতকে মোগল আমলে এটি সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করে। সেই সময় আদালতের নথি, রাজস্ব খতিয়ান, সেনা-আদেশ—সবকিছুই ফারসিতে রচিত হতো। এই সময় বাংলার শব্দভাণ্ডারে স্থায়ী আসন নেয় “দফতর” (অফিস), “খাজনা” (কর), “ফরমায়েশ” (আদেশ)-এর মতো শব্দ, যা সাম্রাজ্যের অবসান ঘটলেও আজও তা এই ভূখণ্ডে রয়ে গেছে।
প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রিচার্ড ইটন এই প্রবাহকে কোনো আধিপত্য নয়, বরং অভিযোজন হিসেবে দেখিয়েছেন—যেখানে পারস্যের ধারা স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলে এক স্বতন্ত্র বাঙালি সংস্কৃতি তৈরি করে।
ধীরে ধীরে হাজার হাজার ফারসি শব্দ বাংলার ভান্ডারে যোগ হয়। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, প্রায় দুই হাজার ফারসি শব্দ বাংলা অভিধানে যোগ হয়েছে। একইসঙ্গে অনেক সময় আরবি ও তুর্কি শব্দও বাংলার সাথে মিশে গেছে। যেমন—“বাজার” (হাট), “খবর” (সংবাদ), “দুনিয়া” (বিশ্ব)—এসব শব্দ এতটাই সাধারণ হয়ে গেছে যে এগুলো ছাড়া বাংলা ভাবাই কঠিন।
মধ্যযুগের কবিরা ফারসির ভঙ্গি ও কল্পনা ব্যবহার করে এক নতুন “দোভাষী” ধারার সূচনা করেছিলেন। সেখানে ফারসি-আরবি মিশ্রিত শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করা হতো, এমনকি অনেক সময় আরবি হরফেও লেখা হতো। সেই সময়ে পুঁথি, ধর্মীয় গ্রন্থ আর আইনি নথিতে এ ধারার প্রভাব দেখা যেত। একই সঙ্গে লাইলি-মজনু, ইউসুফ-জুলেখার মতো পারস্যের প্রেমকাহিনী বাংলায় অনূদিত হয়ে মানুষের মনে জায়গা করে নেয়।
পারস্যের প্রভাবের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দিক ছিল কবিতা। রুমি, হাফিজ আর সাদীর আধ্যাত্মিক রূপক ও ভাবনা বাংলার কবিতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আলাওল, দৌলত কাজী ও সইদ সুলতানের মতো কবিরা তাঁদের লেখায় সেই কল্পচিত্র ও রূপক ব্যবহার করেছেন। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে স্পষ্ট দেখা যায় ফারসির সেই প্রভাব। “ইশ্ক” (প্রেম), “দিল” (হৃদয়), “মেহফিল” (আসর), “মঞ্জিল” (গন্তব্য)—এসব শুধু ধার করা শব্দ নয়; এগুলো হয়ে উঠেছিল আবেগ, ভালোবাসা ও আধ্যাত্মিকতার বাহক। গবেষক আন্নেমারি শিমেল লিখেছেন, পারস্যের সুফি ঐতিহ্য এমন এক ভাষা তৈরি করেছিল যেখানে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে দূরত্ব ঘুচে যায়।
রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, ভাষা বেঁচে থাকে অন্যের প্রভাব গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই। আর সৈয়দ মুজতবা আলী মন্তব্য করেছিলেন, পারস্য বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে নতুন বৈচিত্র্য ও গভীরতা।
সঙ্গীতেও ছিল পারস্যের গভীর প্রতিধ্বনি। সুফি সাধকেরা নিয়ে এসেছিলেন কাওয়ালি, গজল ও মাকামের ধারা, যা এসে মিলেমিশে যায় বাংলার বাউল ও ভাটিয়ালি লোকসঙ্গীতে। পারস্যের মাকাম ধীরে ধীরে ভারতীয় রাগের সঙ্গে একাত্ম হয়। বাদ্যযন্ত্রেও এই প্রভাব স্পষ্ট—“সেতার” এসেছে ফারসি শব্দ সে-তার (তিন তার) থেকে, আর তবলার তাল গঠনে আছে পারস্য-তুর্কি ছাপ।
মহরম উপলক্ষে কারবালার শোকগাথা জারিগানেও ছিল ফারসির রীতির ছাপ। আর গজল—যা পুরোপুরি পারস্যের ঐতিহ্য—উনিশ শতক থেকে বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলায় গজল রচনা করেন, যেখানে ফারসির ছন্দ, পুনরাবৃত্তি ও আবেগের তীব্রতা অটুট থাকে। গ্রামীণ বাউলগানেও ঢুকে যায় ইশ্ক (প্রেম) আর দিল (হৃদয়)-এর মতো শব্দ। এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীতেও পাওয়া যায় সুফি ভাবনার প্রতিধ্বনি—“দুনিয়া”, “ইমান”-এর মতো শব্দের মাধ্যমে।
ব্রিটিশ উপনিবেশ আসার পর বাংলায় ফারসির সরকারি প্রভাব মুছে যায়। উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে ইংরেজি প্রশাসনিক ভাষা হয়ে ওঠে। এরপর থেকে ফারসি মিশ্রিত বাংলার ব্যবহার ক্রমে কমতে থাকে। তবু ধার করা শব্দ, রূপক আর সুর থেকে যায় অমলিন। “খবর”, “বাজার”, “দুনিয়া”-র মতো শব্দ আজও আমাদের প্রতিদিনের ভাষার অংশ। গ্রামীণ কিসসা আর জারিগান আজও গ্রামে শোনা যায়।গবেষক কার্ল আর্নস্ট লিখেছেন, পারস্যের সুফি ধারা দক্ষিণ এশিয়ায় কোনো একক কর্তৃত্ব চাপায়নি; বরং দিয়েছে সৃজনশীলতার সুযোগ এবং তৈরি করেছে নতুন রূপান্তরের ধারা।
তাই বাংলায় পারস্যের প্রতিধ্বনি কোনো অতীত নয়, বরং এক জীবন্ত সুর। এটি ভাষাকে দিয়েছে আবেগের বৈচিত্র্য, আর সংস্কৃতিকে যুক্ত করেছে বৃহত্তর পারস্য ও ইসলামী জগতের সঙ্গে। এর সঙ্গে মিশেছে সংস্কৃত, ইউরোপীয় ও স্থানীয় ধারা। এই বহুমাত্রিক উত্তরাধিকারই বাংলার শক্তি।
আমরা যে বাজারে কেনাকাটা করি, যে খবর পড়ি, বা যে বাউলগান আজও গ্রামবাংলায় গাওয়া হয়—সবকিছুর ভেতরেই বাজে সেই পারস্যের সুর। বাংলা ভাষা, সঙ্গীত ও কাহিনিতে কান পাতলে এখনো শোনা যায়—পারস্যের ফিসফিসানি বাংলার সুরে মিশে আছে।