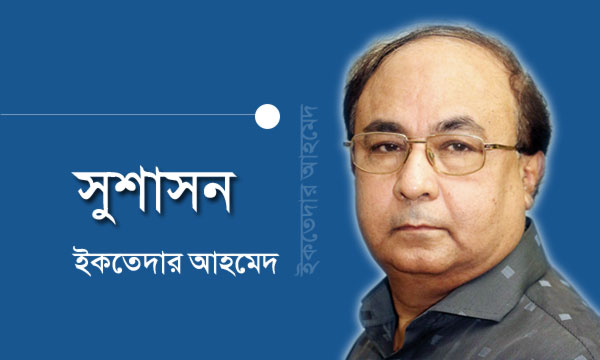বন উজাড় ও ভাগ্যের পাহাড়
- ইকতেদার আহমেদ
- ১৩ জানুয়ারি ২০২০, ২০:৩৫
বাংলাদেশসহ এ উপমহাদেশের অন্যান্য দেশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন থাকাবস্থায় ১৯২৭ সালে বন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই আইনটি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল বনজ উৎপাদনের বাহন এবং কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ উৎপাদনের ওপর কর আরোপ। এ আইনে সরকারের কোনো সম্পত্তি অথবা যে সম্পত্তির ওপর সরকারের মালিকানা স্বত্ব আছে অথবা বনজ উৎপাদনের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক যার ওপর সরকার স্বত্ববান এমন বনভূমি, পতিত ভূমি অথবা বনায়নযোগ্য ভূমিকে সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণার বিষয়ে সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়। এ আইনের অধীনে বনজ উৎপাদনের মধ্যে যেসব দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, বাঁশ, বেত, ফুল, ফল, পাতা, ঘাস, মধু, মোম, নানা প্রকার বন্যপ্রাণী, চামড়া, হাড়, শিং প্রভৃতি।
আড়াই শ’-তিন শ’ বছর আগ পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের ভূ-ভাগের অর্ধাংশেরও বেশি বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ও তরুলতা দিয়ে আবৃত ছিল। সে সময় সাধারণ মানুষের বসবাসের জন্য উপযোগী গৃহ নির্মাণের সব ধরনের দ্রব্য আশপাশের বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হতো। কায়িক শ্রমের মূল্য ব্যতীত এ সব সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সচরাচর কোনো অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হতো না।
প্রাকৃতিকভাবে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়গুলো সামুদ্রিক জাহাজ বানানোর উপযোগী বৃক্ষরাজিতে সমৃদ্ধ ছিল। এ কারণে আরব উপদ্বীপ ও ইউরোপের সাথে যোগাযোগের জন্য সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হলে সামুদ্রিক জাহাজ নির্মাণের উপযোগী কাষ্ঠ সম্পদের সহজলভ্যতার কারণে চট্টগ্রামে ১২০০ শতাব্দী থেকে ক্রমান্বয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ শিল্প ব্যাপক বিকাশ লাভ করে। তা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই টিকে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে পরাশক্তি অটোমান সাম্রাজ্যাধিপতি তুর্কিরা তাদের সামুদ্রিক নৌবহরে যেসব যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করেছিল, তার ৮০ শতাংশেরও বেশি চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড় থেকে সংগৃহীত কাঠ দিয়ে সন্দ্বীপে নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে কাষ্ঠ সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা এবং কাঠের জাহাজের স্থলে ইস্পাতের খোলের জাহাজের পুনঃস্থাপনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সমুদ্রগামী কাঠের জাহাজের প্রচলন একেবারে নেই বললেই চলে। তবে সমুদ্র উপকূলবর্তী অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ এবং লবণ পরিবহনে কাঠের খোলের জাহাজ বা বৃহদাকারের নৌকার ব্যবহার আজও সফলভাবে টিকে আছে।
ঔপনিবেশিক শাসক ব্রিটিশদের এ উপমহাদেশে আগমনের পর তারা পাহাড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চল এবং পতিত ভূমিতে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে বৃক্ষ রোপণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে তারা চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়গুলোয় বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান বৃক্ষ সেগুন, মেহগনি, চাপলাইশ, গর্জন, করই প্রভৃতি রোপণ করে বৃক্ষের গড় আয়ুভেদে বনাঞ্চলকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে সেগুলো পরিপক্ব হওয়ার পর কর্তনের ব্যবস্থা করে। এতে দেখা গেল বছরজুড়েই বৃক্ষ নিধন ও রোপণের কাজ চলছে। তবে বিশেষত শীত ও গ্রীষ্ম মৌসুমকে বৃক্ষ নিধনের কাজের জন্য বেছে নেয়া হতো। আর রোপণের কাজটি বর্ষা মৌসুমে বেশি গুরুত্ব পেত। এভাবে নিধন ও রোপণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হতো এবং সরবরাহ ও চাহিদার সমন্বয়ের মাধ্যমে বনভূমির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হতো। প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিধান প্রতিপালিত হতো। সিলেট ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বনভূমির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হতো না।
ব্রিটিশদের বিদায়ের পর উপমহাদেশ বিভক্ত হলে আমাদের পূর্ববঙ্গ ‘পূর্ব পাকিস্তান’ নামে অভিহিত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বনভূমি সংরক্ষণের আইন ও বিধিবিধান প্রয়োগে যে ধরনের কঠোরতা অনুসরণ করা হতো তা পাকিস্তানের শাসনামলে কিছু স্বার্থান্বেষী আমলার লোভ আর ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের কারণে শিথিল হতে থাকে এবং বাংলাদেশ হওয়ার পর ’৮০-এর দশকের প্রারম্ভ থেকে সে শিথিলতা কিছু আমলার স্বেচ্ছাচারিতা ও জবাবদিহির অনুপস্থিতিতে লোপ পেতে থাকে। এ অবৈধ সুযোগ যারা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ’৮০-এর দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ঊর্ধ্বতন যেসব কর্মকর্তা চট্টগ্রাম এবং বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অন্তর্ভুক্ত। বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে প্রশাসন, পুলিশ, বন বিভাগ ও অপর কোনো কোনো বিভাগের কর্মকর্তারা পারমিটের নামে কার্যত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটিয়েছেন।
’৭০-এর দশকের শেষ দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ‘শান্তি বাহিনী’র দৌরাত্ম্য শুরু হলে সে অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন বাহিনী মোতায়েন করে সমন্বয়কের দায়িত্ব সেনা অধিনায়কদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। তারা কর্তৃপক্ষকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, উপজাতীয় বিদ্রোহীরা পাহাড়ের দীর্ঘাকৃতির বৃক্ষগুলো কেন্দ্র করে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা গড়ে তোলায়, সফলভাবে ওদের বিদ্রোহ দমন করতে হলে সড়ক ও নৌপথে চলাচলের দু’ধারের বৃক্ষের কর্তন আবশ্যক। বৃক্ষ কর্তন ঠিকই হলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পকেট ভরল অসৎ কর্মকর্তাদের। এ ধরনের লোকজনের বাড়িঘর পরিদর্শন করলে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। এমন কর্মকর্তার নামও শোনা যায় যারা সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণের সব ব্যয় কাষ্ঠ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে নির্বাহ করেছিলেন।
বৃক্ষ নিধনের এ অবৈধ প্রতিযোগিতায় কোনো আমলা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পেছনে পড়ে থাকবেন, এ কেমন কথা। বিশেষত প্রশাসন, পুলিশ, বন বিভাগ এবং অপরাপর বিভাগের কিছু কর্মকর্তা যাদের বেশির ভাগ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে বর্তমান দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চাকরিতে ছিলেন, তারা বনজসম্পদ বিশেষত সেগুন কাঠ আহরণে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এ কাজ তাদের এতই বেসামাল করে দিয়েছিল যে, সরকারি কার্য সম্পাদনের চেয়ে কাষ্ঠ আহরণ তাদের অনেকের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।
এমন কর্মকর্তাদের মধ্যে উচ্চপদে কর্মরত প্রশাসনের জনৈক কর্মকর্তার উল্লেখ না করলে নিবন্ধটির আবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে।
এ কর্মকর্তা সাম্প্রতিককালে বনেদি আবাসিক এলাকায় বহুতল ভবনে সেগুন কাঠের যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে এক দিকে ভবনের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং অপর দিকে বিপুল কাঠ বিক্রি করে যে সম্পদের মালিক হয়েছেন, তার স্ফীতি এত ব্যাপক যে কেউ কেউ বলেন, দু’তিন প্রজন্মকে হয়তো আর ‘পেছন ফিরে তাকাতে হবে না’।
অপর এক ভাগ্যবান কর্মকর্তা তার ঢাকার বাড়ি, নিজ জেলা শহর ও গ্রামের বাড়ির দালানের সর্বত্র এত নিপুণভাবে সেগুন কাঠের ব্যবহার করেছেন, যা দেখলে তার রুচির প্রশংসা না করে পারবেন না। কিন্তু যখন জানা যায় তার এ কাষ্ঠ আহরণ সরকারকে বিপুল রাজস্ব থেকে বঞ্চিত এবং প্রাকৃতি ভারসাম্য নষ্ট করেছে, তখন তার প্রতি ক্ষোভই হতে পারে সমাজের সচেতন অংশের জন্য প্রকৃত প্রতিবাদ।
উপকূলীয় জেলায় কর্মরত জনৈক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অন্য জেলায় বদলি হয়ে গেলে বিপুল পরিমাণ সেগুনকাঠ তিনি তার মালামালের সাথে নতুন কর্মস্থলে নিয়ে আসেন। তার বাসভবনে কাঠ রাখার জায়গা না হওয়ায় তিনি সরকারি টাকা দিয়ে সেগুন কাঠ রাখার জন্য একটি ছাউনি নির্মাণ করেন, যাতে তার এ দুর্লভ কাঠ রোদ-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ কাঠ মহাদুর্লভই হয়েছিল এ কারণে যে, তিনি কাষ্ঠগুলো প্রতি বর্গফুট মাত্র ৬০ টাকা মূল্যে ক্রয় করে বাড়ির দরজা জানালা ও আসবাবপত্র নির্মাণের পরিবর্তে ক্রয়মূল্য থেকে ৪০ গুণ অধিক দরে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করেন। নিজ বিবেচনায় সৎ এ ব্যক্তি পরে আরো উচ্চপদে সমাসীন হয়েছিলেন।
বন বিভাগের কর্মকর্তাদের কীর্তিকলাপের ব্যাপারে সব শ্রেণীর মানুষ কমবেশি অবহিত। দীর্ঘকাল যাবৎ বিরামহীনভাবে বনজসম্পদের উজাড় হওয়ায় বর্তমানে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশির ভাগ পাহাড় বৃক্ষশূন্য। রাস্তার দু’ধারের পাহাড়ের দিকে তাকালে ১০ বছরের অধিক বয়সের গাছ পাওয়া যাবে হাতেগোনা কয়েকটি। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও আমাদের প্রতিটি পাহাড় সুউচ্চ বৃক্ষরাজি দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। এ কারণে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চতুর্পাশের দৃশ্যের অবলোকন গাছপালার ডালপালার প্রতিবন্ধকতার কারণে ব্যাহত হতো। কিন্তু সেসব গাছ আজ কোথায়? এ নিধনযজ্ঞে যারা সক্রিয় ছিলেন পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে তারা ছিলেন দেশ গড়ার দায়িত্বে। তাদের বিবেকের কাছে জনগণ কি প্রশ্ন রাখতে পারে না, পাহাড়ের বৃক্ষ নিধন করে তারা কি দেশ গড়েছেন না নিজেদের ভাগ্যের পাহাড় গড়েছেন?
লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক
E-mail: [email protected]
আরো সংবাদ
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা