স্কুলজীবনের খণ্ড কড়চা
- সারওয়ার মো: সাইফুল্লাহ খালেদ
- ০১ জুন ২০২১, ১৯:৫০
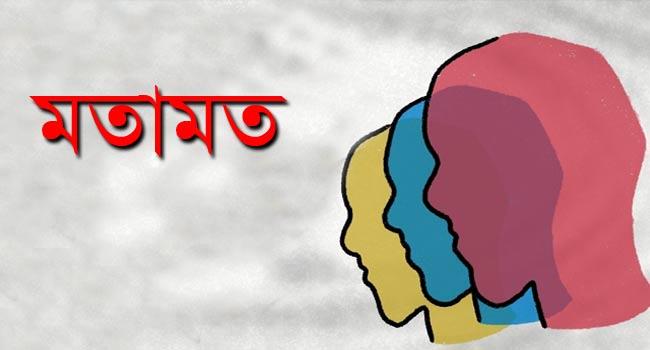
সবার স্কুলজীবনের কড়চা এক রকম হয় না। ১৯৪৮ সালে ছয় বছর বয়সে গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকা আসার আগে মাঝে মধ্যে শ্লেট-বই মাথায় করে কাছেই পশ্চিমের গ্রাম কদমতলীর ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে গিয়েছি। এরপর ঢাকা এলে আমাকে এবং আমার বড় বোনকে আব্বা বাসার কাছেই একটি স্কুলে দিলেন। স্কুলের নাম আনন্দ বিদ্যাপিঠ। বর্তমানে যেটি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ সে ভবনটি তখন আনন্দ বিদ্যাপিঠ। তিন তলার উত্তর-পূর্ব কোণের একটি কক্ষে সতরঞ্জি বিছিয়ে আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হতো। মাসিক দুই আনা বেতন। এক দিন খয়েরি সুতির শাড়ি পরা এক মধ্যবয়সী মহিলাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখলাম। সাথে ক’জন পুরুষ। কে একজন বলল, মহিলা রবিঠাকুরের আত্মীয়া। রবিঠাকুর কে বা কী জানতাম না। ঢাকা এসে প্রথমে ঋষিকেশ দাস লেনের ৮৮ নম্বর যে বাসায় আমরা উঠেছিলাম তা বছর খানেক পর ছাড়ার সাথে সাথে এ স্কুল ছেড়ে দেই।
এরপর ১৯৪৯ সালে ওয়ের স্ট্রিটের ৩ নম্বর বাসায় এলে আব্বা আমাদের দুই ভাইবোনকে পৃথক দু’টি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আমার বোন ভর্তি হলো কামরুন্নেছা গার্লস হাইস্কুলে। আমাকে প্রথমে দিলেন ইসলামিয়া হাইস্কুলে ক্লাস ওয়ানে। মন চায় না স্কুলে যেতে। তবু যাই। এক রকম জোর করেই পাঠানো হয়। এক দিন আরবির শিক্ষক কী এক পড়া জিজ্ঞেস করলেন। পারলাম না। হাত পাততে বললেন। হাত পাতলাম। দিলেন কষে এক বেতের বাড়ি। ডান হাতের মধ্যমার ডগা ফেটে একটু রক্ত বেরুল। অজুহাত পেয়ে গেলাম। মাস্টার মারে। স্কুলে যাবো না। কিন্তু আব্বা নাছোড়বান্দা। স্কুলে যেতেই হবে। যাই। কিন্তু গিয়ে ক্লাসে যাই না। আমাদের গ্রামের বাড়ির উত্তরপাড়ার জ্ঞাতি মাইনুদ্দিন সরকারের বাড়ির কেরামত ভাই সে স্কুল সংলগ্ন ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বেয়ারার। কলেজ এবং স্কুল একই বাউন্ডারির ভেতর। এরই মধ্যে মাঝখানে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একঠি একতলা ভবন। তার উত্তর দিকের একটি কক্ষে তার বাস। বাসা থেকে স্কুলে এসে তার কক্ষে দরজা বন্ধ করে একা শুয়ে থাকি। স্কুল ছুটি হলে বাসায় ফিরি। আমার এ অবস্থা দেখে তিনি আব্বাকে বলে কয়ে এ স্কুল ছাড়ালেন। মাত্র অল্প ক’দিন সে স্কুলে গিয়েছিলাম। সে কলেজটি এখন কবি নজরুল কলেজ।
এরপর দেড় বছর আমাকে আর স্কুলে ভর্তি করা হলো না। বাসায় আব্বা মাঝে মধ্যে সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে দুই ভাইবোনকে পড়ানোর চেষ্টা করতেন। লম্বা একটা বাঁশের বাতা নিয়ে আমাদের পড়াতে বসতেন। কোনো দিন আমাদের ওপর সেটার প্রয়োগ হয়নি। কিন্তু এটি দর্শনেই ভয় হতো। আব্বা ব্যস্ত মানুষ। সরকারি চাকুরে এবং একই সাথে ঢাকায় কুমিল্লা অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক। তার পক্ষে আমাদের পড়ানোর মতো সময় দেয়ার সময় নেই। দুই ভাইবোনকে পড়ানোর জন্য আমাদের এক আত্মীয়কে নিয়োগ করলেন। আধাপাকা দাড়ি, পঞ্চাশের কাছাকাছি এক কৃশকায় ভদ্রলোক। তিনি দূর সম্পর্কে আমাদের দুলাভাই। শনিবার বিকেল থেকে রোববার পুরোটা দিন ছুটি। তিনি চাকরি করতেন। প্রতি শনিবার বিকেলে মদনগঞ্জ চলে যেতেন। ফিরতে ফিরতে রোববার দিন পেরিয়ে রাত হয়ে যেত। তিনি আমাদের বাসায় খেতেন আর হলঘরে থাকতেন।
১৯৫২ সালে আবার আমাকে স্কুলে ভর্তি করা হলো। এবার নবাবপুর হাইস্কুলে। ক্লাস থ্রিতে। স্কুলের ভেতর পূর্ব দিকে একটি টিনের ঘরে ক্লাস বসত। ঘরটির কড়ি-বরগা সব লোহার। ক্লাস চলাকালে ঘরের কড়ি-বরগায় বানর লাফালাফি করত। এত দিনে বানর কোনো নতুন জিনিস নয়। ওয়ারীর বাসায় এসব দেখে অভ্যস্ত। বানরের কারণে ক্লাসে পড়ালেখার কোনো ব্যাঘাত ঘটত না। স্যারেরা ভালো পড়াতেন। ক্লাসে বেত আনতেন না। সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরা ছিপ ছিপে ফর্সা বাংলার শিক্ষক নুরুল হক স্যার ব্যাকরণ পড়াতেন। আরেকজন স্যারের নাম মনে আছে। তিনি ওলিউল্লাহ ভূঁইয়া স্যার। স্যার প্যান্ট ইন করে ফুলহাতা শার্ট পরতেন।
ক্লাস থ্রি থেকে ফোরে উঠলাম। ক্লাস চলে গেল বড় রাস্তার ধারে স্কুলের গেটের পাশে পূর্বদিকে দোতলায়। নিচতলায় স্কাউট ও কাব রুম। সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা রুম। সিক্সসের নিচের ক্লাসের ছেলেদেরকে কাবের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। কাব হওয়ার বাসনা হলো। ক’দিন কাব হওয়ার চেষ্টাও চলল। এরই মধ্যে বড় চাচা বড় চাচী গ্রাম থেকে বেড়াতে এসেছেন বাসায়। আমার স্কুলে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তবু আসতে হলো। দুই পিরিয়ড যেতে না যেতেই টেবিলের ওপর মাথা রেখে বাহুতে মুখ ঢেকে চোখের পানি লুকিয়ে রেখেছি। সহপাঠীরা জিজ্ঞেস করে আমার কী হয়েছে। মিথ্যা বললাম। বললাম পেটে ব্যথা। তারা স্যারকে বলে ছুটি নিয়ে দিলো। বাসায় চলে এলাম।
আমরা ১৯৫৩ সাল অবধি ওয়ারীর বাসায় ছিলাম। সে অবধি আমার বড় বোন কামরুন্নেসা হাইস্কুলেই পড়ত। তবে তার একটি দুর্ঘটনার কথা মনে আছে। একদিন স্কুলের গাড়িতে করে বাসায় ফেরার পথে হঠাৎ করে সে রাস্তায় পড়ে যায়। এ গাড়িতে বসা স্কুলের আয়া তা লক্ষ করেনি। গাড়ির পাদানি ধরে অনেক পথ ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে আসার পর তা কারো নজরে পড়ল। গাড়ি থামিয়ে তাকে গাড়িতে উঠানো হয়। ততক্ষণে তার সালওয়ার ফেঁটে পায়ের চামড়া বেশ কিছুটা ছিলে গেছে। আব্বা রেগে গেলেন। এ ঘটনা হেড মিস্ট্রেস বা হেড মাস্টারকে জানাবেন বললেন। স্কুলের আয়া তো কেঁদে ফেলল। তিনি জানলে তার চাকরি যাবে। অনেক কান্নাকাটি করে আব্বাকে তিনি শান্ত করলেন। আর কোনো দিন এমন হবে না। এ আশ্বাস দিলেন। তবে এমন আর পরে কোনো দিন হয়নি।
সে সময়ের আমার সহপাঠীদের যে ক’জনের নাম মনে আছে তারা হলো- রেজাউল করিম আর একজন হিন্দু ছেলে কালি। কালির গায়ের রঙ তার মা-বাবার দেয়া নামকে সার্থক করেছে। কালি আমাদের বাসার পথে তার বাসায় ফিরত নারিন্দার দিকে শ্রীমদ্য গৌরী মঠের কাছে। রেজাউল করিমের হাতের লেখা চমৎকার। স্যারেরা সবাই তার হাতের লেখার প্রশংসা করতেন। সে থ্রি থেকে ফোরে উঠতে ক্লাসে প্রথম হয়েছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালে ঢাকা অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সামনের রাস্তা দিয়ে রিকশায় বিকেলে উত্তর দিকে বাসায় যেতে তাকে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে জনাকয়েকের সাথে বেশ কয়েকবার দেখেছি।
নবাবপুর স্কুলের একটি ব্যান্ড দল ছিল। এর কমান্ডার জাহাঙ্গীর তো ছিল আমার কাছে এক বিস্ময়কর বালক। তার পরিচালনা এবং কমান্ড দণ্ড আন্দোলন এমন নিখুঁত ছিল যে, তা সবারই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ব্যান্ড দলের সবাই ছিল চৌকস। সে সময়ে উঝঅ-এ গ্রাউন্ডে যেটি বর্তমানে ঢাকা স্টেডিয়াম তাতে বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানে ব্যান্ড বাজিয়ে কুচকাওয়াজ করে নবাবপুর স্কুলের ব্যান্ড দলটি জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে বহুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এটি আমাদের নবাবপুর স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য আনন্দের ও গৌরবের বিষয় ছিল। স্কুলে সামরিক পোশাক পরে উপরের ক্লাসের ছেলেরা কুচকাওয়াজ করত। কুচকাওয়াজ হতো সারা মাঠজুড়ে আর ম্যাজিক শো হতো মাঠের পশ্চিম পাশে উর্দু সেকশন লাগোয়া। স্কুলটি বেশ বড়। মাঝে মধ্যে ম্যাজিক শো’রও আয়োজন হতো। এটি সেকালে ঢাকার নামকরা স্কুলগুলোর একটি সরকারি স্কুল। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকালের নাম ছিল প্রিয়নাথ হাইস্কুল।
১৯৫৩ সালেই আমাদের বাসা আবার বদল হয়। ক্ষণস্থায়ীভাবে দু’য়েক আত্মীয় বাড়ি থাকার পর যে ভাড়া বাড়িতে এলাম সেটা পূর্ব ধানন্ডির সেন্ট্রাল রোডে ইসমাইল সাহেবের বাড়ি। এখানে এসে কিছু দিনের জন্য আমার স্কুলে পড়ালেখার ছেদ পড়ে। একপর্যায়ে আমার নিঃসন্তান বড় চাচা সর্বজন শ্রদ্ধেয় পুণ্যাত্মা শামসুল হক ভূঁইয়া আমাকে গ্রামের বাড়ি নিয়ে মুরাদনগর থানার জাহাপুরের কমলাকান্ত একাডেমিতে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। স্কুলটি আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় আড়াই মাইল পুবে। বর্ষাকালে আরো ক’জনার সাথে সেই স্কুলের শিক্ষক আমার বাবার সৎচাচাতো ভাই আলি আহমেদ ভূঁইয়ার নৌকায় চড়ে এবং শুকনা মওসুমে হেঁটে স্কুলে যাতায়াত করতাম। এ মাস্টার চাচার কতেক ছেলে এবং তার বাবা আবদুল আজিজ ভূঁইয়া ১৯০৬ সালে এন্ট্রান্স পাস করে এ স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন।
এর চেয়েও কষ্টকরভাবে অনেককেই সে স্কুলে যাতায়াত করতে হতো শুনেছি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে আমার এক বিভাগীয় সহকর্মী এবং আমাদেরই ইউনিয়নের রঘুনাথপুরের বাসিন্দা প্রয়াত ইসমাইল মিয়া। তার মুখে শুনেছি তিনি নিজে লগি দিয়ে নৌকা বেয়ে এই আড়াইমাইল পথ পাড়ি দিয়ে প্রতিদিন বর্ষা মওসুমে স্কুলে আসা-যাওয়া করতেন। এমনটা অনেকেরই বিধিলিপি ছিল। সে সময়ে এ স্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের নারায়ণগঞ্জ গিয়ে পরীক্ষা দিতে হতো। তাদের কথা শুনলে শরৎবাবুর শ্রীকান্ত উপন্যাসে বর্ণিত স্কুলযাত্রী ছাত্রদের দুর্দশার কথা মনে পড়ে। এ স্কুলে আমি প্রায় ছয় মাস পড়েছি। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখতাম আমার বড় চাচী এক বদনা পানি আর এক জোড়া খড়ম নিয়ে আমার জন্য ঘরের দুয়ারে বসে আছেন।
এরপর ১৯৫৫ সালের ২৫ নভেম্বরে আমরা পরিবাগে চলে আসি। এই বাসায় আসার পর আব্বা আমাকে লেখাপড়া করানোর কথা ভাবলেন। ওয়ারী বাসার সাথে নবাবপুর স্কুল ছাড়ার পর জাহাপুরের কথা বাদ দিলে আমার লেখাপড়া এ যাবৎ বন্ধ ছিল। সহপাঠীরা এগিয়ে গেছে। আমি পিছিয়ে পড়েছি। একদিন আব্বা বললেন, তেজগাঁও গভর্নমেন্ট টেকনিক্যাল হাইস্কুলে ভর্তি পরীক্ষা হবে, ফরম নিয়ে আয়। সেখানে নবাবপুর স্কুলের ওয়ালিউল্লাহ স্যারকে তার নাম বলতে বললেন। তিনি এখন এ স্কুলে। স্যারের কথা মনে ছিল। স্কুলে গিয়ে তাকে আব্বার নাম বললে তিনি আমাকে একটি ভর্তি ফরম দিলেন। ভর্তি ফরম যথারীতি পূরণ করে স্কুলে জমা দিয়ে এলাম।
ভর্তিপরীক্ষা দিলাম। কতদিন থেকে বইপত্রের সাথে দেখা নেই। কোনো রকমে তা সেরে এলাম। ভর্তিপরীক্ষার ফল যেদিন বেরুবে সেদিন স্কুলে গেলাম। স্কুলের হেড মাস্টার স্যার তার কক্ষে মেধাক্রমানুসারে একজন করে ডাকছেন। বোঝা গেল যাদের ডাকা হচ্ছে তারা সবাই ভর্তির যোগ্য। প্রথম যাকে ডাকা হলো তার নাম আবদুর রহিম। একে একে অনেককেই ডাকা হলো। আমাকে ডাকা হলো না। স্কুলের ভেতর দিকের উত্তরের কলাপসিবল গেট বন্ধ। ওখান দিয়েই ভর্তি ইচ্ছুকদের ডাকা হয়েছে। অনেকের সাথে আমিও দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখন আর কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। আমি কলাপিসবল গেটের লোহার পাত ধরে হেডস্যারের রুমের দরজার দিকে তাকিয়ে একাই দাঁড়িয়ে রইলাম। কি আশ্চর্য! প্রায় আধা ঘণ্টা পর আমার ডাক পড়ল। ভেতরে গেলাম। পিতার নাম। বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দিলেন। ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলাম। খুশিতে মনটা ভরে গেল।
ভর্তির পর যেদিন প্রথম স্কুলে এলাম সেদিন সাথে আব্বা আবদু মিয়া ভূঁইয়া। মধ্যবয়সী সুঠামদেহী হেডমাস্টার বিলেতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুদর্শন সুবেশী মাথায় অ্যাশ কালারের স্যুটের সাথে মানানসই একটি মোটা কাপড়ের হ্যাট পরিহিত আবদুর রাজ্জাক পদার্থবিদ্যায় এমএসসি। তার কণ্ঠস্বর ধীর, ভরাট এবং গম্ভীর। পরে তিনি ভারপ্রাপ্ত ডিপিআই হয়েছিলেন। তার সামনে আমাকে এগিয়ে দিয়ে আব্বা বললেন, ‘মাংসগুলো আপনার আর হাড্ডিগুলো আমার’। এ স্কুলে আমাকে কারো হাতে একটি বেতের বাড়িও খেতে হয়নি তবে দশম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় কোনো এক সহপাঠীর চক্রান্তের জেরে আমাকে অঙ্কের শিক্ষক গহর স্যারের একটি চপেটাঘাত সহ্য করতে হয়েছে। দূরে কাছের ছাত্ররা সবাই হেঁটে স্কুলে আসত। কেউবা সাইকেলে চড়ে। একদিন এক সহপাঠীর সাইকেল নিয়ে তাকে পেছনে কেরিয়ারে বসিয়ে বাসায় ফেরার পথে কাওরান বাজারের কাছে অ্যাক্সিডেন্ট করে ঢাকা মেডিক্যালের চিকিৎসা নিয়ে দুই মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। আমার লেখাপড়ার ব্যাপারে মায়ের উৎসাহটাই ছিল বেশি। ১৯৫৬ সালে এ স্কুলে ভর্তি হলাম শেষ ছাত্র হিসেবে; আর বেরিয়ে এলাম ১৯৬১ সালে প্রথম ছাত্র হিসেবে। এমনটা এ স্কুলে আগে আর ঘটেনি বলে আমাদের শ্রেণিশিক্ষক অঙ্কের নুরুল হক ভূঁইয়া স্যার প্রকাশ্যেই বললেন।
লেখক : অর্থনীতির অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মহিলা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা
আরো সংবাদ
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা
-
- ৫ঃ ৪০
- খেলা




